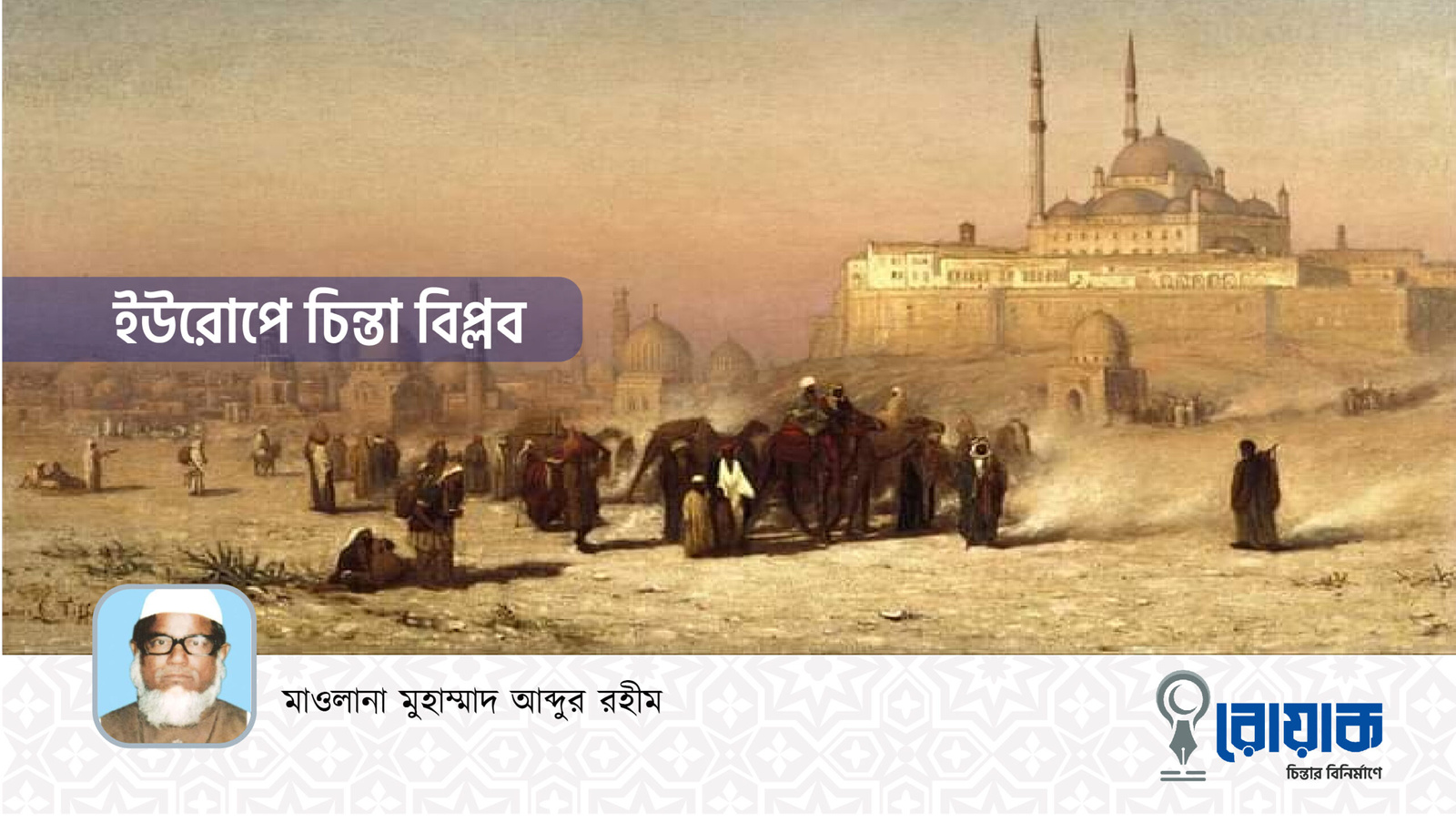মুসলমানরা যেকালে বাগদাদ, মিশর ও স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগন্তপ্লাবী আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, সেকালে সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞতার সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। ইউরোপীয় ইতিহাসে এই যুগটি অন্ধকার যুগ (Dark Age) নামে অভিহিত। এ সময়ে স্পেনের মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অংকশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ও রসায়ন, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যাপক ব্যবস্থা বর্তমান ছিলো এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা এসে এখানে ভিড় জমিয়েছিলো। তারা গ্রানাডা ও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগদান করে নিজেদের ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করতো। প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্স ও ইটালী থেকেও বহুসংখ্যক জ্ঞানপিপাসু এ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে এসে জমায়েত হতো এবং মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত এ বিশাল জ্ঞানকেন্দ্র-সমূহে মুসলিম মনীষীদের নিকট শিক্ষালাভ করে ও উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করে নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করে লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচারে আত্মনিয়োগ করতো। এরই ফলে ইউরোপ ধীরে ধীরে অজ্ঞতা ও মূর্খতার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে জাগ্রত হতে শুরু করে এবং তার পরিণতি স্বরূপ সমগ্র ইউরোপে নবজাগরণের জোয়ার প্রবাহিত হয়, আসে রেনেসাঁর যুগ। খ্রিষ্টীয় ষোল ও সতের শতকে এই জাগরণ অধিক ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধি লাভ করে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও রোমে এ সময়েই বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেসব স্থানে জ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যাপক ব্যবস্থা কার্যকর হয়। অপরদিকে এ সময়েই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সাধিত হয়। নিত্য-নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হতে শুরু করে এবং সূচিত হয় এক নতুন শিল্পযুগ। এ শিল্পযুগে ইউরোপ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভূ-খন্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করার ও বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলার বিরাট সুযোগ লাভ করে। এভাবে শিল্প-উৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধন-ঐশ্বর্যের বিপুল প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চায়ও ইউরোপ সমধিক অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত ইউরোপীয়দের জীবনদর্শনে চিন্তা ও মতবাদে বিশেষ কোন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা খ্রিষ্টীয় অস্তিত্ব ও পরিস্থিতি, পরকালীন পুরষ্কার ও শাস্তি, নৈতিক মূল্যমান ও খ্রিস্টীয় প্রেম-ভালোবাসার চর্চা প্রভৃতি ধর্মীয় ভাবধারা ঊনবিংশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে।
কিন্তু এই ঊনবিংশ শতকেই ইউরোপবাসীদের চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে ইউরোপ সকল ক্ষেত্রে নতুনত্ব সৃষ্টির লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তাদের সাহস, কর্মোদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্য বিপুলভাবে বৃদ্ধি করে দেয়, যন্ত্রপাতির নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীর ফলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রায় সবকটি বিভাগে যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ প্রবল ও প্রকট হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুজিঁবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশ্বলোককে একটা বিরাট ‘যন্ত্র’ মনে করতে শুরু করা হয়। পূর্ববর্তী ধর্মতাত্ত্বিক মতাদর্শ (Metaphysical Ideas) সন্দেহপূর্ণ ও অবিশ^াস্য বলে ধরে নেয়া হয় এবং এ পর্যায়ের সব চিন্তা ও মতাদর্শকে যান্ত্রিক নীতিতে (Mechanical Principles) পুনর্বিবেচনা করার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। গোটা সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈষয়িকতাবাদী-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল হয়ে ওঠে। আদর্শ ও নৈতিকতার গুরুত্ব লঘু হয়ে যায় এবং সুবিধাবাদ ও স্বার্থবাদের ভিত্তিতে নতুন নীতিদর্শন (Ethics) বিরচিত হয়। এমনকি মানুষকে একটা ‘জীবন্ত চলমান যন্ত্র বিশেষ’ প্রমাণ করার প্রবণতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় এবং বর্তমান ও সাম্প্রতিক সংক্ষিপ্ত জীবনটুকু ছাড়া তার কোন অতীত বা ভবিষ্যত আছে বলে বিশ্বাস করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এই সময় সার্বিকভাবে ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে যে চিন্তা-বিশ্বাস ও মনোভাব-মানসিকতা দানা বেঁধে উঠতে থাকে, তারই পারিভাষিক নাম হচ্ছে ‘সেকিউলারিজম’।
ইউরোপীয় সমাজের তদানীন্তন পরিবেশ পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে জনগণের এ যান্ত্রিক মনোভাবের জন্যে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে দায়ী করা চলে না, কারূর কোন বিশেষ ইচ্ছাগত সিদ্ধান্ত বা চেষ্টা সাধনার ফলে এরূপ হয়েছিল বলেও দাবি করার কোন অবকাশ নেই। ইউরোপীয় সমাজে তখনকার সমগ্র সমাজের গতি এদিকেই নিবদ্ধ ছিল, একটা তীব্র ও বিদ্বেষমূলক বৈষয়িকতাবাদী (Secularist) বস্তুবাদী ভাবাবেগই যেন গোটা ইউরোপীয় সমাজকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করে বসেছিলো। এরূপ অবস্থায় মানুষ নিতান্ত বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে চিন্তা ও গবেষণা পরিচালনা করতে যেন একান্তভাবে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। তখনকার সমাজে যান্ত্রিকতা ও বৈষয়িকতার নীতিতে যে তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা পেশ করা হতো তা মন ও মানসকে পরিতৃপ্ত করতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গেই তা সর্বজন গৃহীত হয়ে যেতো। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার (Physical Science) যান্ত্রিক নীতিসমূহ তখন জ্ঞান গবেষণায় এমন উজ্জ্বল প্রদীপ বলে মেনে নেয়া হয়েছিল যে, তার চোখ ঝলসানো চাকচিক্য ও আলোকচ্ছটায় প্রত্যেক চিন্তাবিদ ও গবেষক গভীরভাবে প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়েছিলো।
বিশ্বলোক (Universe) ও মানুষকে বৈষয়িক ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে বিচার করার একটা তীব্র প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসব কারণে খ্রিস্টান ধর্মীয় পণ্ডিতেরা তাঁদের খ্রিষ্ট ধর্মকে এক মহাবিপদের সম্মুখীন দেখতে পেয়ে রীতিমতো কেঁপে উঠেছিলেন এবং খ্রিস্ট ধর্মকে জ্ঞান ও চিন্তার নতুন আলোর আঘাত থেকে রক্ষা করার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। অধ্যাপক উইলিয়ামস বেক এ সময়কার অবস্থা বিশ্লেষেণ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ
“হাক্সলি (Huxley) যখন মানুষের আদি পুরুষ সম্পর্কে নিজের মতবাদ প্রচার করলেন, তখন মানুষের পরিকল্পিত অপমানের জন্যে লোকেরা শত বছর পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকলো। আর পবিত্রতা ও নৈতিকতার প্রবক্তরা বলতে শুরু করল যে, বিজ্ঞান তার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফলাফল ঘোষণা করলেও অনুরূপ চিৎকার উঠেছিলো। তা সত্ত্বেও কালের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মতাদর্শ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বস্তুত এ দু’টি মতাদর্শ সমগ্র মানব সমাজের সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টি ও চিরন্তন কালের চিন্তা-বিশ্বাসের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করলো।”
এ সময় ইউরোপে বর্ষাকালীন পোকামাকড়ের মতো অসংখ্য মতবাদ গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে সেকিউলারিজম ভিত্তিগত মতাদর্শ বা অসংখ্য মতবাদের উৎস হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। এ মতবাদটিকে ভিত্তি করেই চিন্তাবিদগণ তাদের চিন্তা ও মতবাদ রচনার কাজ চালিয়ে গেছেন। এই পর্যায়ের চিন্তাবিদের মধ্যে তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং এ তিনজনই চিন্তার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। এ তিনজনের একজন হলো চার্লস ডারউইন। তিনি বিবর্তনবাদী মতবাদের উদ্গাতা। দ্বিতীয়জন সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। আধুনিক মনস্তত্ত্ব তারই অবদান। আর তৃতীয়জন কার্ল মার্কস। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ তার কল্পনার ফসল। এক কথায় এ তিনজন চিন্তাবিদ পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা বা নির্মাতা বলে অভিহিত। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তিভূমি এই তিনজনের চিন্তাধারাই সম্মিলিতভাবে রচনা করেছে। এদের উপস্থাপিত মতাদর্শ পাশ্চাত্যের লোকদের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, প্রভাবিত করেছে এবং তাতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এ কালের চিন্তাবিদদের মতে এদের চিন্তাধারাকে বাদ দিয়ে একালের পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন সম্পর্কে কোন আলোচনাই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।
প্রসঙ্গত বলা যায়, এই চিন্তাবিদ ত্রয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন সর্বজন জ্ঞাতভাবেই ইসলাম ও মুসলমানদের চির দুশমন ইয়াহুদী বংশজাত।১ আর প্রথমজন নিজে ইয়াহুদী না হলেও তার সমস্ত চিন্তা ও মত ইয়াহুদীদের দ্বারাই ব্যাপক প্রচারিত ও তাদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে সর্বাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) দীর্ঘ কয়েক বছরকাল ধরে গাছপালা, বৃক্ষলতা ও জীব-জন্তুর গভীর জীবতাত্ত্বিক অধ্যয়ন করেন এবং দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন ও গবেষণার পর Origin of Species নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেই তিনি তার চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী মতবাদটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেন। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে তিনি শুরু থেকেই অস্বীকার করে এসেছেন। তার দৃষ্টিতে তা একটা ধাঁধাঁ বা ‘নিছক কল্পনা’ ছাড়া আর কোন মর্যাদারই অধিকারী হয়নি। কিন্তু মানুষের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্রমের কোন ব্যাখ্যা দান তখনকার বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উত্তরকালে ডারউইনী বিবর্তনবাদ যখন দৈহিক কার্যক্রমের একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পেশ করেছিল, তখন ইয়াহুদী চিকিৎসাবিদ ফ্রয়েড কর্তৃক উপস্থাপিত হলো মনস্তাত্ত্বিক (কার্যক্রমের জড়বাদী বা যৌনবাদী) ব্যাখ্যা। ফ্রয়েড উনিশ শতকের শেষ দশকে ভিয়েনায় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি এক অভিনব পন্থার সাহায্য গ্রহণ করেন। এ পন্থর নাম হলো ‘মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ (Psycho Analysis) এই প্রসঙ্গে তিনি যেসব মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক মতবাদ ও চিন্তাধারা উপস্থাপিত করেন, অধ্যাপক উইলিয়ামস বেক সেগুলোকে বিজ্ঞান-চিন্তার ফসল আখ্যায়িত করেছেন এবং তার প্রতিবাদ, সমালোচনা বা বিপরীত চিন্তাকে ‘চিৎকার’ বলে অভিহিত করেছেন। এই মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ডারউইনের ক্রমবিকাশ দর্শনের সাথে মিলিত হয়ে সেকিউলার বা ধর্মহীন বরং ধর্মবিরোধী জড়বাদী এবং নাস্তিক্যবাদী প্রবণতাকে খুবই বলিষ্ঠ করে তুলেছে। ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসকে তো কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন বলে তার প্রতি উৎকট ঘৃণা প্রকাশ করেছেই। মানুষের যে কোন উচ্চ মর্যাদা ও মহান জীবন-লক্ষ্যে থাকতে পারে, প্রেরিত হয়ে থাকতে পারে কোন মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে-কিংবা তা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এরূপ মনোভাবকে অপরিপক্ক চিন্তা ও নিতান্তই খোশ-খেয়াল বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই চিন্তা ও মন-মানসিকতা আল্লাহ অস্বীকৃতির দিকে আরও অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।
ডারউইনের মতবাদ মানুষের মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আর ফ্রয়েড মানুষের উন্নতমানের মহান পবিত্র চরিত্র গুণের উপর তীর চালিয়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। অতঃপর কার্ল মার্কস এসে সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তনের মূলে অর্থনৈতিক কার্যকারণের অনিবার্যিক কার্যকরতা প্রমাণ করে মানুষকে নিতান্তই অর্থনৈতিক জীব প্রমাণ করতে বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন।
মার্কস ১৮৬৭ সালে ‘Das Capital’ নামে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তাতে অর্থনীতি পর্যায়ে বহু বিপ্লবী চিন্তাধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থটিই হলো ‘কমিউনিজম’ ধর্মের ‘বাইবেল’।
এ গ্রন্থের মূল বক্তব্য হলো, বিশ্বলোকের নৈসর্গিক সম্পদ ও উপায়-উপাদান এবং শ্রমিকের শ্রম দিয়েই সমস্ত ব্যবহার্য দ্রব্য ও পণ্য উৎপন্ন হয়-প্রাকৃতিক সম্পদ উপায়-উপকরণের উপর সকলেরই সমান অধিকার।
অতএব উৎপন্ন ব্যবহার্য পণ্য সবই শ্রমিকদের শ্রমের ফসল। মালিকের ব্যবস্থাপনা (Management) শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাদের ব্যক্তিগত শ্রম অপেক্ষা অনেক বেশি লাভ করার লোভে সমস্ত বিবর্তনবাদী মতাদর্শ (theory of Evolution) পেশ করেন।
এই ক্রমবিকাশ তত্ত্বের দৃষ্টিতে মূল জীবনটাই যেন ক্রমবিকাশমূলক কার্যক্রম। তা একটি অতি নগণ্য সূক্ষ্ম কীট থেকে শুরু হয়ে বিবর্তনের ধারা অবলম্বন করে এই মানুষ পর্যন্ত হয়েছে। এ ক্রমবিকাশ কার্যক্রমের কার্যকরণ (Cause) একান্তভাবে জৈবিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক।
মৌল উপাদানের কোন প্রাথমিক আকস্মিক সংঘাত কেবল একটিমাত্র সূক্ষ্ম জীবকোষ (Life Cell) সৃষ্টি করেছে। পরে তাতে বিপুল জীবন সংগতি ও বেঁচে থাকার যোগ্যতার উদ্ভব হয়। কালের ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে শক্তি পরীক্ষা এবং কোটি কোটি বছরের ক্রমাগত প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও ক্রম অভিব্যক্তি প্রবণতা (Evolutionary Trend) এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবকোষ (Germplasm)-কে বিকাশ দান ও রূপান্তর সাধন করে এখনকার মানুষের আকৃতি বাস্তবায়িত করেছে। ক্রম-বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে জীবসমূহের বিভিন্ন আকার-আকৃতির উদ্ভব হয়েছে। দূরে অতীতের সেসব জীব-জন্তুর অবশিষ্ট এখনও কিছু বেঁচে আছে। আর অনেক-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
বিশ্বলোকে জীবনের উন্মেষ এবং বিভিন্ন প্রজাতীয় অভিব্যক্তির ডারউইনীয় ব্যাখ্যা মানব জীবন সংক্রান্ত যুগ যুগ থেকে চলে আশা ধারণা, বিশ্বাস (Conception) ও মূল্যমানকে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির খোলাহাটে নির্মমভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও অপদস্ত করেছে। শাশ্বত মূল্যমানের এ অপমানে নীতিবাদীর চিৎকার করে উঠেছে বটে; কিন্তু আধুনিকতাবাদীদের মন ও মানস সেই ব্যাখ্যাকেই পরম সত্য রূপে গ্রহণ করেছে এবং তাতেই লাভ করেছে মন ও মানসের গভীর তৃপ্তি ও স্বস্তি। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রকৃতি প্রবণতা অনুযায়ী বিশ্বলোকে জীবনের ও জীবের উন্মেষ ও অস্তিত্বের রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক ব্যাখ্যা লাভ করেছে। লাভ করেছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণের আচ্ছাদনে, তাতে যত ফাঁক ও ফাঁকিই থাকুক না কেন, সেদিকে এতটুকু ভ্রুক্ষেপ করারও প্রয়োজন তারা বোধ করেনি; বরং তাকে উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেছে।
সেকিউলারিজম মতাদর্শভিত্তিক এ ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ বর্তমান সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ কারণে আজকের মানুষের নিকট আবহমানকালের মানবতা, মনুষ্যত্ব এবং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা নিতান্ত মূল্যহীন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানুষ জীব মাত্রে-উন্নত আকৃতিসম্পদ পশুতে-পরিণত হয়েছে।
এই পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মপ্রকাশ করেছে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের চিন্তাধারা। সে চিন্তা ও মত অনুযায়ী মানুষ মূলত একটি ‘বস্তুগত যন্ত্র’ মাত্র। এখানে দেহ ও প্রাণশক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বলতে কিছুই থাকলো না। কেননা উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ‘প্রাণ’ কোন স্বতন্ত্র সত্তারূপে গণ্য নয়, তা বস্তুরই বিবর্তনের একটি পর্যায় মাত্র। পাশ্চাত্যেও ‘সেকিউলার’ বিজ্ঞান-আল্লাহ অস্বীকারকারী জড়বাদী বিজ্ঞান ‘রূহ’ বা প্রাণশক্তিকে এড়িয়ে এবং তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে আস্বীকার করেই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে। আর পুঁজিবাদের ব্যাখ্যায় কার্ল মার্কস বলেছেন যে, পুঁজিপতিরা শিল্পের আমল ও মৌলিক মুনাফা নিজেরাই কুক্ষিগত করে। তাই বঞ্চিত শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে এ উৎপাদন ব্যবস্থাকে খতম করে, পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে বলে এক ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।
ডারউইন, ফ্রয়েড ও মার্কসের পূর্বোদ্ধৃত চিন্তাধারাই বর্তমানে পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের ভিত্তিপ্রস্তর। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি এই চিন্তাধারার আঘাতে সদা কম্পমান। মার্কসের কমিউনিজম তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত না হলেও পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলে সমাজতন্ত্রের অনেকখানি কাছে এসে গেছে। আর রাজনৈতিক গণতান্ত্রিকতা অনেকখানি সমাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেকিউলারিজম-এর মতাদর্শ এসব দেশেই সমাজের ভিত্তি হিসেবে অভিন্নভাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে।
বস্তুত মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে জিনিসকে ‘স্বাভাবিক’ বলে মনে করে, বাস্তব জীবনে তাকেই সত্য করে তোলে। এটাই হলো মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দুর্বলের ধ্বংস ও বিলয় এবং সবল ও শক্তিমানের উর্দ্বতন অনিবার্য করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এবং তার ফলাফলকে অতীব স্বাভাবিক পরিণতি রূপে গণ্য করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতেই মানুষের বাস্তব জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি, শ্রেণী ও জাতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে অত্যন্ত স্বাভাবিক, যথার্থ ও কাম্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। আর এর পরিণামে শাক্তিমানের বিজয় ও উর্দ্বতন এবং দুর্বল-শক্তিহীনের পরাজয় ও অবলুপ্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত বলে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে। এর কোন একটি ক্ষেত্রে একবিন্দু অস্বাভাবিকতা অনুভূত নয় পাশ্চাত্য সামাজের নিকট। এক কথায় ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নীতি শাশ্বত ও চরম সত্য বিধানরূপে পাশ্চাত্য সমাজের নিকট চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
কিন্তু আবহমান কালের পরম সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের দৃষ্টিতে তা নিতান্তই অন্যায়, জুলুম ও স্বভাব পরিপন্থী কার্যকলাপ রূপে প্রমানিত। সে দৃষ্টিকোণে সব মানুষই আল্লাহর সৃষ্টি, সকলেই সমান মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন। শক্তিমানের হস্তে দুর্বলের স্বার্থহানি অবৈধ ও অতি বড় অপরাধ। মূল্যমানের দিক দিয়ে তা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং কার্যত অবশ্য পরিত্যাজ্য।
ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্বের আলোকে মানুষ তার পাশবিক পূর্ব পুরুষদের স্বভাব গ্রহণ করেছে। চারদিকে পশুসুলভ রীতিনীতির আইন-কানুন চালু হওয়া তারই অনিবার্য পরিণতি। বর্তমানের পাশ্চাত্য জাতিসমূহ জাতিসংঘের সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এসব আইনের অধীনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ন্যায় বা অন্যায়, শোভন বা অশোভন, জুলুম বা ইনসাফ প্রভৃতির প্রশ্ন তাদের নিকট কোন গুরুত্বই পাচ্ছে না। বঞ্চিত, নিপীড়িত ও দুর্বল জাতিগুলোর ফরিয়াদ আকাশ-বাতাসকে মথিত করে তুলেছে। কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত করার কেউ নেই। প্রবল ও পরাশক্তিগুলো ‘খায়ও এবং হুংকারও ছাড়ে’ আর ভোটদানের সময় নিপীড়িত জাতিগুলোকে বড় বড় অত্যাচারী জাতিগুলোর পক্ষে রায় দিতেও বাধ্য করছে। তা না দিলে তাদের পরিণামও অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি বৃহৎ শক্তি অপর বৃহৎ শক্তির পক্ষেই কাজ করে। বাহ্যিকভাবে বক্তৃতা-ভাষণে যত বিরোধই দেখানো হোক, আসল কাজে তাদের সকলেরই ভূমিকা সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন । কোন বৃহৎ শক্তি অপর কোন দুর্বল শক্তির পক্ষে কাজ করলেও তা করে তাকে সমূলে ধ্বংস করার তাকে চূড়ান্তভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে । তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকার সুযোগদানের লক্ষ্যে নিশ্চয়ই নয়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এদিক দিয়ে খুবই তিক্ত।
ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শে তো স্পষ্ট ভাষায় মানুষকে এক ‘যৌন আবেগসর্বস্ব জন্তু’ বানিয়ে দেখানো হয়েছে। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও একান্তই সাধারণ ব্যাপাররূপে পেশ করে নৈতিক বিধিনিষেধ, বাধা-বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণকে নিতান্তই অনভিপ্রেত এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণ বলে চিহ্নিত করেছে। এটাই ছিল ধন-ঐশ্বর্যে মদমত্ত পুঁজিবাদীদের কাম্য। ফলে চারদিকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্বিশেষে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনজনিত ব্যভিচারের প্লাবন বয়ে গেল। এর পূর্বে পাশ্চাত্য দেশসমূহের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন প্রাচ্য দেশীয় পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের মতোই সুস্থ ও পবিত্র ছিল। ভিন পুরুষের সাথে ভিন নারীরা গোপনে মিলিত হওয়া প্রাচ্য দেশের মতোই দূষণীয় ও অবাঞ্ছিত ছিল। সেখানে যুবতী মেয়েরা কোন আত্মীয় পুরুষ বা নারীরা সঙ্গ ছাড়া ঘরের বাইরে যাতায়াত করতে পারতো না। কিন্তু ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শ পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষকে বাঁধাভাঙ্গা জলস্রোতের মতোই উদ্দাম ও উত্তাল করে দিয়েছে, অবিবাহিত নারী-পুরুষের পারস্পরিক প্রেম বিনিময় একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। মেয়েরা এখন আর ঘরের রাণী হয়ে থাকতে প্রস্তুত নয়, তারা এখন সভা-সম্মেলনের প্রদীপ শিখা, মঞ্চের গায়িকা, নৃত্যরতা শিল্পী আর অফিসের রিশিপসনিস্ট, বড় সাহেবের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী, কর্মচারীদের সহকর্মিণী, টাইপিস্ট, স্টেনো এবং দোকানের বিক্রয়কারিণী (Sales Girls) ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রী এখন স্বামীর একক শয্যা-সঙ্গিনী নয়, বন্ধু ও প্রিয়জনকে আপ্যায়নের সামগ্রী বিশেষ। স্বামীদের পক্ষে এটা যেমন একটা গৌরবের ব্যাপার, তেমনি স্ত্রীদের জন্যেও বহু ভোগ্য হওয়া কম গৌরবের ব্যাপার নয়। কুমারীরা মা হতে এবং মা রূপে সমাজে পরিচিতা হতে এখন আর কোন লজ্জা বা সংকোচ বোধ করে না, সামাজিকভাবে নয় তারা ঘৃণিতা বা লাঞ্ছিতা। বরং বৈধ মা’দের অপেক্ষা তারা কিছুমাত্র কম সম্মানিতা নয়। কেননা ফ্রয়েডের দর্শন সব দ্বিধা, সংকোচ, লজ্জা বা অন্যায়বোধের অবসান ঘটিয়েছে। অবৈধ সন্তানের উৎপাদন বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনের চাইতেও অধিক উন্নতির পথে। ফ্রয়েডীয় দর্শনের এটাই বড় অবদান।
ধন-সম্পদেও অসম বণ্টন, পুঁজিপতিদের অমানুষিক শোষণ, বিলাস-ব্যসন, লালসা চরিতার্থতা ও বিলাসী জীবন-যাপন, সুখ-সম্ভোগ গরীবদের অনশন ও দুঃখ-দারিদ্র এবং নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের প্রচণ্ড অভাব কার্লমার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের জন্যে সহায়ক ও অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। শ্রমিক শ্রেণীর অসহায় অবস্থা যখন চরমে,তখন তারা ক্রুদ্ধ-বিক্ষুদ্ধ হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং সব রকমের বাধা-বন্ধনকে চূর্ণ করে বন্য হিংস্র পশুর মতো এমনভাবে হুংকার দিলো যে, পুঁজি ও পুঁজিদারদের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও ধর্মের সব নিয়ম-কানুন ও মূল্যবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দিলো। রাশিয়ার রক্তাক্ত বিপ্লব কত নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত ঝরাবে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। ১৯১৭ থেকে যে নির্মম রক্তপাতের ধারা শুরু হয়েছে, বর্তমানে দুনিয়ার অন্য বহু সংখ্যক দেশে সে ধারাই চলছে অব্যাহতভাবে। যে হিংসা,আক্রোশ ও শত্রæতা-জিঘাংসা দিয়ে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, তা দুনিয়ার দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের রক্তের বন্যা প্রবাহিত করে চলেছে। তবু মার্কসীয় দর্শনের রক্ত পিপাসা এখনও নিবৃত্ত হয়নি।
বর্তমান দুনিয়া এমন একটি একটি কারখানায় পরিণত হয়েছে, যেখানে মালিক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক শ্রেণী মুখোমুখী হয়ে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার কঠিন দ্বন্দ্ব সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। কোন পক্ষই অপর পক্ষের নিকট একবিন্দু নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, কোন পক্ষই উন্নত নৈতিকতা, মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমানের প্রতি একবিন্দু শ্রদ্ধা জানাতেও আগ্রহী নয়।
ডারউইন ও ফ্রয়েডীয় দর্শন তাদের এসব বন্ধন ও বাধ্যবাধকাতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়েছে। আর কার্ল মার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের দর্শন ‘বিশ্ব কারখানায় বিশ্ব ধর্মঘট’ করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকটি দেশের জনগণ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক ভাগের লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে রাশিয়া। আর অপর ভাগের আসল প্রভু বা মন্ত্রণাদাতা হচ্ছে আমেরিকা। আর তারই অনিবার্য পরিণতিতে প্রায় প্রত্যেকটি দেশ ‘রুশপন্থী’ আর ‘মার্কিনপন্থী’ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘিœত করছে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলেছে।
বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরে যে দলাদলি ও সংঘর্ষ চলছে, তার পেছনে এই পরাশক্তিগুলোর হাত রয়েছে নিশ্চিতভাবে। এসবের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ও ধন-সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। একথা নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে, স্থানীয় সংঘর্ষ ও সংঘাত মূলত স্থানীয় নয়, তা দুনিয়ার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ শক্তিবর্গেরই কারসাজি। দুনিয়ার বহু ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতি বৃহৎ শক্তিবর্গের মানবতা বিধ্বংসী চাল ও চক্রান্তে পড়ে পয়মাল হয়ে যাচ্ছে।
কিন্তু মানুষের রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে দেখে- না স্থানীয় মানুষের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসছে, না বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্তরে কোনরূপ দয়া-মায়ার উদ্রেক হচ্ছে। তারা নিত্যনতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণ করে, তার ভয়ে ভীত করে প্রাচ্যের লোকদের ওপর তাদের নিজস্ব মতাদর্শ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চাইছে। বিশ্ব মানবতার প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতার এটাই হচ্ছে বড় অবদান। আর এ সভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছে এ সমস্ত আলোচিত চিন্তা ও দার্শনিক মতবাদসমূহের ওপর।
টীকাঃ
১. ইয়াহুদী জাতি জাতীয় ভাবেই খোদাদ্রোহী। সকল প্রকারের অনিষ্ট সাধনে সিদ্ধ হস্ত। হিংসা-বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মহাজনী পুঁজিদারী এই জাতির রক্তে মাংসে মিশ্রিত। দুনিয়ার যেখানেই কোন গণ্ডগোল হয়েছে বুঝতে হবে তার পিছনে অবশ্যই ইয়াহুদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হাত রয়েছে। অতীতের কথা বাদ দিলেও বর্তমান দুনিয়ার উদ্ভাবিত অকল্যাণ সৃষ্টিকারী প্রধান মতবাদ সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম এদেরই অবদান। সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ পুঁজিবাদেরই একটি আকর্ষণীয় রূপ মাত্র। ইয়াহুদীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সহকারে এই মতাদর্শের বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালিয়েছে। এই মতবাদের রচয়িতারও বড় বড় নেতা; সকলেই দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন ইয়াহুদী। ১৯৭১ সনের রুশ বিপ্লব মূলত ইয়াহুদীদেরই চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফসল। এ বিপ্লবের হীরো লেনিন ইয়াহুদী মত প্রচারে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ছিলেন। ইয়াহুদী লোকেরাই এ বিপ্লবকে সমর্থন ও তার কল্যাণের ব্যাখ্যা করে সব চাইতে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছে। ইয়াহুদী মহাজনী কাজে ও জাতীয় উন্নয়নে সব চাইতে বড় অবদান রয়েছে রাশিয়ার। আজকের দুনিয়ায়ও ইয়াহুদীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে রাশিয়া। আমেরিকা ও রাশিয়া বাহ্যত দুটি প্রতপক্ষ হলেও ইয়াহুদী স্বার্থে উভয়ের নীতি অভিন্ন। তাই বলা যায়, পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রের সাথে ইয়াহুদীবাদ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আর বর্তমানে দুনিয়ার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক’ উভয় ধরণের রাষ্ট্র ও সমাজ আলোচ্য তিনজন চিন্তাবিদের দার্শনিক চিন্তাধারার বড় সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক, ধারক ও অনুসারী। আজকের দুনিয়ার এই দুই পরাশক্তির চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণ সম্যকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে এই তিনজন চিন্তাবিদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। এঁদের প্রত্যেকেরই চিন্তা-গবেষণার মূলে নিহিত রয়েছে ‘সেকিউলারিজম’ মতবাদটি। প্রথমে তারা ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে, ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব থেকে নিজেদের মন-মগজকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেই নিজ নিজ বিষয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা চালিয়েছেন। এই কারণে ‘সেকিউলারিজম’ মতাদর্শটিকে সর্বপ্রথম গভীরভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। তার পরই উক্ত প্রধান তিনজন চিন্তাবিদের উপলদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে।