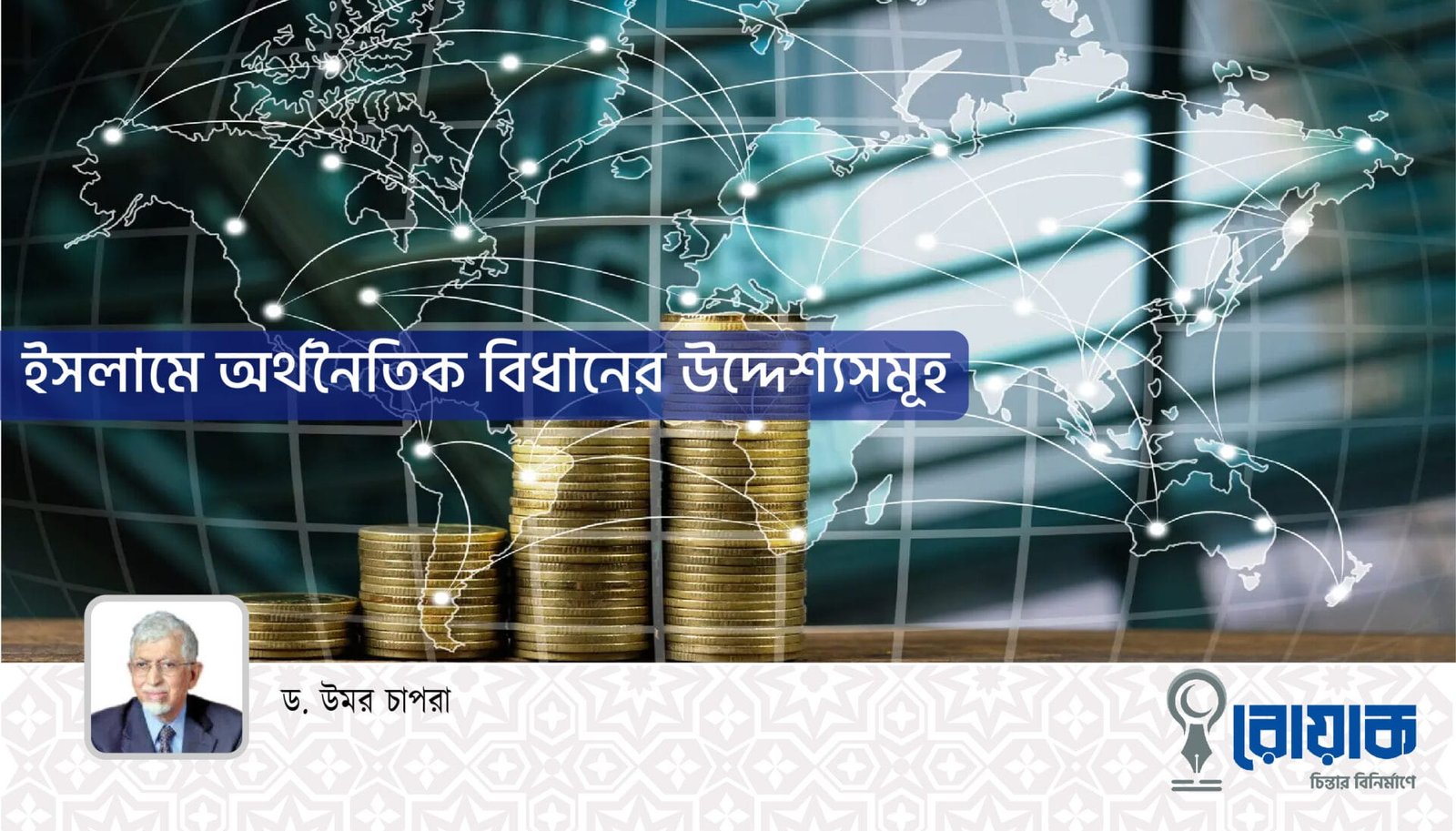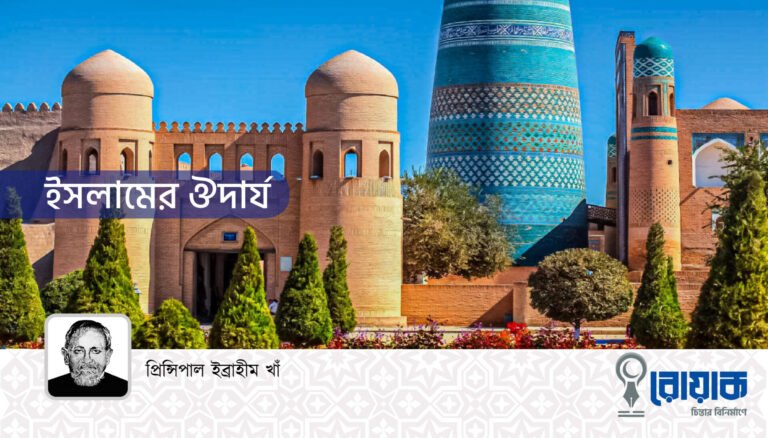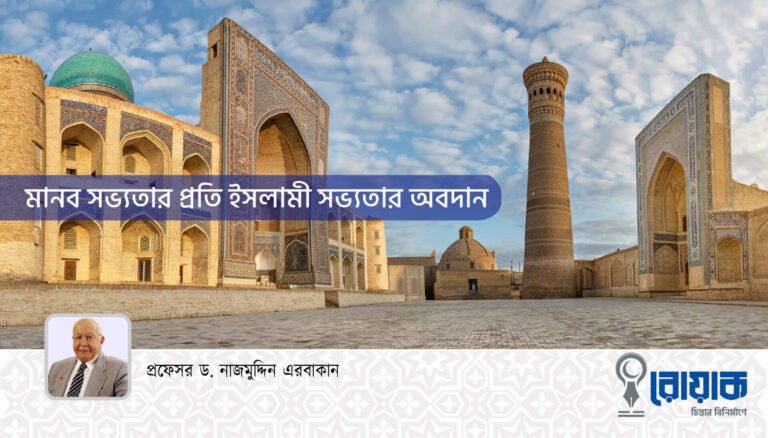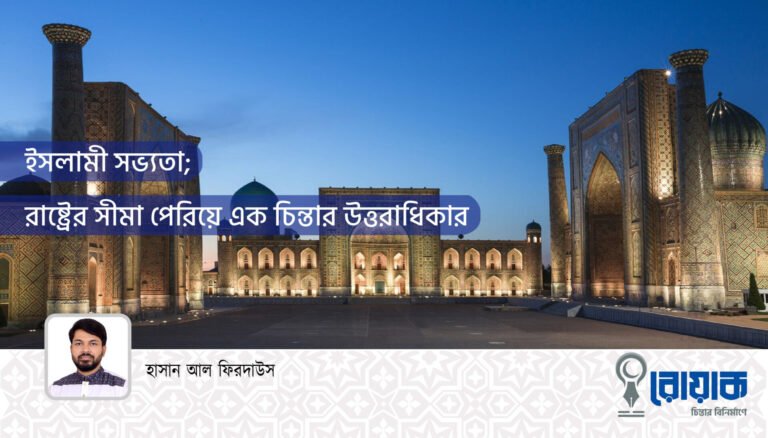ইসলাম জীবনবিমুখ কোনো ধর্ম নয় (১) এবং এটি কখনো মানুষকে “আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ” (কোরআন, ৭:৩২) থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে না। বরং ইসলাম মানুষের প্রতি ইতিবাচক একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে এভাবে, “মানুষ জন্মগতভাবে গুনাহগার নয়, বরং সে পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি বা খলীফা এবং সে শুধুমাত্র নিজের কৃত গুনাহসমূহের জন্যই দায়ী থাকবে।” (আল কোরআন, ২:৩০) এমনকি “মানুষের জন্যই এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।” (২:২৯)। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহকে ত্যাগ করার মধ্যে নয়, বরং তার দেওয়া সীমারেখায় থেকে সেগুলোকে ভোগ করার মাঝেই কল্যাণ নিহিত।
যাবতীয় মানবীয় কার্যাবলি ইসলামের ধর্মীয় মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে জাগতিক কাজ বলে আলাদা করে কোনো বিভাজন নেই। অর্থনীতিসহ মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরণের কাজই আধ্যাত্মিক, যদি সেটি শান্তির জন্য হয় এবং ইসলামের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের সীমার মধ্যে হয়। এই লক্ষ্য এবং মূল্যবোধগুলোই ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। তাই, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আরো ভালো দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এই বিষয়গুলোর সঠিক বোঝাপড়া থাকা দরকার। এই মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যগুলো হলো-
- ১. ইসলামের নৈতিক কাঠামোর মধ্য থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- ২. সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আদালত।
- ৩. আয়ের ন্যায়সংগত বণ্টন।
- ৪. সামাজিক অগ্রগতির প্রেক্ষিতে ব্যক্তির স্বাধীনতা।
এই লক্ষ্যগুলো ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য সম্পূর্ণ নয়, তবে পর্যাপ্ত ফ্রেমওয়ার্ক (কাঠামো) সরবরাহ করার পাশাপাশি সেসব বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে যা ইসলামী ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্য নিরূপণ করে।
১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ইসলামের নৈতিক মূল্যমান:
“তোমরা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহ থেকে খাও এবং পান করো, এবং দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।” (আল-কোরআন, ২:৬০)
“হে মানবজাতি! এই পৃথিবীতে যা কিছু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তা তোমরা খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।” (আল-কোরআন, ২: ১৬৮)
“হে ইমানদারগণ! আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তাকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। এবং হালাল খাবার গ্রহণ করো, আর যে আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান এনেছো আর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকো।” (আল-কোরআন, ৫: ৮৭-৮৮)
কোরআনে এরকম অসংখ্য আয়াত আছে (২), যেগুলো অর্থনীতিতে কোরআনী মূলনীতি তুলে ধরে। ইসলাম আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহসমূহকে ভোগ করার জন্য মুসলমানদের তাগিদ দিয়ে থাকে এবং মুসলিম সমাজে বস্তুগত উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যাগত সীমারেখ বেঁধে দেয় না। বরং এটি বস্তুগত উন্নতিকেও একটি সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য করে।
“যখন নামাজ শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো।” (আল কোরআন, ৬২: ১০)
আল্লাহ যদি তোমাদের সামনে জীবিকা উপার্জনের কোনো সুযোগ করে দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এটিকে কাজে লাগাও যতক্ষণ না সেটি নিঃশেষ হয়ে যায়।(৩)
কোনো মুসলমান যদি একটি বৃক্ষরোপণ করে, অথবা জমি চাষাবাদ করে এবং সেখান থেকে যদি একটি পাখিও রিযিক আহরণ করে থাকে, তবে তা তার জন্য সাদকাহ হিসেবে আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে।(৪)
যারা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে জমিনে রিযিক অন্বেষণ করে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হয়, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে তাদের চেহারাগুলো পূর্ণ চাঁদের মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছে।(৫)
এমনকি ইসলাম আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে মানুষকে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের তাগিদ দিয়েছে (৬) এবং রাসূল (স.) বলেছেন যে, পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ নেই, যার জন্য আল্লাহ একটি প্রতিকার নির্ধারণ করে রাখেননি।(৭) সুতরাং, এটি সহজেই অনুমেয় যে মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ অন্যতম। কেননা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহকে মানবতার সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে মানুষ তার আগমনের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করতে পারে।
ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করেছে, এবং মানুষকে জীবিকা অন্বেষণের তাগিদ দিয়েছে।(৮) এটি থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, মুসলিম সমাজে আরেকটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেন কাজ করতে আগ্রহী মানুষ বা যারা কাজ খুঁজছে এরকম সকলেই তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী জীবিকা উপার্জনের উপায় খুঁজে পায়। যদি এটি সম্পন্ন না হয়, তবে মুসলিম সমাজ তার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণেও সক্ষম হবে না। কেননা, বেকার মানুষগুলো জীবনে অমানুষিক কঠিন পরিস্থিতির স্বীকার হবে যদি না সে অন্যের দয়া বা দানের উপর নির্ভর করে অথবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কিংবা কোনো অসদুপায় অবলম্বন করে। আর এসবগুলো পন্থাই; বিশেষ করে প্রথম দুটি ইসলামের প্রাণসত্তার সাথে বেমানান।
অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে জোর দেবার বিষয়টি মূলত ইসলামের মৌল বার্তা থেকেই উদ্ভূত। ইসলাম এসেছেই মানবতার জন্য আর্শীবাদস্বরূপ, মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য, দারিদ্র্য এবং কষ্টের মধ্যে নিপতিত করার জন্য নয়। কোরআন এ ব্যাপারে বলেছে-
“আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবতার জন্য রহমত হিসেবে।” (আল-কোরআন, ২১: ১০৭)
“হে মানুষ! তোমাদের জন্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসিহত এসে গেছে, এটি সে জিনিস যা অন্তরের সমস্ত রোগের নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও নিয়ামত।” (আল-কোরআন, ১০:৫৭)
“আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তা চান না।” (আল-কোরআন, ২: ১৮৫)
“আল্লাহ তোমাদের বোঝাকে লাঘব করতে চান। কেননা, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।” (আল-কোরআন, ৪: ২৮)
“আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দিতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পরিশুদ্ধ করতে এবং তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহকে পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ থাকো।” (আল-কোরআন, ৫:৬)
এ আয়াতগুলোর উপর ভিত্তি করে মুসলিম ফকীহগণ সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষের স্বার্থে উৎপাদন এবং মানুষের কষ্ট লাঘব করাই ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি।(৯) ইমাম গাযযালীর মতে, শরীয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন যা নির্ভর করে তাদের বিশ্বাসের নিরাপত্তা, জীবনের নিরাপত্তা, আকলের নিরাপত্তা, বংশের ও সম্পদের নিরাপত্তা এবং এই পাঁচটি জিনিসের নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় জনগণের স্বার্থরক্ষার কবচ এবং অনুমোদনযোগ্য।(১০) ইমাম ইবনে কাইয়ুম জোর দিয়ে বলেন, “শরীয়তের ভিত্তি হচ্ছে হিকমত এবং দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের কল্যাণ সাধন। এই কল্যাণ নির্ভর করে পরিপূর্ণ আদালত, মারহামাত, মাসলাহাত এবং হিকমতের উপর। যা কিছু আদালত থেকে জুলুমের দিকে মারহামাত থেকে রূঢ়তার দিকে, মাসলাহাত থেকে দুর্দশার দিকে এবং হিকমত থেকে মূর্খতা/ নির্বুদ্ধিতার দিকে নিয়ে যায়, শরীয়তে তার কোনো স্থান নেই। “(১১)
কিন্তু এই অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে গিয়ে একজন মুসলিম যদি তার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে, অন্যের ক্ষতি করে, আদালত থেকে দূরে সরে গিয়ে এবং কল্যাণের বিষয়কে মাথায় না রেখে সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তবে সে চরমপন্থায় চলে যায় এবং জাগতিক উন্নতির মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ইসলাম যেহেতু মানব জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে চায়, তাই কোরআন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে, “নামাজ শেষে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাকো যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।” (আল কোরআন, ৫৭ঃ ৭) অধিকাংশ আলেমদের মতে, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা বলতে বেশি বেশি ইবাদত করা বুঝায়নি, বরং এর মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আখলাকী জীবন যাপনঃ(১২) হালাল উপার্জন, সবধরনের হারাম পন্থাকে বর্জন এবং সম্পদকে আমানত হিসেবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে, যার হিসাব কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে দিতে হবে।(১৩) এই প্রেক্ষিতে হয়তো পৃথিবীর এবং এর কর্তৃত্বের অসারতা বিষয়ক কোরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো বোঝা সহজ হবে।(১৪) সূক্ষ্ম এ কথাটি আক্ষরিক অর্থে বলা হয়নি, বরং এটি আধ্যাত্মিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বিসর্জন না দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্বও অধিকার করা যায়, তাহলে তা ত্যাগ করার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। রাসূল (স.) বলেন, “যে আল্লাহকে ভয় করে তার সম্পদ উপার্জনে কোনো দোষ নেই।”(১৫) কিন্তু সেখানে যদি কোনো বিবাদ ঘটে থাকে, তাহলে মানুষের উচিত ততটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, যতটুকু সভাবে উপার্জন করা যায় সেটা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। কোরআন বলছে, “তাদের বলে দিন, ভালো এবং মন্দ কখনোই সমান নয়। যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাদের মোহিত করে। হে বোধসম্পন্ন লোকেরা। তোমরা আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো।” (আল কোরআন, ৫: ১০০) যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সন্তুষ্টির উপর ইসলামের চিরন্তন মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়, সে খুব সহজেই দুনিয়াবী সম্পদকে বিসর্জন দিতে পারে। কেননা, তার সামনে আছে রাসূলের বাণী, “এই পৃথিবীর মোহ তো কেবল শয়তানের কারসাজি”(১৬) এবং “যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে সে আখেরাতকে হারিয়ে ফেলে আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালোবাসে সে দুনিয়াতেও এর প্রতিদান লাভ করে। সুতরাং তোমরা ক্ষণস্থায়ী জিনিসের তুলনায় চিরস্থায়ী জিনিসকে বেছে নাও।”(১৭)
এভাবেই একদিকে বস্তুগত উন্নতির জন্য চেষ্টা করার তাগিদ দেয়া আবার একইসাথে এই জাগতিক প্রচেষ্টাকে একটি আখলাকী পাটাতনের উপর স্থাপন করার মাধ্যমে ইসলাম জাগতিক এবং নৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে যা জাগতিক চেষ্টাকে আধ্যাত্মিকতার অলংকারে সজ্জিত করে।
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ
“আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে তোমার আখিরাতের ঘর নির্মাণের চেষ্টা করো, কিন্তু দুনিয়াতেও তোমার অংশের কথা ভুলে যেও না। আর আল্লাহ তোমার উপর যেমন দয়া করেছেন, তুমিও মানুষের প্রতি তেমনি দয়া করো। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।” (আল-কোরআন, ২৮: ৭৭)
সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম তারাই যারা তাদের দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় বিষয়ে সচেতন।(১৮)
“তোমাদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ নয়, যে আখিরাতের জন্য দুনিয়াকে অস্বীকার করে, আবার সেও শ্রেষ্ঠ নয় যে দুনিয়ার জন্য আখিরাতকে অবহেলা করে। বরং তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়কেই প্রাধান্য দেয়।” (১৯)
এভাবে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিকের উপর জোর দেওয়ার বিষয়টি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, এ দুটো একত্রে পারস্পরিক শক্তির আধার হয়ে প্রকৃত মানবকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে। জীবনে এদুটো দিকের কোনো একটিকে অবহেলা করেই প্রকৃত মানবকল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়া সম্ভব নয়। যদি শুধু জাগতিক বিষয়গুলোকে লালন করা হয় এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়হীনতা বিরাজমান থাকে তাহলে সমাজে হতাশা, অপরাধ, মাদকাসক্তি, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক, ডিভোর্স, মানসিক অসুস্থতা, আত্মহত্যার মতো অসংগতিগুলো প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকবে যার সবগুলোই ব্যক্তিজীবনে মানসিক প্রশান্তির ঘাটতির কারণে হয়ে থাকে। আবার যদি শুধু আধ্যাত্মিক বিকাশকেই লালন করা হয়, তাহলে অনেকের কাছেই তা অবাস্তব এবং অকার্যকর হয়ে পড়বে। এভাবে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মধ্যে দ্বি-বিভাজন এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে যা সমাজের যাবতীয় মূল্যবোধকেই হুমকির দিকে ঠেলে দিতে পারে।
অন্য দুটি ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদে আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত জীবনের এই মেলবন্ধন অনুপস্থিত। কেননা, এ দুটি মতবাদই মূলত সেকুলার এবং অনৈতিক বা নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ। উৎপাদনশীল প্রযুক্তি এবং জীবনমানের উন্নতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের ভূমিকাকেও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এই দুটি ব্যবস্থাই মানবজীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেছে।
২. সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং আদালত:
“হে মানবজাতি। আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে মুত্তাকীগণই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন।” (আল কোরআন, ৪৯:১৩)
“তোমাদের রব একজন। তোমরা সবাই আদম থেকে এসেছো, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। শ্রেষ্ঠত কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে হয়। অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর কালোর উপরও সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (২০)
“মানবজাতির সূচনা হয়েছে আদম এবং হাওয়ার মাধ্যমে, আর তোমরা সবাই তাদের বংশধর। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ কারও কাছে তার বংশ বা গোত্র পরিচয় জানতে চাইবেন না। বরং সেদিন আল্লাহর সামনে সেই সবচেয়ে সম্মানিত হবে যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।
ইসলাম এমন এক সমাজ বিনির্মাণের কথা বলে যেখানে সকল মানুষ একই স্রষ্টার দ্বারা আবদ্ধ থাকে। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, এটি কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে আবদ্ধ নয়, আর এক দম্পতি থেকে সৃষ্ট একই পরিবারের সদস্যের মতো ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার বন্ধনে না কোনো জাতি, গোত্র বা বর্ণে, বরং যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এই ভ্রাতৃত্ব সমগ্র মানব জাতিকে এক করে। কোরআনের ভাষ্যমতে, “বলুন, হে মানুষ। আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।” (আল কোরআন, ৭:১৫৮) আর রাসূলুল্লাহ (স.) জোর দিয়ে বলেন, “আমি তোমাদের মধ্যে সাদা-কালো সবার জন্যই সমানভাবে প্রেরিত হয়েছি।”
আর স্বাভাবিকভাবেই এই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পূর্বশর্ত হলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে, যারা একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও একই বিশ্বাসের বন্ধনেও আবদ্ধ যাকে কোরআন ‘দ্বীনি ভাই’ (আল কোরআন, ৯:১১) (২৩) এবং ‘পরস্পরের প্রতি রহমশীল’ (আল কোরআন, ৪৮:২৯) হিসেবে অভিহিত করেছে। রাসূল (স.) বলেন,
“সমগ্র মানবজাতি আল্লাহর পরিবারভুক্ত আর তার কাছে তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সেই বেশি প্রিয় যে সর্বশ্রেষ্ঠ।”(২৪)
“জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি রহমশীল হও, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি রহমশীল হবেন।”(২৫)
“পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা এবং সহানুভূতির ক্ষেত্রে আপনি মুসলমানদের একটি দেহের মতো পাবেন। এর এক অংশ আঘাত পেলে সারা দেহে সে ব্যথা অনুভূত হয়। “(২৬)
“এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে কখনো তার প্রতি অন্যায় আচরণ করে না, কখনো বিপদে তাকে একাকী ছেড়ে দেয় না কিংবা তাকে তাচ্ছিল্য করে না। (২৭)
“ইসলামের এই ভ্রাতৃত্বের ধারণা থেকেই ইসলাম আদালতের উপর এত গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি কোরআনে বলা হয়েছে, নবীগণের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো দুনিয়ার বুকে আদালত প্রতিষ্ঠা।” (আল-কোরআন, ৫৭: ২৫)
আদালতবিহীন ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে কোরআন ঘোষণা করেছে- “তাদের জন্যই জন্যই রহমত এবং হেদায়াত যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জলুমের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেনি।” (আল-কোরআন, ৬:৮২)
সুতরাং ইসলাম মুসলমানদের আদালতের ব্যাপারে নিছক উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে তাগিদ দিয়ে গেছে, “আল্লাহ তোমাদের সৎকাজের এবং আদালত কায়েমের আদেশ দিচ্ছেন” (আল কোরআন, ১৬:৯০) এবং “যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করো, ইনসাফের ভিত্তিতে করো।” (আল কোরআন, ৩:৫৮)
ইসলামে ইনসাফ এবং আদালতের গুরুত্ব এত বেশি যে, ন্যায়পরায়ণ হওয়াকে মুত্তাকী এবং মুমিন হবার শর্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে-
“হে ঈমানদারগণ। আল্লাহর জন্য তোমরা সত্যের উপর কায়েম থাকো এবং ইনসাফের সাক্ষী হও। কারও প্রতি দুশমনি যেন তোমাদেরকে ইনসাফ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। ইনসাফ করো। এটিই তাকওয়ার কাছাকাছি। আল্লাহকে ভয় করো। নিশচয়ই তোমরা যা কিছু করো, সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি খবর রাখেন।” (আল কোরআন, ৫:৮)
এমনকি ইনসাফের ক্ষেত্রে যদি কারও নিজের বা তার কাছের মানুষদের ক্ষতি হয়ে যায়, তবুও তা কায়েম করতে বলা হয়েছে-
“এবং যখন তোমরা কথা বলো, ইনসাফের সহিত বলো, যদি তা তোমাদের নিকটাত্মীয়দের বিপক্ষেও যায়।” (আল কোরআন, ৬: ১৫২)
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে বা তোমাদের পিতামাতা বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়, সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক। আল্লাহ সবার উত্তম হেফাজতকারী। কাজেই নফসের প্রতারণায় ইনসাফ থেকে দূরে সরে যেও না। যদি তোমরা (সত্য থেকে) বিচ্যুত হও বা ইনসাফ থেকে দূরে সরে যাও তাহলে মনে রেখো আল্লাহ তোমাদের সকল তৎপরতার খবর রাখেন।” (আল কোরআন, ৪: ১৩৫)
এ বিষয়টি আরো বিস্তারিত অনুধাবনের জন্য আমরা ইসলামের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি।
সামাজিক সুবিচার:
ইসলাম যেহেতু সমগ্র মানবতাকে একটি পরিবার হিসেবে বিবেচনা করে তাই আল্লাহর আইনে সকল মানুষই সমান। এখানে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, সাদা-কালোর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। গোত্র-বর্ণ বা সামাজিক পদমর্যাদার জন্য মানুষের মধ্যে কোনো বিভাজন করা হয় না। এখানে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি হলো আখলাক, যোগ্যতা, এবং মানবতার কল্যাণে ভূমিকা। পয়গাম্বর (স) বলেন-
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের কাজ।”(২৮)
“তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যার আখলাক সর্বোত্তম।”(২৯)
আল্লাহর রাসূল (স.) সেসব মানুষ এবং জাতির জন্য ধ্বংসের সতর্কবাণী করেছেন, যারা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভেদেভেদ এবং অসাম্যের সৃষ্টি করে।
“তোমাদের পূর্বের অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছিলো, কারণ যখন তাদের মধ্যে উচ্চবিত্তরা চুরি করতো, তাদের কোনো শাস্তি দেয়া হতো না। বিপরীতে নিম্নবিত্তের উপর শাস্তি কার্যকর হতো। খোদার কসম। যদি আমার আদরের দুলালী ফাতিমাও চুরি করতো আমি তার হাত কেটে দিতে দ্বিধা করতাম না।”(৩০)
“যদি কেউ কোনো মুসলিম নারী অথবা পুরুষকে তার দারিদ্য বা অনটনের জন্য তাচ্ছিল্য বা উপহাস করে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। “(৩১)
ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) তার গভর্ণর আবু মুসা আল আশয়ারী (রা.)-এর কাছে চিঠি লেখেন এই মর্মে-
“সকল মানুষকে সমানভাবে দেখবে যেন দরিদ্ররা তোমার আদালত থেকে নিরাশ না হয়, আবার ধনীরা তোমার কাছে কোনো বাড়তি সুবিধা আশা না করে।”(৩২)
ইসলামের প্রথম চার খলীফার শাসনামলেই আদালতের এই রূহ সর্বত্র বিদ্যমান ছিলো। কিছুটা শিথিল হলেও পরবর্তী শাসকরাও এটির অনুসরণ করেছেন, বিভিন্ন ঘটনায় যার নজির পাওয়া যায়। খলীফা হারুন উর রশিদের সময়কার বিখ্যাত ইমাম কাজী আবু ইউসুফের খলীফাকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠির বক্তব্য থেকে আমরা যেমনটি দেখতে পাই, “সকলের প্রতি সমান আচরণ করুন, হোক সে আপনার নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী” এবং “আপনার রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করবে কোরআনের আইন কায়েম করা এবং অন্যায় ও জুলুম নিরসন করার মধ্যে। “(৩৩)
অর্থনৈতিক সুবিচার:
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক সুবিচারের ধারণাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না এর সাথে অর্থনৈতিক সুবিচারের মেলবন্ধন ঘটে; যদি না সমাজে প্রত্যেকেই তার অবদানের মূল্য পেয়ে থাকে এবং একে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কোরআন মুসলমানদের বলে, “কখনো অন্যের পাওনা আটকে রেখো না।” (আল কোরআন, ২৬: ১৮৩)।(৩৪) ফলে প্রত্যেকে তার ন্যায্য পাওনা পেয়ে যাবে এবং কেউ অন্যের অংশ হস্তগত করে কাউকে বঞ্চিত করবে না। রাসূল (স.) উম্মতকে বারবার সতর্ক করেছেন, “তোমরা জুলুমের ব্যাপারে সচেতন হও। কেননা, জুলুম কেয়ামতের মাঠে ঘোর অন্ধকারের মতো হবে।”(৩৫) শোষণ এবং জুলুমের ব্যাপারে এরূপ সতর্কবার্তার কারণ হলো সমাজে প্রতিটি মানুষের জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন যা ইসলামের মূল লক্ষ্য। হোক সে ভোক্তা, উদ্যোক্তা, বণ্টনকারী কর্মচারী অথবা মালিক) অধিকার সংরক্ষণ এবং এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, শ্রমিক বা কর্মচারী এবং মালিকের সম্পর্কের ব্যাপারে আদালতের ভিত্তিতে ইসলাম সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। একজন শ্রমিক মালিকের জন্য তার কর্মচারীকে বঞ্চিত করা ন্যায়সংগত নয়। রাসুল (স.) ইরশাদ করেন, দ্রব্য উৎপাদনে তার অবদানের জন্য ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকারী এবং একজন মুসলিম “ঠিন ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর বিরাগভাজন হবে; যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তার কৃত ওয়াদা পূর্ণ না করেই মৃত্যুবরণ করেছে, যে ব্যক্তি কোনো মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে এবং মূল্য ভোগ করে, আর যে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে তার উৎপাদিত পণ্য ভোগ করে, কিন্তু তার মজুরি শোধ করে না।”(৩৬) এই হাদীসে একজন মুক্ত মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা এবং শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি আদায় না করাকে পাশাপাশি রাখার মাধ্যমে ইসলাম এ বিষয়ে কতটা কঠোর তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।
এখানে শ্রমিকের ‘ন্যায্য মজুরি’ এবং ‘শ্রমিক শোষণ’ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, সেটিকে আমাদের কোরআন এবং সুন্নতের আলোকে বুঝতে হবে। মার্কসের মতো ইসলাম শ্রম ব্যাতীত অন্য কোনো ফ্যাক্টর দ্বারা উৎপাদনের স্বীকৃতি দেয় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই ইসলামে শ্রমিকের মজুরি এবং শ্রমিক শোষণের ধারণাটিও মার্কসের প্রস্তাবিত উদ্বৃত্ত মূল্যের (suplus value) ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাত্ত্বিকভাবে এরূপ বক্তব্য আসতে পারে যে, শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের সমপরিমাণ মূল্যই শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি। কিন্তু বাস্তবে এভাবে মূল্য নির্ধারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য তাই এই তত্ত্বের কার্যকরীতাও যৎসামান্য। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে সর্বনিম্ন এবং আদর্শ মজুরি সম্পর্কে একটা গুণগত ধারণা পাওয়া যায়, যা অনেক বেশি বাস্তবিক। রাসূল (স.) বলেন, “একজন শ্রমিকের (নারী অথবা পুরুষ) ন্যূনতম মজুরি এমন হবে, যা দিয়ে সে পরিমিতভাবে তার খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করতে পারবে এবং তাকে দিয়ে কখনো তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ করানো যাবে না।”(৩৮) সুতরাং এই হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি এমন হওয়া চাই যা তার এবং তার পরিবারের মানসম্মতভাবে ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত হয় এবং এজন্য তাকে সাধ্যের অতিরিক্ত চাপ নিতে না হয়। মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক মান রক্ষার্থে সাহাবীরা এভাবেই শ্রমিকের মজুরি দিয়েছিলেন। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা) বলেন, “অদক্ষ নারী শ্রমিকদের তার বৃত্তিমূলক কাজে অতিরিক্ত চাপ দিওনা, তাতে করে সে হয়তো অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। তোমার অধীন পুরুষদেরও অতিরিক্ত কাজের চাপ দিও না। তাহলে সে হয়তো চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। তোমার অধীনস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, তাহলে তোমার রব তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। আর মনে রাখবে, তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত।”(৩৯)
আরেকটি হাদীস থেকে আদর্শ মজুরি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া। আদর্শ মজুরি এমন হবে যাতে কর্মচারী তার মালিকের সমমানের খাদ্য এবং বস্ত্রের আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়।
“তোমাদের কর্মচারীগণ তোমাদের ভাই। যদিও আল্লাহ তাদের তোমাদের অধিনস্ত করেছেন। সুতরাং যে তার ভাইকে অধীন হিসেবে পায় সে যেন তাকে তাই খেতে দেয় যা “তোমাদের কর্মচারীগণ তোমাদের ভাই। যদিও আল্লাহ তাদের তোমাদের অধিনস্ত সে নিজে খায়, এবং তাই পরতে দেয়, যা সে নিজে পরিধান করে।”(৪০)
সুতরাং ন্যায্য মজুরি ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হতে পারবে না এবং এর কাক্সিক্ষত মান আদর্শ মজুরির যথাসম্ভব কাছাকাছি হবে যাতে করে আয়ের বৈষম্য যতটা সম্ভব কমানো সুতরাং ন্যায্য মজুরি ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হতে পারবে না এবং এর কাঙ্ক্ষিত মান যায়। এর ফলে শ্রমিক ও মালিকের জীবনমানের মধ্যেকার যে ব্যবধান, যা সমাজে দুটি ভিন্ন শ্রেণির সৃষ্টি করে এবং ফলশ্রুতিতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা নষ্ট হয়ে যায়, যা মুসলিম সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি তাতেও একটা সেতুবন্ধন রচিত হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো ‘ন্যূনতম’ এবং ‘আদর্শ’ এদুটি সীমারেখার মধ্যে চাহিদা (demand) এবং যোগানের (supply) এর মধ্যকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাত্রা, মসলিম সমাজের আখলাকী অবস্থান, এবং রাষ্ট্রের বৈধ আইনের ভিত্তিতে শ্রমিক/কর্মচারীর প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হবে।
ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং আদর্শ মজুরিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ইসলাম এ বিষয়েও জোর দিয়েছে যে, শ্রমিকদের দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো যাবে না, যাতে তার শরীর ভেঙ্গে পড়ে বা সে তার পরিবারের সাথে সময় কাটাতে না পারে।(৪১) যদি তাদেরকে সাধ্যের চেয়ে বেশি কোনো কাজ করতে হয় তাহলে অবশ্যই পর্যাপ্ত সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে অতিরিক্ত চাপ না নিয়েই কাজটি করতে পারে। ইতোপূর্বে শ্রমিকদের ভাই হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়ে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে রাসূল (স.) আরও বলেছেন, “…এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিও না। যদি সেটা দিয়ে থাকো, তাহলে তাদের সাহায্য করো। “(৪২)
এই হাদীস থেকে ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী সর্বাধিক শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ, উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ঝুঁকির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন এর প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব।
মালিকের কাছ থেকে এসব আচরণ নির্ধারণের করার পাশাপাশি আদালতের স্বার্থে ইসলাম কর্মচারীর উপরও কিছু নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করেছে। প্রথম কর্তব্য হলো, নিজের সর্বোচ্চ যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে এবং যথাযথ গুরুত্ব ও সচেতনতার সাথে যত্ন দিয়ে কাজ করা। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তোমাদের উপর কর্তব্যপরায়ণতাকে ফরয করেছেন”(৪৩) এবং “এবং তিনি চান যে তোমরা যখন কোনো কাজ করো, সেটি যথাযথভাবে সম্পাদন করো।”(৪৪)
সুতরাং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য যার উপর ইসলাম এতটা জোর দিয়েছে সেটি নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই কর্মচারীদেরও কর্মদক্ষ হতে হবে। অন্য একটি ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, “যে কর্মচারী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী হবার পাশাপাশি, তার মালিকের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ দায়িত্ব এবং আনুগত্যের সাথে সম্পন্ন করে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। “(৪৫)
কর্মচারীদের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, বিশ্বস্ত এবং আস্থাভাজন হওয়া। কোরআনের ভাষ্যমতে, শ্রেষ্ঠ কর্মচারী সে যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সৎ। (আল কোরআন, ২৮ : ২৬)। এবং রাসূল (স.) বলেন, “যখন কাউকে কোনো কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং তার বিনিময়ে তার জীবিকা সরবরাহ করা হয়, তখন এর চেয়ে বাড়তি যা কিছু সে অর্জন করে তাই তার জন্য অন্যায়/হারাম।”(৪৬)
অতএব, মালিকের উপর অনেকগুলো দায়িত্ব অর্পণ করার পাশাপাশি ইসলাম শ্রমিকের কাছেও তার কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততা প্রত্যাশা করে। এবং এর লক্ষ্য হলো যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের জন্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা।
৩. সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বণ্টন:
ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের অনন্য এবং প্রগাঢ় প্রতিশ্রুতি ও প্রাণসত্তার সাথে আয় ও সম্পদের অন্যায় বণ্টন খাপ খায় না। বরং ইসলাম সারা পৃথিবীতে যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ধন-সম্পদের অন্যায় বণ্টনের ফলে তা কেবল ধ্বংসই হয়। এছাড়াও, কোরআনের বর্ণনামতে যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ “আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবতার জন্য উপহারস্বরূপ।” (আল কোরআন, ২: ২৯)। তাই এ সম্পদ কিছু ব্যক্তির মধ্যে পুঞ্জিভূত থাকার কোনো মানে হয় না। তাই ইসলাম ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের উপর জোর দেয় এবং ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে আয় ও সম্পদের একটি পুনঃবণ্টননীতি প্রণয়ন করে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মানবিক এবং সম্মানজনক জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত হয়। মূলত এর মাধ্যমে ইসলাম “পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে” (আল কোরআন, ২: ৩০) মানুষের মর্যাদাকে সবকিছুর উপরে সমুন্নত করতে চায়। কোনো মুসলিম সমাজ যদি এই রকম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটি তার ধারণ করা নামের অযোগ্য বলে গণ্য হবে। যেমনটা রাসূল (স.) বলেছেন, “সে প্রকৃত মুসলিম নয়, যে পেট পুরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।”(৪৭)
ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এক জনসভায় ইসলামের আদালতপূর্ণ পুনঃবণ্টন নীতির ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন, “সমাজের সম্পদে প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার রয়েছে। এমনকি আমি নিজেও এর চেয়ে বেশি গ্রহণ করতে পারবো না। আল্লাহ যদি আমাদেরকে হায়াত দান করেন, তাহলে আমরা শীঘ্রই দেখতে পাবো যে, এমনকি সান’আ পর্বতের পাদদেশে একজন রাখালও তার ন্যায্য অংশ লাভ করবে। “(৪৮)
খলীফা আলী (রা.) এই বিষয়ে জোর দিতেন যে, “আল্লাহ ধনীর জন্য এটা বাধ্যতামূলক করেছেন যে সে দরিদ্রের প্রয়োজন পূরণ করবে। যদি দরিদ্ররা ক্ষুধার্ত অথবা পোশাকহীন বা দুর্দশার মধ্যে থাকে, তার মানে হলো ধনীরা গরীবকে তার অংশ থেকে বঞ্চিত করেছে। অতএব, আল্লাহ অবশ্যই তাকে এর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং শান্তি দিবেন।”(৪৯) ফিকহবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের দায়িত্ব, এবং বিশেষ করে এ দায়িত্ব ধনীদের উপর ন্যস্ত। যদি স্বচ্ছল ব্যক্তিরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে রাষ্ট্র তাদের এটি করতে বাধ্য করতে পারবে।(৫০)
ইসলামের পুনঃবণ্টন ব্যবস্থা তিন ধাপে বিভক্ত। প্রথমত, ইসলামী ব্যবস্থায় বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং তার ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, যাকাতের মাধ্যমে ধনীদের সম্পদ গরীবের (যারা কাজ করতে অক্ষম অথবা দাস) মধ্যে পুনঃবণ্টন করা। যাতে কোরআনের এ আয়াতের সত্যতা কায়েম হয়, “সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই পুঞ্জিভূত না থাকে।” (আল কোরআন, ৫৯ঃ ৭)। তৃতীয়ত, মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে মিরাসের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন যা সমাজে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনকে শক্তিশালী ভিত এর উপর স্থাপন করে।
ইসলামের এই ইনসাফপূর্ণ বণ্টননীতি এবং অর্থনৈতিক সুবিচারের অর্থ এই নয় যে, সমাজে যার অবদান যাই হোক না কেন প্রত্যেকে সম্পদের সমান অংশ লাভ করবে। কেননা, সমাজে সকল মানুষের চরিত্র, সক্ষমতা এবং সমাজের প্রতি অবদান সবার সমান নয়। তাই ইসলাম যাকাতের মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য জীবনযাত্রার সুষম মান নিশ্চিত করার পর প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও সমাজে তার অবদান অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়াকে সমর্থন করে। ইসলাম এই ইনসাফপূর্ণ বণ্টননীতিতে এতটাই জোর দিয়েছে যে, কোনো কোনো মুসলমান মনে করে যে, ইসলাম সম্পদের সমবণ্টনের কথা বলেছে। রাসূলের অন্যতম সাহাবী আবু যর (রা.) এই মত পোষণ করতেন যে, একজন মুসলিমের জন্য তার পরিবারের ভরণপোষণের অতিরিক্ত সম্পদ রাখা জায়েয নয়। কিন্ত রাসূল (স.)-এর অধিকাংশ সাহাবীই তার এই চরমপন্থার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।(৫২) তবে, আবু যর (রা.) ও আয়ের সমবন্টনের পক্ষে ছিলেন না, বরং তিনি জমাকৃত সম্পদের সমবণ্টনের পক্ষে ছিলেন। অর্থাৎ, তার মতে ব্যক্তির নিজের প্রকৃত ব্যায়ের পর উদ্বৃত্ত সম্পদ সে তার দারিদ্র্য-পীড়িত ভাইদের কল্যাণে ব্যয় করবে। ইনসাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার পক্ষাবলম্বন সত্ত্বেও, আলেমগণ সকলে এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, একজন মুসলিম ন্যায়সংগত উপায়ে উপার্জন করে, এবং তার আয় ও সম্পদ থেকে যাকাত আদায় ও অন্যান্য ভূমিকার মাধ্যমে সমাজের প্রতি তার ফরয দায়িত্ব পালন করার পরও তার ভাইয়ের কল্যাণে আরো সম্পদ ব্যয় করার মধ্যে কোনো বাধা নেই। (৫৩) প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী ব্যবস্থার আলোকে যদি উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম মেনে চলা হয়, শ্রমিক এবং মজুরের মধ্যে আদালতপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সম্পদ ও আয় বণ্টনের ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং ইসলামের মিরাস ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহলে মুসলিম সমাজে আয় ও সম্পদের স্কুল অসাম্য বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়।
৪. সামাজিক অগ্রগতির সাপেক্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতা:
ইসলামী মূল্যবোধের অন্যতম স্তম্ভ হলো এই বিশ্বাস যে, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং সে আল্লাহ ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী নয়। (আল কোরআন, ১৩: ৩৬, ৩১: ২২) এটি ইসলামে মানুষকে সব ধরণের জিঞ্জির থেকে মুক্তির অনন্য দলীল। কোরআন রাসূলের (স.) নবুয়তী মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছে “মানুষের গলা থেকে সকল প্রকার দাসত্বের শৃঙ্খল খুলে ফেলা”-কে। (আল কোরআন, ৭: ১৫৭) এটি ইসলামের সেই রূহ যা খলীফা উমরকে (রা.) এই কথা বলতে প্রবৃত্ত করেছে যে, “তোমরা মানুষকে দাস বানাচ্ছো, অথচ তার মা তাকে স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছেন।”(৫৪) শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যেও এই একই প্রাণসত্তার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় যখন তিনি বলেন, “আল্লাহ তোমাকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন, তাই কখনো পরাধীন হয়ো না।”(৫৫)
যেহেতু মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাই কারও, এমনকি রাষ্ট্রেরও তার গলায় পরাধীনতার জিঞ্জির পরাবার অধিকার নেই। ফিকহবিদদের মধ্যে এই বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, একজন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, এবং মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির উপর কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে না। হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন, “একজন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির উপর কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে না, এমনকি যদি সে ব্যক্তিগত ক্ষতি, যেমন- সে কোনো লাভ ছাড়া বেহিসাবে অর্থ ব্যয় করতে থাকে।” এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার মানে হলো তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করে তাকে পশু জ্ঞান করা। এর মাধ্যমে যে ক্ষতি হয়, তার ঐ সম্পদের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি। এবং একটা ছোট ক্ষতির মোকাবেলায় বড় ক্ষতিকে সমর্থন করা যায় না।(৫৬)
এই মতদ্বৈধতা তখনি কার্যকর হয়, যখন কোনো ব্যক্তি ইসলামের সীমারেখার মধ্যে থেকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি সাধন করে থাকে। কিন্তু যদি কেউ অন্যের কোনো ক্ষতি করে থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে বাধা দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কোনো ভিন্নমত নেই। ইমাম আবু হানিফার ভাষায়, “একজন অদক্ষ চিকিৎসক, একজন দায়িত্বহীন বিচারক, অথবা একজন দেউলিয়া নিয়োগকর্তাকে নিয়ন্ত্রণ করো, কেননা, এর মাধ্যমে ছোট ক্ষতির বিপরীতে বড় ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারবে।”(৫৭) ইসলামে সামাজিক উন্নতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রাথমিক গুরুত্ব সত্ত্বেও এটি সামাজিক দায়বদ্ধতামুক্ত নয়।
অপরাপর ব্যক্তি এবং সমাজের সাথে ব্যক্তির অধিকারকে একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দাঁড় করানোর জন্য ফকীহগণ নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন(৫৮):
- ব্যক্তিস্বার্থের উপর সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ প্রাধান্য পাবে।
- যদিও ‘দুর্দশা লাঘব করা’ এবং ‘কল্যাণের প্রসার’ দুটিই শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত, প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টি প্রাধান্য পাবে।
- ছোট ক্ষতির মোকাবেলায় বড় ক্ষতিকে সমর্থন দেয়া যাবে না। অথবা ক্ষুদ্রতর কল্যাণের জন্য বৃহত্তর কল্যাণ ত্যাগ করা যাবে না। বিপরীতে, বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে ছোট ক্ষতি অথবা বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ক্ষুদ্রতর কল্যাণ ত্যাগ করা অনুমোদনযোগ্য।
কাজেই, ইসলামের নৈতিক সীমার মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ততক্ষণ প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ এটি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী না হয় এবং অন্যের অধিকার হরণ করা না হয়।
ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:
ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের দৃঢ় ভিত্তির উপর বস্তুগত উন্নতিকে স্থাপন করার মধ্য দিয়ে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের পাটাতন নির্মিত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র থেকে ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায়, এর মৌলিক কাঠামোও এই দুটি ব্যবস্থা থেকে আলাদা। তাই ইসলামের সাথে এই দুটি মতবাদ এবং ব্যবস্থার সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে তা কেবল তিনটি ব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণায়-ই পর্যবসিত করবে। তাছাড়া, ইসলামী ব্যবস্থা নিরন্তর মানবীয় ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার, আয়ের ন্যায্য বণ্টন এবং সামজিক অগ্রগতির সাথে প্রাসঙ্গিক ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি নিবেদিত। এই নিবেদন অবশ্যই আধাত্মিকতা কেন্দ্রিক এবং ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের কারুকার্যে চমৎকারভাবে সজ্জিত। অন্যদিকে আধুনিক পুঁজিবাদের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে এককেন্দ্রিক দর্শন। এর সামগ্রিক দর্শন সামজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার এবং আয়ের ন্যায়সংগত বন্টনের লক্ষ্যে নির্মিত হয়নি এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আধ্যাত্মিক প্রাণসত্তার বদলে এটি দলীয় স্বার্থচিন্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত হয়। আবার সমাজতন্ত্র যদিও দাবি করে যে, এটি একটি মৌলিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, একদিকে মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি উদাসীনতা এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত আদালত, নিরপেক্ষ বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার অভাব, অন্যদিকে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অস্বীকারের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা এবং আত্মপরিচয়ের প্রতি অবমাননার ফলে তাদের এই দাবি অর্থহীন হয়ে পড়ে।
ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি ইসলামের অঙ্গীকার এটিকে পরিষ্কারভাবে সমাজতন্ত্র অথবা অন্য যেকোনো মতবাদ ও ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে তোলে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি, যা ব্যবসায়িক লেনদেনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত, তা মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সকল ধারায় অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত।(৫৯) “হে ঈমানদারগণ! কখনো একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। ব্যবসায়িক লেনদেন করো পারস্পরিক সম্পত্তির ভিত্তিতে” (আল কোরআন, ৪: ২৯)। কোরআনের এ আয়াত থেকেই মূলত এই মূলনীতিটি এসেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) এরও এরকম একটি হাদীস আছে, “মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও। কেননা, আল্লাহ মানুষকে একে অন্যের মাধ্যমে রিযিক দিয়ে থাকেন।”(৬০) জীবন এবং স্বাধীনতার এই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে গ্রুপের অধীনে থাকে যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যে কেউ পারে যদি উৎপাদন ও বণ্টনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যক্তি মালিকানা অথবা স্বেচ্ছাসেবী কেনাকাটা করতে পারে। ইসলাম এন্টারপ্রাইজের পাশাপাশি উদ্যোক্তা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে সামনে এনেছে যা সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর, পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ও ব্যবহার, এবং যাকাত ব্যবস্থা ও মিরাসের সাথে সংশ্লিষ্ট মূলনীতিগুলো কোরআন, সুন্নত ও ফিকহের কিতাবাদীতে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে।
দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ইসলামের ইতিহাসে বরাবরই এই মূলনীতিগুলো সার্বজনীনভাবে সমুন্নত ছিলো এবং ব্যতিক্রমগুলোকে ইসলামের মূলধারার সাথে কখনোই মেলানো যাবে না এবং এগুলো ইসলামী ব্যবস্থার নীতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।
সুসংগঠিত বাজার ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র দিক। কেননা, একদিকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এটি ছাড়া অকার্যকর হয়ে পড়বে, অন্যদিকে এটি ভোক্তাদের চাহিদা ও পছন্দের পণ্য ও দাম সম্পর্কে মত প্রকাশের এবং উদ্যোক্তাদের স্বাধীনভাবে নিজস্ব পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ করে করে দেয়।
ইসলাম মুনাফা লাভের প্রেরণাকে সমর্থন করে, যেটি যেকোনো ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে কোনো এন্টারপ্রাইজ পরিচালনার পূর্বশর্ত। চার মাযহাবের উপর ফিকহী গবেষণার জন্য বিখ্যাত আলেম আল-জাযিরী বলেন, “ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পরস্পরের লাভবান হওয়াকে অনুমোদন করে।” যদি ফকীহগণ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মুনাফা অর্জনকে নিষিদ্ধ করে দেয় কিংবা একেবারেই কোনো সীমা বেঁধে না দেয়-দুটোই ইনসাফহীনতায় পর্যবসিত হতে পারে। তাই তিনি এর মধ্যে সীমারেখা আরোপ করেন। এছাড়াও তিনি প্রতারণা, ভণ্ডামী এবং কোনো পণ্য অন্যায়ভাবে ভোগ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। (৬১)
এই বিধানের কারণ হলো, মুনাফা লাভের আগ্রহ আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার প্রেরণা যোগায়। সম্পদের কার্যকর বণ্টন যেকোনো সতেজ-সুস্থ সমাজের চালিকাশক্তি। কিন্তু, মুনাফাকে একটি উপকরণের পরিবর্তে মৌলিক উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করার চিন্তা থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। তাই ইসলাম এক্ষেত্রে কিছু নৈতিক সীমা বেঁধে দিয়েছে যেন মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের বাসনা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী না হয় এবং ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার এবং আয় ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত না করে।
এন্টারপ্রাইজ ও ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা এবং মুনাফা লাভকে অনুমোদন দেবার মধ্য দিয়ে ইসলামী অর্থনীতি এন্টারপ্রাইজের স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদের সদৃশ হয়ে যায় না। দুটোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান দুটো প্রধান কারণে। প্রথমত, ইসলামী ব্যবস্থায় যদিও সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, তবু এটি বান্দার কাছে আল্লাহপ্রদত্ত আমানত। কারণ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কাছে এগুলো আমানত।
কোরআনের ভাষ্যমতে-
“আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর অধীন।” (২: ২৮৪)
“(হে নবী।) এদের জিজ্ঞেস করো, এ যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কার (মালিকানাধীন)? তারা বলবে, এ সবকিছুই আল্লাহর।” (২৩:৮৪-৮৫)
“আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে দান করো।” (২৪:৩৩)
দ্বিতীয়ত, মানুষ যেহেতু পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা এবং সে যে সম্পত্তির মালিক তা তার কাছে আল্লাহর দেওয়া আমানত, তাই সে আমানতের শর্তাবলি মানতে বাধ্য। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে সে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধের সীমারেখা, বিশেষ করে হালাল-হারাম, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার, আয় ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, সামগ্রিক কল্যাণকামিতার মধ্যে আবদ্ধ। তাই সে যে সম্পদ উপার্জন করবে তা হালাল উপায়ে করতে হবে এবং এটিকে সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, “এই সম্পদ নিঃসন্দেহে তাজা এবং সুমিষ্ট। কিন্তু যে এটিকে ন্যায়সংগতভাবে অর্জন করে, তার জন্য। আর যে এটিকে অন্যায় পন্থায় অর্জন করে, তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো যে খেতেই থাকে, কিন্তু কখনো তৃপ্ত হয় না। (৬২)
এখন, এই দুটো বিষয় কী পার্থক্যের সৃষ্টি করে? এটি পরিষ্কার হবে যদি পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাজার ব্যবস্থা নিয়ে একটু আলোচনা করা যায়।
প্রথমত, পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থাকে গণভোটের সাথে তুলনা করা যায় যেখানে একজন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যয়কৃত প্রতিটি মুদ্রা একেকটি ব্যালট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং সকলের সব ব্যালটের ভিত্তিতে মোট জাতীয় সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় হবে। যদি দুধের পরিবর্তে লিকারের পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় হয়ে যায়, তার কারণ হলো, লিকারের চাহিদা জনগণের মধ্যে বেশি। তাই জাতীয় সম্পদ থেকে লিকার উৎপাদনে ব্যয়ের অংশ বেশি। এভাবে মূল্য ব্যবস্থায়, প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম (optimum) বণ্টন নিশ্চিত হয়। বাজার ব্যবস্থা এখানে নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ বিচারকের আসনে আসীন হয় এবং কেবলমাত্র ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কখনো নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হতে পারে না। ইসলামে সম্পদের বরাদ্দ তখনই সর্বোত্তম হিসেবে গণ্য হয়, যদি তা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী না হয় এবং ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী হয়। প্রকৃত ইসলামী সমাজে এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা নেই এবং রাষ্ট্র সেখানে নিষ্ক্রিয় দর্শক হতে পারে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র তার জনগণকে ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে থাকে, ফলে তাদের পছন্দও সে আদলে হয়ে থাকে এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যের আলোকে পরিচালনা করে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে সম্পদের বণ্টন ইসলামী আদর্শের আলোকে হচ্ছে কিনা এ রায় কে দিবে? এটি কোনো গীর্জার হায়ারার্কির কর্তৃত্বে হবে না, কেননা ইসলাম এরকম কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেনি। তাই ইসলামের আবহমান রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে গণতান্ত্রিক পন্থায় যেকোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
দ্বিতীয়ত, যেহেতু প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় মুদ্রাকে ব্যালটের সাথে তুলনা করা হয়, তাই ব্যক্তিভেদে সবার চাহিদা এবং জরুরতকে মুদ্রার মূল্যে বিবেচনা করা হয়। যদি দুজন ব্যক্তি কোনো পণ্য বা সেবার জন্য সমান অর্থব্যয়ে প্রস্তুত থাকে, তবে ধরে নেওয়া হয় তাদের দুজনের কাছে এই জিনিসটির চাহিদা বা জরুরত একই। এমনকি এ ধরণের তুলনা যদি সম্ভবপর হয়ও, তাহলে মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় সম্পদের কাঙ্ক্ষিত বণ্টনের জন্য আয়ের সমবণ্টন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যদি তা না থাকে, তাহলে এধরণের বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন অধিকাংশ ভোক্তার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হবে। এর ফলে একটি পুঁজিপতি উচ্চবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হবে যারা সংখ্যায় কম হওয়া সত্তেও তাদের হাতে জাতীয় সম্পদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুঞ্জিভূত থাকবে। এবং তথাকথিত ভোটের ওয়েট (weight) দিয়ে তারা দুর্লভ জাতীয় সম্পদগুলোকে সামাজিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরবে। ফলশ্রুতিতে জাতীয় সম্পদের যে বণ্টন হবে তাও সমাজের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হবে। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রাব্যবস্থা ব্যক্তিগত ভোটের মূল্যমানে নির্ধারিত হওয়ার পরিবর্তে কোনো একটি পণ্য বা সেবার জন্য সর্বমোট কতটি ভোট বিদ্যমান তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সুতরাং, এখানে সম্পদের প্রত্যাশিত বণ্টন নির্ধারণ করার পূর্বশর্ত হলো, আয়ের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা, যা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য।
তৃতীয়ত, একচেটিয়া (monopoly) ও মনোপসনি (monopsony) বাজার ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে পরিচালনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে, বা এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যাতে পণ্যের দামে (price) এর সঠিক খরচ (cost) ও উপকারিতা প্রতিফলিত হয় না। পণ্যের দাম তার সুযোগ ব্যয় থেকে কম-বেশি হওয়ার কারণ শুধু এই নয় যে, উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক তার উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় কম বেশি হতে পারে। তার কাজের সামাজিক মূল্যমান ও উপকারিতাকে অবজ্ঞা করার কারণেও এটি ঘটতে পারে। অন্যদিকে ইসলামে সামাজিক অগ্রগতির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। যদিও মূল্য ব্যবস্থার আত্ম-সংশোধনের প্রবণতা বিদ্যমান যার ফলে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্বার্থের দূরত্ব দূর হওয়া সম্ভব, কিন্তু কার্যকারিতার (operational) ত্রুটি এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সীমিত স্বাধীনতার জন্য এটি অসহনীয় দীর্ঘ সময় নেয়। এই পরিস্থিতিতে কোনো একটি উন্নয়নমূলক সরকারব্যবস্থার নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা ব্যতীত এই বাজার ব্যবস্থাটি কখনো সম্পদের সর্বোত্তম বণ্টন (optimum allocation) নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে না।
চতুর্থত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তি তার পণ্যের প্রাথমিক মালিক, তাই এগুলো দিয়ে সে যা খুশি তাই করতে পারে। নৈতিক কোনো সীমারেখা না থাকায়, সে চাইলে মূল্যবৃদ্ধির জন্য পণ্যকে পুড়িয়ে ফেলা বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করার মতো জঘন্য কাজও করতে পারে। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় যেহেতু সব সম্পদ আল্লাহর দেয়া আমানতস্বরূপ, তাই এটি একটি মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। জান-মালের ক্ষতি সাধনকে কোরআনে দুর্নীতি ও পাপের সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (২ : ২০৫) এটি সে আয়াত, যা হযরত আবু বকরকে (রা.) তার সেনাপতি ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে যুদ্ধে প্রেরণের সময় অন্যায়ভাবে কাউকে হত্য না করতে এবং এমনকি শত্রুপক্ষের ভূমিতেও কোনো শস্যক্ষেত ও পশুপাখির ক্ষতি না করার নসিহত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।(৬৩) যদি যুদ্ধক্ষেত্রেই এটি অনুমোদিত না হয়, তবে স্বাভাবিক সময়ে বা মূল্যবৃদ্ধির জন্য এধরণের কাজ গ্রহণযোগ্য হবার তো প্রশ্নই আসে না।
পঞ্চমত, এমনকি বাজার পরিচালনায় সুস্থ প্রতিযোগিতার শর্তেও এটি বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অস্থিরতা বা অচলাবস্থা মোকাবেলার জন্য কিংবা পণ্যদ্রব্যের ন্যায্য বণ্টনের জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। তাই, এর জন্য সুনির্দিষ্ট আদর্শিক লক্ষ্য ভিত্তিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।
ষষ্ঠ বিষয় হলো, এরকম প্রতিযোগিতা নির্ভর বাজারে সফলতার রাস্তাগুলো অনেক সময় নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার এবং আয়ের ন্যায্য বন্টনের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো সরকারের তত্ত্বাবধানে না থাকলে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অযোগ্যরা জায়গা পেয়ে যেতে পারে, আবার বিপরীতে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজগুলো পেছনে পড়ে থাকতে পারে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।
অতএব, ইসলাম যদিও একটি বাজার ব্যবস্থার রূপরেখা আমাদের দিয়ে দিয়েছে, তথাপি এটি অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী কোনো কিছু নয়। মূলত এটি হলো একটি ব্যবস্থা যার মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করা, বিশেষ করে ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারটি। সেজন্য ইসলামী আদর্শের আলোকে প্রয়োজন ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাজারব্যবস্থাকে সাজিয়ে নিতে হবে। ইসলাম এক্ষেত্রে সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। তবে সরকার এককভাবে কখনো অর্থনৈতিক সুবিচার ও সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তিতে একটি সুস্থ বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না, হয়তো কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করতে সক্ষম হবে। অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূর করতে হলে আখলাকী দর্শনকে সমাজের গভীরে প্রোথিত হতে হবে। যাকে সজ্জিত হতে হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার, সামাজিক উন্নয়ন এবং আয় ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের আদর্শে। সুতরাং, পুঁজিবাদ যদিও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে এটিকে আলাদা করেছে সেকুলারিজম; এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার ও জনকল্যাণের স্বার্থে একটি সুস্পষ্ট আখলাকী দর্শনের অনুপস্থিতি।
অনুবাদঃ নাজিয়া তাসনীম।
টীকা-
১. দ্রষ্টব্য: সূরা মায়েদার তাফসীর (০৫:৮৭), কাশশাফ, বৈরুত ১৯৪৭, খণ্ড ১. পৃ. ৬৭। ইবনে কাসীর, তাফসিরু কুরআনিল আযীম, কায়রো, খণ্ড ২. পৃষ্ঠা. ৮৭-৮৮। আরও দেখুন, বুখারী, কায়রো, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৯-৫০; মুসলিম, কায়রো ১৯৫৫, খণ্ড ২, পৃ. ৮১২-১৮: দারেমী, দামেশক ১৩৪৯ হিজরী, খণ্ড ২. পৃ. ১৩৩।
২. কোরআন ২:১৭২, ৬:১৪২, ৭:৩১ এবং ১৬০, ১৬:১১৪, ২০:৮১, ২৩:৫১, ৩৪:১৫, ৬৭:১৫
৩. ইবনে মাজাহ, কায়রো, ১৯৫২. খণ্ড ২, পৃ. ৭২৭:২১৪৮
৪. বুখারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ১২৮; মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ১১৮৯:১২, এবং তিরমিযী, খণ্ড ৩, পৃ. ৬৬৬:১৩৮-২
৫. বায়হাকীর শু’আবুল ঈমানের উদ্ধৃতিতে মিশকাতে উল্লিখিত, দামেশক, ১৩৮১ হিজরী, খণ্ড ২, পৃ. ৬৫৮:৫২০৭
৬. দ্রঃ “তোমরা কি দেখো না, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ কোনো জ্ঞান, কোনো পথনির্দেশ বা কোনো দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে”। সূরা লোকমান, (৩১:২০); এছাড়া, কোরআনে অনুরূপ আরো বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, দ্রঃ ১৪:৩২-৩৩, ১৬:১২-১৪; ২২; ৬৫ এবং ৪৫:১২
৭. বুখারী, খণ্ড ৭, পৃ. ১৫৮; ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃ. ১১৩৮:৩৪৩৯
৮. “কারো নিকট ভিক্ষা করো না”, আবু দাউদ, কায়রো ১৯৫২, খণ্ড ১, পৃ. ৩৮২; উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে অধিকতর উত্তম, বুখারী, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৩; নাসায়ী, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৫-৪৬। এছাড়া দ্রঃ ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃ. ৭২৩:২১৩৮; নাসায়ী, কায়রো ১৯৬৪, খণ্ড ৭, পৃ. ২১২
১. দ্র: আবু যাহরাহ, উসূল আল ফিকহ, দামেশক ১৯৫৭, পৃ. ৩৫৫
১০. আবু হামিদ আল গাজালী, আল মুসতাসফা, কায়রো ১৯৩৭, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৯-৪০
১১. ইবনুল কাইয়্যিম, ই’লামুল মুয়াক্কিইয়ীন, কায়রো ১৯৫৫
১২. ইবনে কাসীর, তাফসিরু কুরআনিল আযীম, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৬৭
১৩. ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃ. ৭২৫, ২১৪৪
১৪. দ্রঃ কোরআন (৪:৭৭, ২৯:৬৪, ৫৭:২০-২১); ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৭৮:৪১১৪
১৫. বুখারী, পৃ. ১১৩:৩০১
১৬. বায়হাকীর শু’আবুল ঈমানের উদ্ধৃতিতে মিশকাতে উল্লিখিত, দামেশক, ১৩৮১ হিজরী, খণ্ড ২, পৃ. ৬৫৯:৫২১৩
১৭. মুসনাদে আহমাদ, মিশকাতে উদ্ধৃত, খণ্ড ২, পৃ. ৬৩:১:৫১৭৯
১৮. ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃ. ৭২৫:২১৪৩
১৯. ইবনে আসাকিরের বরাতে উদ্ধৃত, সামান্য শব্দভেদে একই রেওয়ায়েত উল্লেখ হয়েছে, সুয়ুতীর জামি আস সাগীর, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৫
২০. তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৮, পৃ. ৮৪
২১. ইবনে কাসীর, তাফসীর, খণ্ড ৪, পৃ. ২১৮, দেখুন-সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতের তাফসীর।
২২. শাতিবী, আল মুওয়াফিকাত ফি উসূল আশ শারীয়াহ, কায়রো, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৪: বুখারী, মুসলিম এবং নাসায়ীর বরাতে উল্লেখ করেছেন।
২৩. আল কোরআন, ৩৩:৫, এবং ৪৯:১০
২৪. মিশকাত, খণ্ড ২, পৃ. ৬১৩:৪৯৯৮, বায়হাকীর শু’আবুল ঈমানের উদ্ধৃতিতে মিশকাতে উল্লিখিত।
২৫. প্রাগুক্ত, ৬০৮:৪৯৬৯, আবু দাউদ ও তিরমিযীর বরাতে উল্লিখিত।
২৬. বুখারী, খণ্ড ৮, পৃ. ১২; মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৯৯৯, একইসাথে দেখুন ৬৫ এবং ৬৭নং হাদীস।
২৭. মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৯৮৬:৩২
২৮. মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৯৮৭:৩৪
২৯. বুখারী, খণ্ড ৮, পৃ. ১৫
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯ এবং নাসায়ী, খণ্ড ৮, পৃ.৬৫
৩১. মুসনাদ ইমাম আলী আল রিদা, বৈরুত ১৯৬৬, পৃ. ৪৭৪
৩২. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, কায়রো ১৩৬৭ হিজরী।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪ এবং ৬
৩৪. দেখুন, কোরআন ৮৩:১-৩
৩৫. মুসনাদ এবং বায়হাকীর শুআবুল ঈমানের বরাতে সুয়ূতী উদ্ধৃত করেছেন, খণ্ড ১, পৃ. ৮
৩৬. বুখারী, খণ্ড ৩, পৃ. ১১২
৩৭. কিছু উদ্ধৃতিতে (হাদীস অথবা অন্যান্য) ‘দাস’দের সাথে সম্পর্কিত হলেও অনুবাদে কর্মচারী ব্যবহার করা হয়েছে। একজন দাসের সাথেও যখন আদিল ও মানবিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, সে তুলনায় একজন কর্মচারীর সাথেও অবশ্যই তার চেয়েও অধিক ভালো আচরণ করতে হবে।
৩৮. মালিক, মুয়াত্তা, কায়রো ১৯৫১, খণ্ড ২, পৃ. ৯৮০:৪০
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮১:৪২
৪০. বুখারী, পৃ. ১৫ এবং খণ্ড ৩, পৃ. ১৮৫; মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৮৩:৩৮
৪১. “আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে: (সূরা ত্বহা, ২৮:২৭), হযরত শুয়াইব (আ.) যখন মুসা (আ.) কে কাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন, তখন এমনটা বলেছিলেন। যা যেকোনো কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে একটি অনন্য কোরআনী উপদেশ।
৪২. বুখারী, খণ্ড ১. পৃ. ১৬ এবং খণ্ড ৩, পৃ. ১৮৫; মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৮৩:৩৮ এবং 80
৪৩. মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৪৮:৫৭
৪৪. বায়হাকীর শুআবুল ঈমানের বরাতে সুয়তী উল্লেখ করেছেন, খণ্ড ১, পৃ. ৭৫
৪৫. বুখারী, খণ্ড ৩, পৃ. ১৮৬
৪৬. আবু দাউদ, খণ্ড ২, পৃ. ১২১
৪৭. বুখারী, পৃ. ৫২৪১১২
৪৮. হোসাইন হায়কল, উমার আল ফারুক, কায়রো ১৯৬৪, খণ্ড ২, পৃ. ২৩৩
৪৯. আবু উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল, কায়রো ১৩৫৩ হিজরী, পৃ. ৫৯৫:১৯০৯, সামান্য শব্দভেদে উল্লিখিত হয়েছে, নাহজুল বালাগা, কায়রো, খণ্ড ৩, পৃ. ২৩১
৫০. প্রাসঙ্গিক বর্ণনার জন্য দেখুন, সিদ্দিকী, ইসলাম কা নাযারিয়ায়ে মিলকিয়াত, লাহোর ১৯৬৮, পৃ. ২৭২-৭৯
৫১. রাসূল (স.) যখন মুয়ায (রা.)-কে ইয়েমেনের গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করেন, তখন তাকে দায়িত্বের একটি তালিকা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিলো, ‘মানুষকে এ কথা বোঝানো যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা সম্পদশালীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে, এবং দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে’। দেখুন-বুখারী, খণ্ড ২, পৃ. ১২৪; তিরমিযী, খণ্ড ৩, পৃ. ২১:৬২৫; এবং নাসায়ী, খণ্ড ৫, পৃ. ৩ এবং ৪১
৫২. সূরা তাওবার ৩৪ নং আয়াতের তাফসীর দেখুন, ইবনে কাসীর, তাফসিরু কুরআনিল আযীম, খণ্ড ২, পৃ. ৩৫২; এবং জাসসাস, আহকামুল কুরআন, কায়রো ১৯৫৭, খণ্ড ৩, পৃ. ১৩০
৫৩.দ্র: তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃ. ৩৫০-৫৩
৫৪. আলী আল তানতাবী ও নাজী আল তানতাবী, আখবারু উমার, দামেশক ১৯৫৯, পৃ. ২৬৮
৫৫. উদ্ধৃত, ইউসুফউদ্দীন, ইসলাম কি মাশি নাজরিয়াত, হায়দারাবাদ, ভারত, খণ্ড ১, পৃ. ১৪০
৫৬. আল হিদায়াহ, কায়রো ১৯৬৫, খণ্ড ৩, পৃ. ২৮১, আরো দেখুন, জাযিরী, কিতাবুল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবাআ, কায়রো ১৯৩৮, খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৯
৫৭. আল হিদায়াহ, খণ্ড ৩, পৃ. ২৮১ এবং জাযিরী, খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৯
৫৮. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য, দেখুন-শাতিবী, খণ্ড ২, পৃ.৩৪৮-৬৪; আবু যাহরাহ, পৃ. ৩৫০-৬৪; দাওয়ালিবী, আল মাদখাল ইলা ইলমিল উসূল আল ফিকহ, বৈরুত ১৯৬৫, পৃ. ৪৪৭-৪৯
৫৯. জাফিরী, খণ্ড ২, পৃ. ১৫৩-১৬৮
৬০. উদ্ধৃত, ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কায়রো ১৯৬০, খণ্ড ২, পৃ. ১৬৭
৬১. জাফিরী, খণ্ড ২, পৃ. ২৮৩-২৮৪
৬২. মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৭২৮:১২২
৬৩. মালিক, মুয়াত্তা, খণ্ড ২, পৃ. ৪৪৮:১০; আরও দেখুন, মাওয়ারদী, আহকামুস সুলতানিয়া, কায়রো, ১৯৬০, পৃ. ৩৪