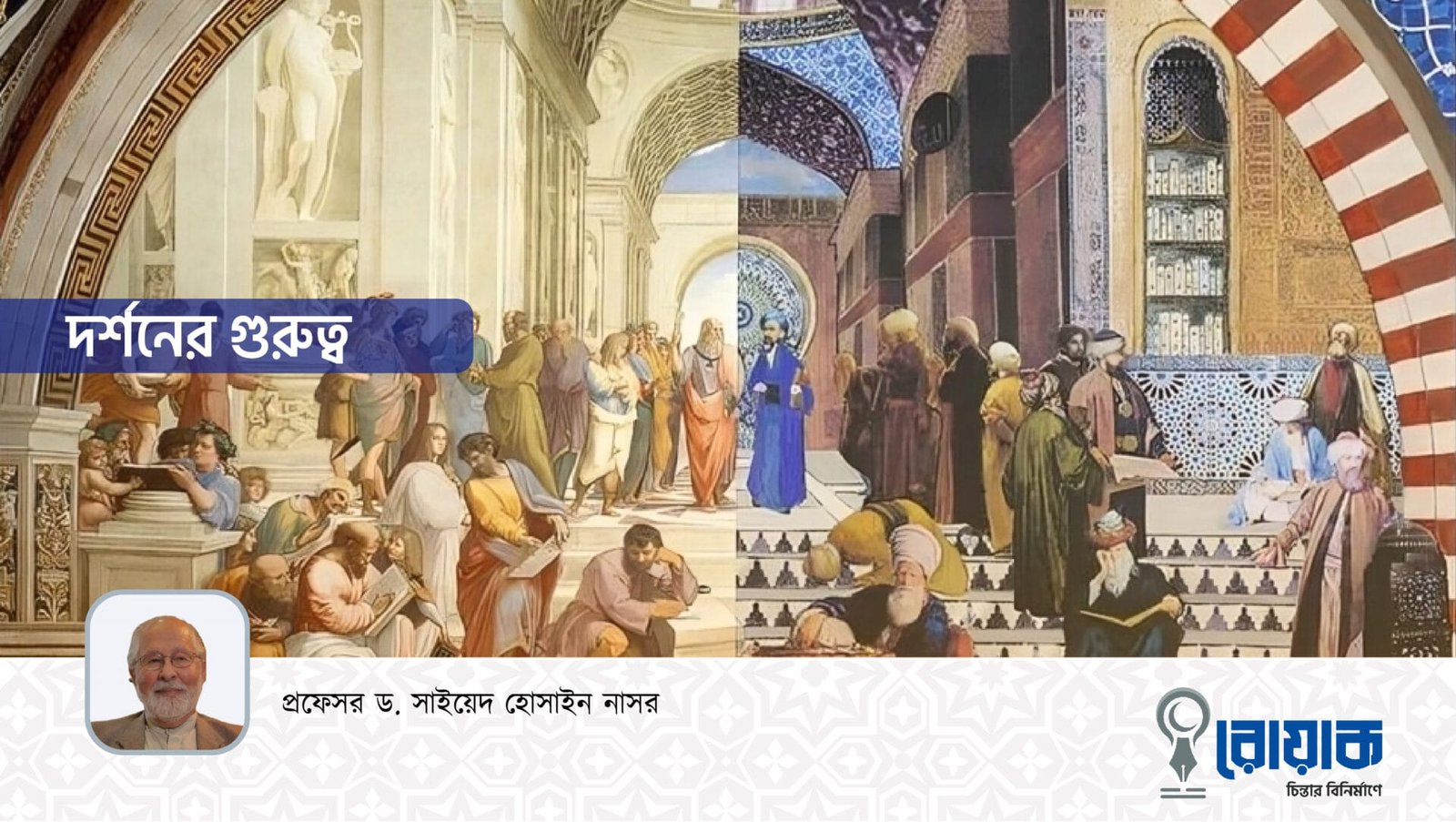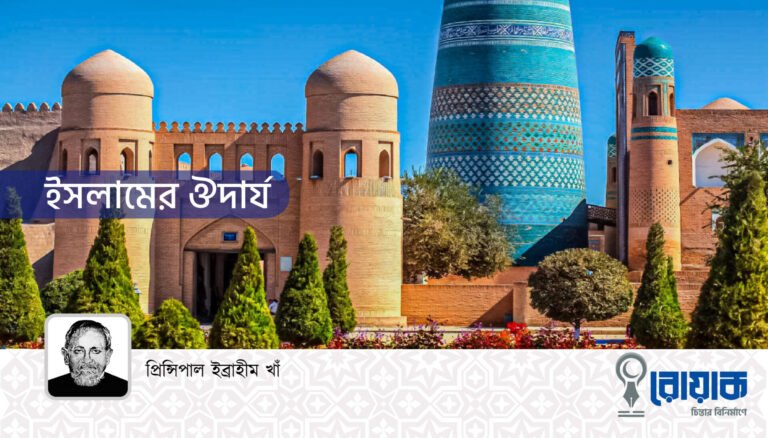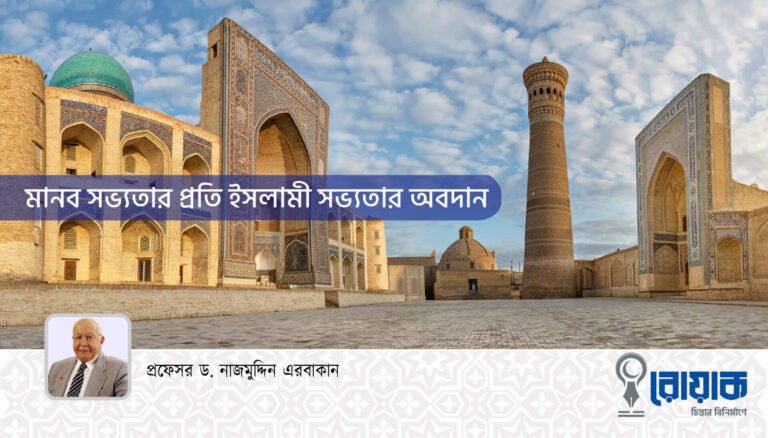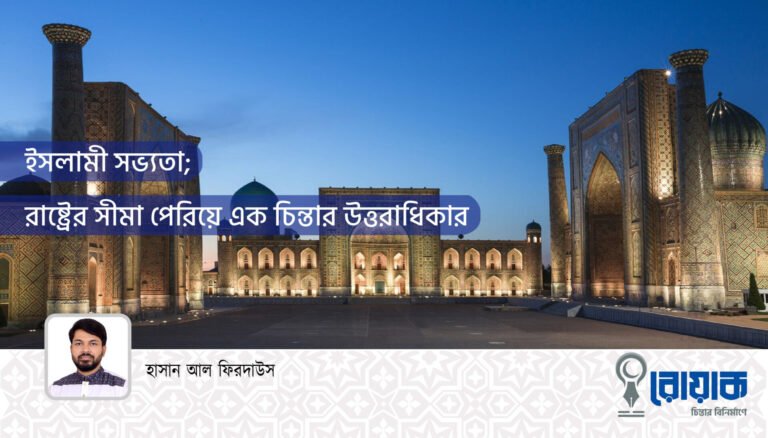দর্শন বলতে আসলে কি বুঝায় ? প্রথমেই দর্শনের সংজ্ঞাকে পরিষ্কার করা দরকার। অনেক আধুনিক মুসলিম সংস্কারক ও চিন্তাবিদ, যেমন মুহাম্মদ আবদুহু, দর্শন শব্দটি নিয়ে একটু ভয় বা সন্দেহ পোষণ করেন। যদিও এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জামালউদ্দিন আফগানি তেহরানে বহু বছর ইসলামী দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন, যতক্ষণ না তিনি সরকারের চাপে দেশ ছেড়ে আফগানিস্তান, তারপর তুরস্ক ও মিশরে পালিয়ে যান। একটি বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে বিদ্যমান থাকায় ইসলামী প্রেক্ষাপটে দর্শন শব্দটি একটু অস্পষ্ট মনে হয়। তবে পশ্চিমা ও ইসলামী প্রেক্ষাপটে দর্শনের অস্পষ্টতার ধরন একেবারেই আলাদা। পশ্চিমে দর্শনের অর্থ অনেক রকম—প্লেটো এবং দেরিদার মত সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষকেও দার্শনিকই ডাকা হয়। এখানে একক কোনও বিশ্বদর্শন নাই, এমনকি অধিকাংশ দার্শনিক অনুসরণ করেছেন, এমন গুটিকয়েক বিশ্বদর্শনও আপনি খুঁজে পাবেন না। ফলে এটা এত বিস্তৃত যে তাদেরকে একই ছাতার নিচে ফেলা যায় না। পশ্চিমে দর্শন এখন আর হাজার বছর ধরে চলে আসা সেই প্রাচীন ধারণা নয়, যা গ্রিক-রোমান যুগে বা ইসলাম ও পশ্চিমের বহুমুখী চিন্তার সম্মিলনের সময়ে ছিল। আধুনিক পশ্চিমা দর্শন অনেক সময় সফিয়া বা প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে গিয়েছে। কোনো কোনো বিজ্ঞজন এটাকে এখন “মিসোসফি” বলে ডাকেন, অর্থাৎ ‘প্রজ্ঞার প্রতি ঘৃণা’, যদিও দর্শনের আসল অর্থ ছিল ‘প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসা’।
ইসলামের ক্ষেত্রে অনেকেই ভুলে যান যে কুরআন নিজেই দুইবার “হিকমা” শব্দটি উল্লেখ করেছে, যাকে আল্লাহর কাছ থেকে মহান উপহার বলা হয়েছে। এই হিকমাকে ইসলামী আলেমরা গ্রিক শব্দ ‘ফিলোসফিয়া’ থেকে আরবীকরণ করে তাকে “ফালসাফা” হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে ইসলামে দর্শনের বিকাশ একটু ভিন্ন পথে গেছে। আমাদের মাঝে ফালসাফা নামে একটি বিদ্যা ছিল ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা- যেমন কালাম এবং অন্যান্য বিষয়ও ছিল, যেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে দর্শন না হলেও অনেক ক্ষেত্রে দার্শনিকই ছিল। ইমাম আশআরী সুন্নি ইসলামের প্রধান কালামী ধারা আশআরি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ফালসাফার বিরোধিতা করলেও যুক্তি, কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমনকি তিনি দর্শনের অস্তিত্বই স্বীকার করতেন না, তবে তিনি যে সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন এগুলো মূলত দার্শনিক বিষয়ই ছিল। এমনকি যারা নিজেদের দার্শনিক বলে দাবি করেননি এনারা সহ সব ধরনের ইসলামী চিন্তাবিদদের কাছে ঈমান ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা নিজেই একটি দার্শনিক বিষয়।
আপনি বলতে পারেন, দর্শন অনেকটা রাজনীতির মতো। রাজনীতি ভালো বা খারাপ হতে পারে, কিন্তু কোনো সমাজ রাজনীতি ছাড়া চলতে পারে না। একইভাবে, দর্শন ছাড়া কেউ চলতে পারে না। সচেতন বা অবচেতন যেভাবেই হোক, নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই—জীবন, কাজ, নীতি, চিন্তা, কী ভালো, কী খারাপ, কী সত্য, কী মিথ্যা, কী সুন্দর, কী কুৎসিত, এসব নিয়ে একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। তাই দর্শন ছাড়া চলা অসম্ভব। গত দুই শতাব্দী ধরে, বিশেষ করে ১৭৯৮-১৮০০ সালে নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণের পর থেকে পশ্চিমা চিন্তাধারার আগ্রাসনের মুখে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় ট্র্যাজেডি হলো- আমাদের নিজস্ব দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে বা এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেকের অস্বীকৃতি। অনেক ইসলামী আন্দোলনে একটা দর্শন-বিরোধী মনোভাব আছে, যদিও তারা মৌলিকভাবে দার্শনিক চ্যালেঞ্জের মুখেই পড়েছে।
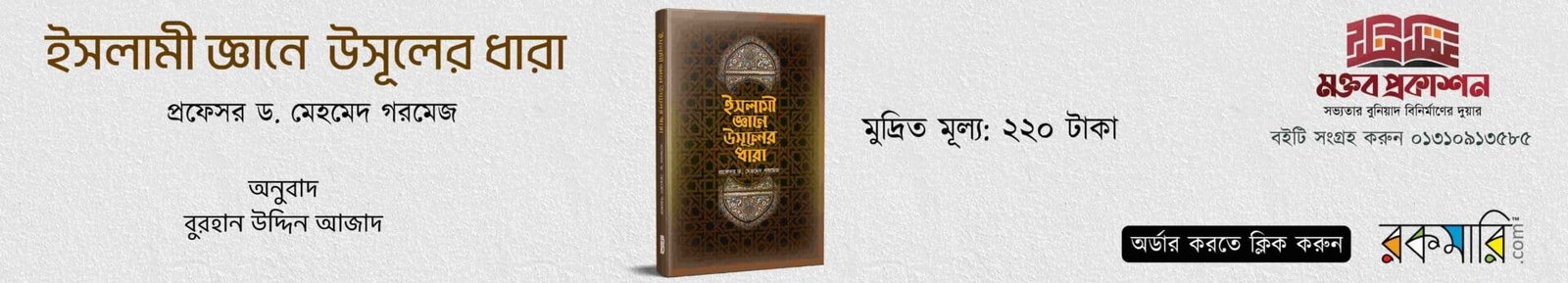
পশ্চিমের এই চ্যালেঞ্জ মঙ্গোল আক্রমণের মতো নয়। মঙ্গোলরা লাখো ঘোড়া নিয়ে এসে জমি ধ্বংস করেছে, লাখো মানুষ মেরেছে, কিন্তু তারা ইসলামকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চ্যালেঞ্জ করেনি। চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকুর নেতৃত্বে তাদের চ্যালেঞ্জ ছিল তীর-ধনুক আর ঘোড়া, কিন্তু ইসলামের প্রতি পশ্চিমের প্রধান চ্যালেঞ্জটা বুদ্ধিবৃত্তিক। এটা শুধু ড্রোন দিয়ে সেই আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে নিরীহ শিশুদের হত্যার ট্র্যাজেডি নয়, যাদের জন্য কেউ কাঁদে না। আমি ওয়াশিংটনে থাকি, এটা আর সহ্য করতে পারি না। কানেকটিকাটে নীল চোখের শিশু মারা গেলে সবাই কাঁদে, আমিও দুঃখিত হই। কিন্তু পেশোয়ারের কাছে কালো চোখের শিশু মারা গেলে কেউ পাত্তা দেয় না। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ এটা নয়। কিংবা এটা শুধু ড্রোন, কিংবা আইএমএফ-এর অর্থনৈতিক চাপ, বা পশ্চিমা শক্তির হাতে বিভিন্ন দেশে ক্ষমতায় বসানো পুতুল সরকার নয়। বরং পশ্চিমের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তার জগতের। আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়েছি, কারণ আমরা একটি সভ্যতা হিসেবে যথেষ্ট ভাবা বন্ধ করে দিয়েছি, সঠিকভাবে চিন্তা করা বন্ধ করে দিয়েছি। যেকোনো মাপকাঠিতে আমাদের সভ্যতা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় চিন্তাবিদ তৈরি করেছে। ইসলামে আলহামদুলিল্লাহ ঈমান এখনো শক্তিশালী হলেও, এটা খুবই দুঃখজনক যে অনেক সংস্কারক সঠিক চিন্তার গুরুত্ব; আব্বাসীয় যুগ থেকে আজ অবধি বিস্তৃত ১১০০ বছরের হিকমা ও ফালসাফার ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেননি।
কুরআনের একটি আয়াত বলে, “আমরা কুরআন নাযিল করেছি যাতে মানুষ তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে।” আমি এখানে “যুক্তি” শব্দটি ব্যবহার করছি না, বরং পুরনো ইংরেজি ব্যবহারে “বুদ্ধি” বা “ইনটেলেক্ট” শব্দটি ব্যবহার করছি, যা এখন হারিয়ে গেছে। আরবিতে এটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধি শুধু যুক্তি নয়, এটা তার চেয়ে গভীর। পশ্চিমের বড় ট্র্যাজেডি হলো বুদ্ধির মৃত্যু, এটিকে শুধু যুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া, যার ফলে যুক্তি ও ওহীর, ধর্ম ও বিজ্ঞান, ইহজগত ও পরজগতের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামী সভ্যতায় এটা কখনো ছিল না, কারণ আমাদের আকল শুধু যুক্তিবাদী বয়ান ছিল না। আকল দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সারবত্তা যা আমাদের মৌলিক ও অপরিহার্যরূপে জানতে সাহায্য করত। আমরা সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আজ আমরা কুরআন পড়ি বটে, কিন্তু আকল খাটাইনা। ফলে স্পষ্টভাবে ভাবতেও পারিনা। এটা কতটা অদ্ভুত যে, এমন একটি সভ্যতা যে সভ্যতা তাজমহলের মতো জ্যামিতিক নিখুঁত স্থাপত্য, ইসফাহানের মসজিদ বা ফেজের মাদ্রাসার ময়দান তৈরি করেছে বিশ্বের সবচেয়ে সূক্ষ্ম গণিত ও জ্যামিতির ওপর ভিত্তি করে, সেই তার চিন্তা আজ এত দুর্বল, পশ্চিমা চিন্তার চ্যালেঞ্জের মুখে এত নড়বড়ে! আমাদের কণ্ঠগুলো বিশ্ব পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, আমাদের ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আছে, কিন্তু মানবজাতির ভবিষ্যৎ ও চিন্তার প্রশ্নে মুসলিম কণ্ঠ কোথায়? এটা আমাদের নিজেদের দোষ, কারণ আমরা এমন এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী যারা কুরআনের ভিত্তিতে স্পষ্ট চিন্তার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। আমরা সেটা করিনা, মাথাটাই খাটাইনা।
আজ পশ্চিম থেকে নানা ধরনের “ইজম” সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো একের পর এক আমাদের উপকূলে এসে আছড়ে পড়ছে। আপনারা সবাই এ ব্যাপারে অবগত, আবার কেউ জেনে নাও থাকতে পারেন। যেমন র্যাশনালিজম, এম্পিরিসিজম, হিউম্যানিজম, ইভল্যুশনিজম ; সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিবারেলিজম, সোশ্যালিজম, ন্যাশনালিজম, জ্ঞানতাত্ত্বিক যায়গায় সায়েন্টিজম। চতুর্দিকে ভেসে বেড়ানো এই ইজমগুলো আমাদের মন ও চিন্তাকে নানা মাত্রায় প্রভাবিত করছে। ইসলামী বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা এমন যে, ইরান এবং দুয়েকটা দেশ ছাড়া বেশিরভাগ দেশে পশ্চিমা শিক্ষাই প্রাধান্য পায়। উপনিবেশিক যুগ থেকে মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে এই প্রভাব চলে এসেছে। মিশর বা পাকিস্তানের ধনী পরিবারের প্রায় ৯০% শিশু পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, মুসলিম স্কুলে নয়। পুরনো মাদ্রাসাগুলো এখন শুধু গরিবদের জন্য। দুই শতাব্দী আগে এমন ছিল না। আজ এই ধরণের লোকেরাই দেশ পরিচালনা করে, কিন্তু পশ্চিমা ইজম দিয়ে তাদের মগজধোলাই হয়ে আছে। ধার্মিকদের মধ্যে কেউ কেউ আমরা নামাজ আদায় করি, কিন্তু বাকি সময় এই ইজমের মধ্যে ডুবে থাকি। ইসলাম এখনো এই ইজমগুলোর পূর্ণাঙ্গ জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। পূবাল হাওয়ার মত আমরা নতুন ইজমের অপেক্ষায় থাকি, কেউ কেউ এগুলো গোগ্রাসে গিলে, আবার কেউ টেরই পায়না, তবু এগুলো আমাদের প্রভাবিত করেই চলেছে।
তেহরানে ফরাসি দার্শনিক ফুকোর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন পশ্চিমেও তিনি খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। এক সন্ধ্যায় আমরা আলোচনায় বসেছিলাম। তিনি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ ছিলেন, কিন্তু আফসোসের বিষয় তিনি ইমানদার ছিলেন না। কিন্তু তিনি আলোচনার জন্য যথোপযুক্ত একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ফ্রান্সে এখন কেউ আমার কথা শোনে না, কিন্তু একদিন শুনবে। আমি কয়েকজন তরুণ পারসিক ছাত্র ও অধ্যাপককে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ফ্রান্সে আমার ধারণা জনপ্রিয় হলেই এখানেও তা ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক তাই হয়েছিল। ফুকো মারা গেলেন, তারপর দেরিদা এলেন, তিনিও চলে গেলেন, এভাবেই চলছে। আমরা শুধু এই ঢেউয়ের শিকার। কিছু ইজম সামাজিক, যেমন জাতীয়তাবাদ বা সমাজতন্ত্র; কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক। কিন্তু আমরা আজ নিষ্ক্রিয়, ফলে এই ইজমগুলো ক্রমাগত আমাদের উপর হামলে পড়েছে।
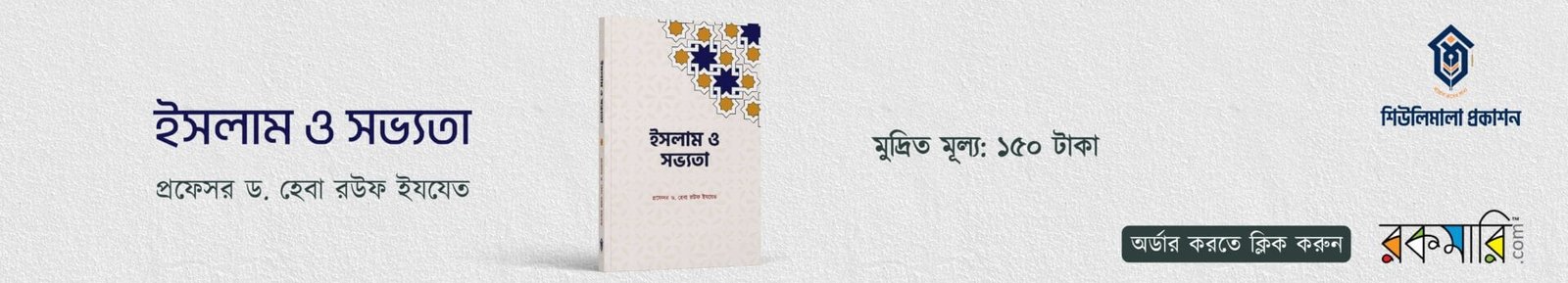
এই তাবৎ ইজমগুলো দর্শনের সঙ্গে যুক্ত, চিন্তার ধরন ও বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি – র্যাশনালিজম তো নিজেই এক ফিলসফি। সে বলে যুক্তিই সত্যে পৌঁছানোর একমাত্র পথ। কত মুসলিম আছেন, যারা নামাজের সময় ধার্মিক, কিন্তু বাকি সময় র্যাশনালিস্ট? অনেক আধুনিক মুসলিম লেখক পশ্চিমা চিন্তার প্রভাবে বিভ্রান্ত। পাশ্চাত্য চিন্তার প্রশ্নে তারা কোনো ডান-বাম হদিস করতে পারেননা। তারা আকল ও রিজন বা ইস্তিদলাল (যুক্তি) এর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না। ফলে তারা বলেন, ইসলাম পুরোপুরি র্যাশনাল! এই বিভ্রান্তির কারণে কিছু জায়গায় চরম মৌলবাদ ও প্রযুক্তির পূজার অদ্ভুত মিশ্রণ দেখা যায়। মুসলিম বিশ্বের কিছু কিছু যায়গায় আপনি এমনও দেখবেন, যেখানে লেটেস্ট প্রযুক্তির পূজা করা হচ্ছে, মুখে বলা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অথচ তাদের আসল খোদা এই উন্নত প্রযুক্তি। আবার এরাই অন্তঃসার শুণ্যভাবে চলে আসছে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধকে হেফাজত করতে। এটি ইসলামী বিশ্বের একটি বড় ট্র্যাজেডি।
আমরা প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না, কারণ আমরা আকল খাটাই না। সব প্রশ্নের উত্তর মুষ্টি বা আবেগ দিয়ে দেওয়া যায় না। আগুন লাগলে বেহালা বাজিয়ে তা নেভানো যায় না, পানির প্রয়োজন। হ্যাঁ ভালো বেহালার সুর দিয়ে খারাপটাকে বদলে দেয়া যায়। ঠিক সেভাবেই ভুল চিন্তার জবাব একমাত্র সঠিক চিন্তা দিয়ে দেওয়া যায়। ভুল চিন্তাকে চিৎকার করে সঠিক করা যায়না। আবেগ কখনো ভুল চিন্তাকে শোধরাতে পারেনা, যেটা কেবল সঠিক চিন্তাই পারে। কুরআন বারবার বলে, যারা সঠিকভাবে আকল ব্যবহার করে, তারা যারা করে না, তাদের সমান নয়। যারা আকল খাটায়, তারাই প্রকৃত মুসলিম। এই শিক্ষা আমরা আজ সত্যিই ভুলে গেছি।
আমি পঞ্চাশ বছর ধরে এই বিষয়ে কাজ করছি, কিন্তু আমাদের অগ্রগতি খুব ধীর। ১৯৭৭ সালে মক্কায় প্রথম বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে আমি ড. জোব, ড. নাসিফ ও মরহুম বাংলাদেশি চিন্তাবিদ ড. সাইয়েদ আলী আশরাফের সঙ্গে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলাম। আমি এই চার অগ্রপথিকের একজন ছিলাম। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও শিক্ষামন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু আমরা সফল হইনি, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু শরিয়া ফ্যাকাল্টিতেই ইসলামী শিক্ষা দেওয়া হয়, বাকি সব পশ্চিমা বিষয়। মুসলিম হিসেবে আমরা আমাদের আকল দিয়ে এই বিষয়গুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবিনি। এটি সহজ কাজ নয়, তবে অসম্ভবও নয়। একটি অনন্য সভ্যতা হিসেবে ইসলামের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আমরা কতটা ইসলামী কায়দায় ও স্পষ্টভাবে ভাবতে পারি তার উপর।
এজন্য সবার আগে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাকে পুনর্জাগরিত করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের, প্রতিটি শাখার মধ্যেই একটি দার্শনিক দিক রয়েছে। এমনকি উসুল ; উসূলুদ্দীন উসুলে ফিকাহ, যা আল-আজহারের মতো ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞান, তারও একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দিক রয়েছে, যা পুনর্জাগরিত করা প্রয়োজন। এমনকি আধুনিক পশ্চিমা দর্শনের একটি শাখা সেমান্টিকসও (শব্দার্থবিজ্ঞান) উসুলের মধ্যে ভিন্ন কারণে আলোচিত হয়। মোটকথা হলো, উসুলের মতো ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যেও দার্শনিক দিক রয়েছে, যা আমাদের পুনরায় জাগিয়ে তুলতে হবে।
কালাম বা ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিকতাবাদীদের আক্রমণের মুখে পড়েছে, তবু এটি এখনো টিকে আছে। মিশরে নব্য মুতাজিলা এবং নব্য আশআরি মতবাদও দেখা যায়। সালাফি আন্দোলন অবশ্য এই সবকিছুর বিরুদ্ধে, এমনকি সমগ্র ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু শিয়া সুন্নি নির্বিশেষে যারা নিজেদের ঐতিহ্য গভীরভাবে বোঝেন, সেই দরদি মুসলিমরা কালামের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এটিকে আমাদের সময়ের জন্য উপযুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, এবং এর দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। এছাড়া, মা‘রিফাহ বা ইরফান, যাকে আমরা বাস্তবতার চূড়ান্ত জ্ঞান বলি, সেটা হচ্ছে ইসলামী মেটাফিজিক্স। এটি ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এটিকেও পুনর্জাগরিত করতে হবে এবং আমাদের সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক করতে হবে। এবং অবশ্যই এর সাথে ইসলামী বিজ্ঞান, ইসলামি দর্শনের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে।
যদি আমরা এই সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে পারি, তবে তা আমাদের জন্য এমন একটি কাঠামো দেবে, যার মধ্যে আমরা আধুনিক জ্ঞানের শাখাগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারব। এই জ্ঞানের শাখাগুলোর জন্য ইসলামী জবাব, ইসলামী সচেতনতা এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন, যা ইসলামী সভ্যতার জীবন্ত কাঠামোয় একীভূত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার কথা বলি। ১৯৬৪ সালে আমি “ইসলামী বিজ্ঞান” নিয়ে একটি বই লিখেছিলাম। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে “ইসলামী বিজ্ঞান” শব্দটি ব্যবহার করেছি দুটি কারণে। প্রথমত, আরব জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে “আরবি বিজ্ঞান” বলা ঐতিহাসিকভাবে ভুল। ইসলামী বিজ্ঞান শুধু আরবদের নয়, পারস্য, তুর্কি, মুসলিম ভারতীয়রাও এতে অবদান রেখেছে। ইবনে সিনা, আল বিরুনির মতো মহান বিজ্ঞানীরা আরব ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, এই বিজ্ঞান ইসলামী ওহীর সঙ্গে যুক্ত। সে সময় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। মুসলিম বিশ্বের অনেক বিজ্ঞানী আমার বিরোধিতা করেন, তারা বলেন – বিজ্ঞান বিজ্ঞানই, ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের এই দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।
বিজ্ঞান একটি বিশ্বদৃষ্টি ও প্যারাডাইমের উপর নির্ভর করে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন নাস্তিক সায়েন্টিস্ট ফিলোসফার আপনাকে এটাই বলবে। সুতরাং মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য ইসলামী বিজ্ঞানকে ইসলামী প্যারাডাইমের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে। আমি পঞ্চাশ বছর ধরে সায়েন্টিজমের সমালোচনা করে লড়াই চালিয়ে আসছি। সায়েন্টিজম ইসলামী বিশ্বের একটি বড় রোগ, পূর্ব আফ্রিকার ম্যালেরিয়ার চেয়েও ভয়ানক। সৌদি আরব, ইরান, মালয়েশিয়া, মিশর—সব সরকার বিজ্ঞানকে সমর্থন করে, কিন্তু এর প্রকৃতি না বুঝেই। তারা ক্ষমতা ও সম্পদ চায় তাই এরকমটা ভাবে বোঝাই যায়। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরাও ভাবেন বিজ্ঞানই যেহেতু ক্ষমতা দেয়, তাই এটি ইসলামী। তারা ভাবে, আল্লাহ জ্ঞান অন্বেষণ করতে বলেছেন, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানই শক্তি। তাই ক্ষমতা প্রদানকারী বিজ্ঞানও ইসলামীই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান, যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অপ্রাসঙ্গিক, যেখানে ক্যাথলিক বা নাস্তিক ফিজিসিস্ট হয়েও নোবেল পুরস্কার জেতা যায়, তা ইসলামী সভ্যতায় স্থান পেতে পারে না। বেশিরভাগ মানুষেরই এই কথাটা বলার সাহস নেই। অথচ আমি ২৫ বছর বয়সে এ কথা বলেছিলাম, এখনো বলছি।
আমাদের বুঝতে হবে, সায়েন্টিজম গ্রহণযোগ্য নয়। বেশিরভাগ মুসলিম বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপাসনা করেন। তারা বলেন, তারা আল্লাহর ইবাদত করেন, কিন্তু দিনের বেশিরভাগ সময় ঠিকই তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপাসনায় মগ্ন। এটি আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় রোগ। পরিবেশ সংকট একদিন ঠিকই আমাদের উচিত শিক্ষা দেবে। তখন লোকে এই অন্ধ পূজা বন্ধ করবে। এই রোগ শুধু ইসলামী বিশ্বে নয়, হিন্দু ভারত, কমিউনিস্ট চীনেও দেখা যায়। মাওসেতুং এর সময় থেকে তারা নাস্তিক হয়েও প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে তাদের উপাস্য বানিয়েছে। তাদেরতো আমাদের মত স্বতন্ত্র আদর্শ নেই, ফলে আমাদেরই এই বিজ্ঞানবাদ থেকে খুব খুব সতর্ক থাকতে হবে।
সায়েন্টিজমের মোকাবিলা করতে হলে আমাদের ইসলামী দার্শনিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, কারণ সায়েন্টিজম নিজেই একটি দর্শন। এটি প্রকৃতি ও জ্ঞানের দর্শন, যা আধুনিক বিজ্ঞান ছাড়া প্রকৃতিকে জানার অন্য সব পথ অস্বীকার করে। এর জবাব শুধু দর্শন দিয়েই দেওয়া সম্ভব। সায়েন্টিজমের বিপদের মোকাবিলা আমরা দর্শন ছাড়া করতে পারি না। আমাদের নিজস্ব দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে সঠিক দর্শন নিয়ে এটি মোকাবিলা করতে হবে।
মানববিদ্যার কথা যদি বলি, অনেক দিন ধরেই এটাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণে গড়ে তোলার কথা হচ্ছে। আমি বহু বছর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য অনুষদের ডিন ছিলাম, যা ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানববিদ্যার কেন্দ্র। আমি এই আন্দোলনের একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছি—পদার্থবিজ্ঞানে না পারলেও, অন্তত ইতিহাস, সাহিত্যের মতো বিষয়গুলো ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমরা ইতিহাস ফ্রান্সের চোখে দেখব না, মাঝখানে একটু একটু ইসলামী অংশ যোগ করে দিয়ে। সাহিত্য ইংরেজির দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ব না, শেষে উর্দু সাহিত্যের একটা ছোট অংশ যোগ করে। ইসলামী বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম দেখলে লজ্জা লাগে। কোনো সভ্যতা কি নিজেকে অন্যের চোখে দেখে? আজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ইতিহাসের বেশিরভাগ বই পশ্চিমা বিশ্বদৃষ্টির ওপর ভিত্তি করে। নৃবিজ্ঞান, ভাষা, এমনকি অন্যান্য বিষয়েও একই অবস্থা। আমাদের সেই আন্দোলনের ফলে ইরানে এ নিয়ে সর্বোচ্চ নেতা ফতোয়া দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন এই বিষয়ে কাজ করে। কিন্তু এখন তারা প্রায় নিজেদের পায়েই কুড়াল মারছে। আমি শীঘ্রই তেহরানে এ নিয়ে একটা লেখা প্রকাশ করতে চাই, কারণ এই কাজে আমি সবার সামনে ছিলাম।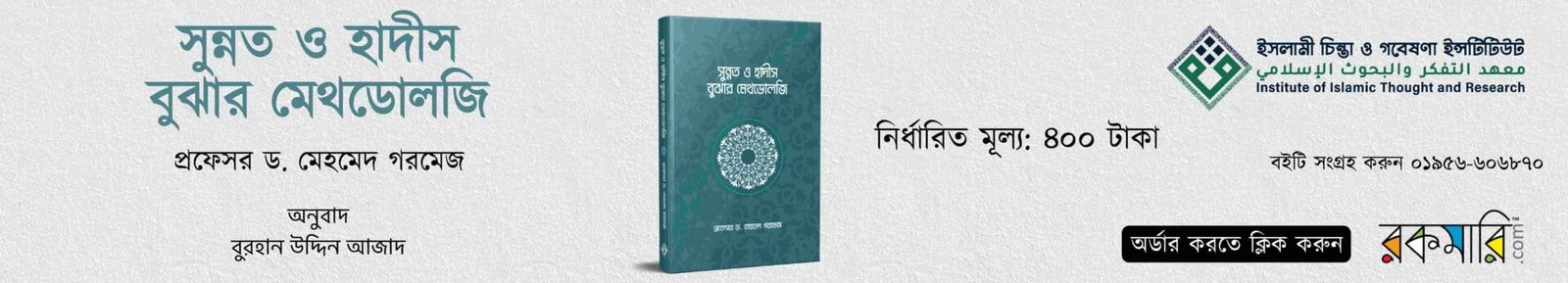
কিন্তু আমাদের সন্তানরা পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন ছেড়ে নিজেদের সাহিত্য, শিল্প, চিন্তা, সমাজের গঠন, বা বিশ্বদৃষ্টিকে নিজস্ব সভ্যতার চোখে না জানলে এই সভ্যতা কীভাবে টিকবে? এটা একটা বিশাল বড় সংকট; এখানেও এটা একটা দার্শনিক বিষয়ই। এটা শিক্ষাগত সমস্যা অবশ্যই, তবে শিক্ষার দর্শন শুধু ‘কীভাবে পড়ানো হবে’ তা নয়, ‘কী পড়ানো হবে’ তাও ঠিক করে।
আলহামদুলিল্লাহ, সবকিছু অন্ধকার নয়। আলোর আভাস রয়েছে। কিছু মানুষ এখন এই বিষয়গুলো বুঝতে শুরু করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। মরুভূমিতে একজন মানুষের চিৎকারও মূল্যবান, কারণ সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। আমি আশা ও দোয়া করি, আমাদের তরুণ প্রজন্ম, যাদের কেউ কেউ এখানে উপস্থিত, দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে মনোযোগ দেবে। মা-বাবাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আমি অধ্যাপক হিসেবে অনেক মুসলিম ছাত্র দেখেছি, যারা আমার এক-দুটি বক্তৃতা শুনে ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিসিন ছেড়ে ইসলামী অধ্যয়ন বা দর্শন পড়তে চেয়েছে। শোনা মাত্রই তাদের বাবা প্রায় হার্ট এটাক করেন, মা প্রায় মাথা ঘুরে রান্নাঘরে পড়ে যান।
যারা ইসলামকে ভালোবাসেন, আল্লাহর কথা ভাবুন, ইসলামের কথা ভাবুন, ইসলামের জন্য কিছু ত্যাগ করুন। আপনার সন্তানের শুধু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরি নয়। তাদের পাশাপাশি আমাদের এমন মুসলিমও প্রয়োজন, যারা এই বিষয়ে জান কুরবান করবে। হয়তো তারা কম আয় করবে, কিন্তু উম্মতের জন্য এটি অপরিহার্য। আমি প্রায়শই বলি, এটা ফরজে কিফায়া।
বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য উচিত ইহুদি সম্প্রদায়ের মতো কাজ করা, যারা আমেরিকায় মাত্র পঞ্চাশ বছরে ইহুদি অধ্যয়নের প্রায় সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহন করেছে। একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, আমেরিকার সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদি অধ্যয়নের অধ্যাপকরা এখন ইহুদি। তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা। আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন দুপুরের খাবারের সময় বন্ধুদের সঙ্গে এই বিষয়ে বলছিলাম। তখন শুধু ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদি অধ্যয়নের অধ্যাপক ছিলেন ইহুদি, বাকি সবাই ছিলেন হিব্রু ও তাওরাত জানা খ্রিস্টান। এখন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমনকি নিউ জার্সির ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেটন হলেও ইহুদি অধ্যয়নের অধ্যাপকরা ইহুদি। আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ, আমার মৃত্যুর পর কয়েক দশক পরে আপনারা যখন বক্তৃতা দেবেন, তখন কেউ ইসলামী বিশ্ব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এই কথা বলতে পারবেন। এটি নির্ভর করবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে ঈমানের সঙ্গে মিলিয়ে পুনরুজ্জীবিত করার ওপর। ঈমান ও আকল—এই দুটি আমাদের জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে সফল উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর দেওয়া সবচেয়ে বড় উপহার—আকলের সঠিক ব্যবহারই আমাদের পথ। আলহামদুলিল্লাহ।।
অনুবাদঃ হিশাম আল নোমান।