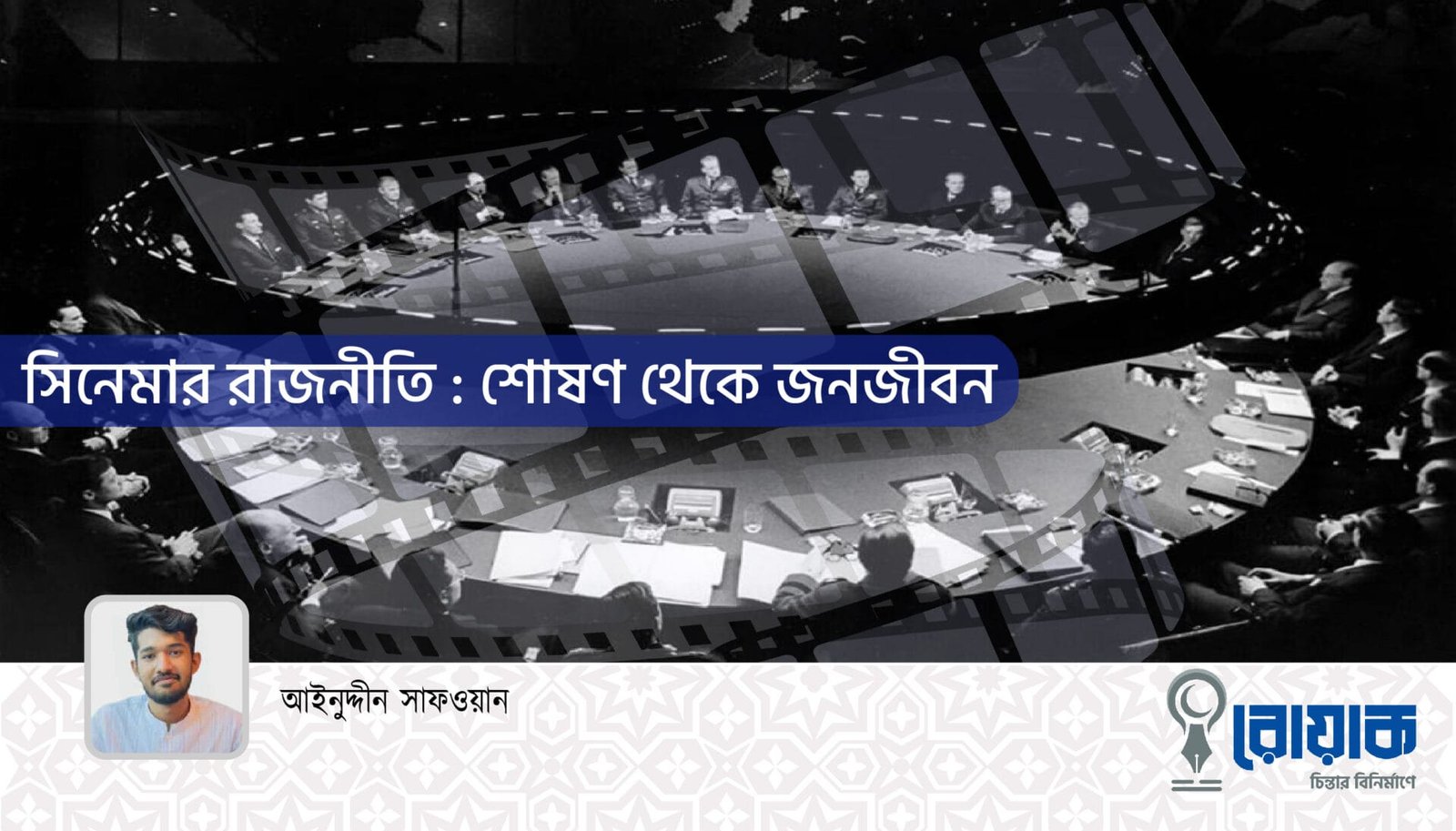পহেলা পর্ব–সিনেমায় রাজনৈতিক ভাষার সৃষ্টি
“সিনেমা হলো সমাজের আয়না” বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ফেদেরিকো ফেলিনির এই মন্তব্যের মতো করেই সিনেমার রাজনৈতিক ভাষা প্রভাবিত করেছে শিল্পের সকল মাধ্যমকে। রাজনৈতিক চলচ্চিত্র এমন এক মাধ্যম যেখানে পর্দায় যা দেখানো হয় এবং যা আড়ালে থাকে, তার মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র ও শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। এই চলচ্চিত্রগুলো শুধু বিনোদনের সীমাবদ্ধতার বাইরে গিয়ে সমাজের বিবর্তনের দিকে মানুষের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র সমাজের সংকট, শোষণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকে কেন্দ্র করে সমাজের সামনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। ফলে, চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক ভাষা ও ভাবধারা মানুষের চিন্তায় বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছে। রাজনৈতিক সিনেমাকে সম্বোধন করে এখনকার সময়ে বহু ধরনের এজেন্ডা ভিত্তিক সিনেমা নির্মাণ হয় যেখানে সত্যিকার অর্থে মানুষের দৃষ্টিকে এবং চিন্তাকে ভিন্নখাতে ধাবিত করাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে কিন্তু সিনেমার সাথে রাজনৈতিক এপ্রোচের পথঘাট যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে মূলত শুধু বিনোদন নামক শব্দের বাহিরে গিয়ে মানুষের দুর্দশা এবং বৈষম্যের সমাজকে দেখানোর উদ্দেশ্যই পৃথিবীর বহুজায়গায় সরাসরি গণমানুষের জীবনকে ফ্রেমবন্দি করা হয়। পরবর্তীতে এটাই রাজনৈতিক সিনেমা হিসেবে এস্টাবলিশমেন্টের পর্যায়ে আসে। এই আলোচনায় মূলত সেই শুরুয়াতের প্রেক্ষাপট এবং এই রাজনৈতিক সিনেমা কিংবা সিনেমার রাজনৈতিক ভাষার প্রভাব সম্পর্কে বলার চেষ্টা করবো।
রাজনৈতিক প্রভাবসম্পন্ন চলচ্চিত্রগুলো কেবল সমকালীন রাজনীতির প্রতিচ্ছবি নয়, বরং এটি ভবিষ্যতের রাজনীতির দিকনির্দেশও করে। চলচ্চিত্র পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর আদর্শিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস চলচ্চিত্রে প্রকাশ পায় এবং সেই ধারণাগুলো মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আহ্বান চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে।
চলচ্চিত্র কখনোই একমুখী যোগাযোগের মাধ্যম নয়। এটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিতর্ক উসকে দেয় এবং সমাজকে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। একদিকে, চলচ্চিত্রে যে রাজনৈতিক ভাষা প্রচারিত হয়, তা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; অন্যদিকে, সেই ভাষা সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলোকে চলচ্চিত্র নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্বিন্যস্ত করে। এই প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র একটি শিল্পমাধ্যমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে।
সিনেমায় রাজনৈতিক ভাষার ব্যবহার সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। ১৯২০-এর দশক থেকে সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালকরা যেমন সের্গেই আইজেনস্টাইন রাজনৈতিক ভাষার মাধ্যমে বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার বিখ্যাত চলচ্চিত্র “Battleship Potemkin” সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথমদিকের চলচ্চিত্রগুলোতে বিপ্লব, শ্রেণি সংগ্রাম, এবং সামাজিক বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো।
আইজেনস্টাইনের সংগ্রাম ছিলো শুধুমাত্র শিল্পের সীমাবদ্ধতা নয়, বরং রাজনৈতিক চাপে কাজ করার মধ্যেও। তিনি বলেছিলেন, “Cinema is, first and foremost, montage”– এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে একটি দৃশ্যের কাঠামোই রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তৎকালীন ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি চলচ্চিত্রকে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে দেখলেও, আইজেনস্টাইন এটিকে একটি শিল্পমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন বিপ্লবী বার্তা প্রচারের জন্য। সময়ের চলচ্চিত্রগুলো সাধারণত ক্ষমতা এবং জনগণের মধ্যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে নির্মিত হতো। এই ধারা সারা বিশ্বেই রাজনৈতিক সিনেমার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক উন্মোচন করে।
ইউরোপীয় সিনেমায় রাজনৈতিক ভাষা এবং প্রভাব
ইউরোপীয় সিনেমার ইতিহাসে রাজনৈতিক ভাষা ও প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপে চলচ্চিত্র শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি পরিণত হয় মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে। ইতালীয় নব্য-বাস্তববাদ (Italian Neorealism) আন্দোলন রাজনৈতিক সিনেমার একটি বিশাল মাইলফলক। যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরার মাধ্যমে এই ধারা একটি বিপ্লব ঘটায়। ভিট্টোরিও ডি সিকার “Bicycle Thieves” (1948) একটি উদাহরণ, যেখানে যুদ্ধের পর ইতালির অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে।
রবার্তো রোসেল্লিনির “Rome, Open City” (1945) চলচ্চিত্রটি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক। এই সিনেমাটি রোমের নাৎসি দখলকালে একটি প্রতিরোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যেখানে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিচালক দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে ফ্যাসিবাদ একটি দানবীয় শক্তি হিসেবে মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, এবং সাধারণ মানুষ কীভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।
ইতালীয় নব্য-বাস্তববাদের অন্যতম পুরোধা রবার্তো রোসেল্লিনি বলেছিলেন, “Realism is something that exists independent of us. ItÕs just there. The director has to have the courage to show it.” এই সাহসিকতা নিয়ে তারা যুদ্ধ-পরবর্তী ধ্বংসের বাস্তবতা এবং রাষ্ট্রের অব্যবস্থাকে তাদের সিনেমায় তুলে ধরেছেন। সেই সময়ে, ইতালির শাসকরা এই চলচ্চিত্রগুলোতে বাঁধা দিয়েছিলেন কারণ সেগুলো রাষ্ট্রের দুর্বলতাকে প্রকাশ করত। ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ (French New Wave) আন্দোলনও সমাজে রাজনীতি এবং সংস্কারের প্রতি বিরোধিতা নিয়ে তৈরি হয়েছিলো। জঁ-লুক গদার, একজন বড় বিপ্লবী পরিচালক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন। তার বিখ্যাত চলচ্চিত্র “La Chinoise” (1967) নির্মাণ করে মাওবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করেন। গদার বলেন, “Cinema is not the reflection of reality, it is the reality of that reflection.” তিনি বিশ্বাস করতেন যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের অন্ধকার দিকগুলোকে তুলে ধরা সম্ভব। তবে তার নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারার কারণে তাকে প্রচুর বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং অনেক সময় তার চলচ্চিত্রগুলো সেন্সরশিপের শিকার হয়েছে।
আফ্রিকান চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক ভাষার প্রভাব এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিফলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকার অন্যতম প্রভাবশালী পরিচালক ওসমান সেম্বেন কে বলা হয় “আফ্রিকান সিনেমার জনক”। তার “La Noire de…” (1966) চলচ্চিত্রটি ঔপনিবেশিক শোষণ এবং আফ্রিকান নারীর জীবনের দুঃখ-দুর্দশাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। সেম্বেন বলেছিলেন, “I do not want to be a politician, but I am committed to politics because that is life.” তার এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি রাজনীতিকে জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখতেন, এবং তার চলচ্চিত্র সেই রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রকাশ।
সেম্বেনের সংগ্রাম শুধুমাত্র চলচ্চিত্র তৈরির জন্য অর্থায়ন পাওয়া নয়, বরং সেন্সরশিপ এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র শিল্পের বিরুদ্ধে লড়াই ছিলো। ওসমান সেম্বেনের “Xala” (1975) সিনেমাটি আফ্রিকার পুঁজিবাদী অভিজাতদের সমালোচনা করে, যারা স্বাধীনতা লাভের পরেও ঔপনিবেশিক শোষণের ধাঁচে নিজেদের জনগণকে শোষণ করতে থাকে। এই চলচ্চিত্রে সেম্বেন দেখিয়েছেন কিভাবে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা আফ্রিকার সাধারণ মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের অধিকার কেড়ে নেয়।
সেম্বেন বলেছিলেন, “Cinema is a night school, a place for education.” তার চলচ্চিত্রে এই শিক্ষা পাওয়া যায়, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পুঁজিবাদ এবং ঔপনিবেশিক শাসন আফ্রিকার জনগণকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।
ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ে আফ্রিকার সিনেমা সমাজের শোষণ এবং জাতিগত স্বকীয়তার দিকে মনোনিবেশ করে, এবং অনেক সময় এই চলচ্চিত্রগুলো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসা কুড়িয়েছে কিন্তু নিজ দেশের সরকার এবং সেন্সরবোর্ডের কাছ থেকে বাধা পেয়েছে।
ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায় ফ্যাসিবাদের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সিনেমার সংস্কৃতি। যুগের পর যুগ ধরে কেবল এই মাধ্যমেই জুলুমের অন্ধকারকে রঙিন করার চেষ্টা চলেছে।
ফ্যাসিবাদী শাসনগুলি সিনেমাকে তাদের আদর্শের প্রচারক হিসেবে ব্যবহার করেছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জোসেফ গোয়েবলস, হিটলারের প্রচারণা মন্ত্রী, সিনেমাকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন যাতে নাৎসি মতাদর্শের প্রচার করা যায়। নাৎসি জার্মানির সময়, ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক প্রযোজিত সিনেমাগুলোকে সাধারণত তাদের নৃশংস শাসন ও জাতীয়তাবাদের প্রচারক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিলো। এই সময়ে নির্মিত বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র, যেমন “Triumph of the Will” (1935), পরিচালিত লেনি রিফেনস্টাল, হিটলারের নেতৃত্বের প্রশংসা ও নাৎসি দলের রাজনৈতিক শক্তিকে মহিমান্বিত করেছে। ফ্যাসিবাদী আদর্শ, জাতিগত উচ্চতার ধারণা, এবং একনায়কতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস সিনেমার মাধ্যমে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছিলো।
ফ্যাসিস্ট ও একনায়কতান্ত্রিক সরকারগুলো শিল্পের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলো এবং ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করা যেকোনো চলচ্চিত্র নির্মাণের কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলো। ফলে সিনেমা হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদী প্রচারণার হাতিয়ার, যেখানে শুধুমাত্র শাসক দলের আদর্শ প্রচারিত হয়েছিলো, এবং সমাজের নিম্নবিত্তদের জন্য কোনো জায়গা ছিলো না।
সিনেমাকে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে উন্মুক্ত করে যিনি সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছেন তার নাম ‘চার্লি চ্যাপলিন’। সিনেমা এবং তার সাথে মিলেমিশে থাকার রাজনীতিতে চার্লি চ্যাপলিন হচ্ছেন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক নাম। চ্যাপলিনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গড়ে ওঠার পেছনে বড় ভূমিকা ছিলো তাঁর শৈশবের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন। লন্ডনের দারিদ্র্যে বেড়ে ওঠা চ্যাপলিনের চলচ্চিত্রগুলোতে বারবার নিম্নবিত্ত মানুষের কষ্ট ফুটে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত চরিত্র ‘ট্র্যাম্প’ সেই অবহেলিত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে, যার জীবনের হাস্যরসাত্মক চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে সমাজের বড় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। ট্র্যাম্পের জীবনে দারিদ্র্য, অসমতা এবং নিপীড়নের মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা ছিলো পুঁজিবাদী সমাজের তীব্র সমালোচনা। ÒModern TimesÓ (1936) চলচ্চিত্রে এর স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে চ্যাপলিন শিল্পায়ন এবং যান্ত্রিকতার অমানবিক প্রভাবগুলো তুলে ধরেছেন। চলচ্চিত্রের ট্র্যাম্প চরিত্রটি একটি যান্ত্রিক পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, যেখানে শ্রমিকদের কেবল একটি মেশিনের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারখানার দৃশ্য, যন্ত্রের অংশে আটকে যাওয়া এবং মেশিনের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সিকোয়েন্সগুলো পুঁজিবাদী শিল্প ব্যবস্থা এবং এর শোষণমূলক প্রকৃতির তীব্র সমালোচনা করে। যদিও চ্যাপলিন এখানে কমেডি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম এবং শোষণের বিরুদ্ধে বার্তা স্পষ্ট ছিলো।
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই : ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ এবং রাজনৈতিক বিদ্রুপ: চ্যাপলিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হলো ÒThe Great DictatorÓ (1940), যা সরাসরি ফ্যাসিবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, বিশেষ করে অ্যাডলফ হিটলার এবং নাৎসি শাসনের সমালোচনা করে। এটি এমন এক সময়ে মুক্তি পেয়েছিলো যখন হলিউড সরাসরি নাৎসি জার্মানির সমালোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। তবে চ্যাপলিন এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে হিটলারকে বিদ্রুপ করেন এবং চলচ্চিত্রের শেষ অংশে একটি আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মানবতা এবং শান্তির জন্য একটি শক্তিশালী আহ্বান জানান।
এই চলচ্চিত্রে চ্যাপলিন একসঙ্গে দুটি চরিত্রে অভিনয় করেন-একজন ইহুদি নাপিত এবং একজন স্বৈরাচারী শাসক। চলচ্চিত্রটি ক্ষমতাবান এবং নির্যাতিত মানুষের জীবনকে পাশাপাশি দাঁড় করায়। হাস্যরসের মাধ্যমে তিনি ফ্যাসিবাদী মতবাদ, ইহুদি বিদ্বেষ এবং একনায়কতন্ত্রের বিপদগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছেন। চলচ্চিত্রের সমাপনী ভাষণে চ্যাপলিন স্বৈরাচারের বিপরীতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং ঐক্যের আহ্বান জানান, যা আজও এক অনন্য রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে রয়ে গেছে।
ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর প্রভাব :
ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প শুরু থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসছে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিলো মানুষের দুঃখ-কষ্ট, শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং একটি বিপ্লবী চেতনা গড়ে তোলা। উপমহাদেশের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং পরবর্তীতে আধুনিককালের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বÑসবকিছুই রাজনৈতিক সিনেমাগুলোর মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। এই অঞ্চলটির রাজনৈতিক চলচ্চিত্রশিল্প বিভিন্ন সময়ে জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে, যা শুধু বিনোদন নয়, বরং একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ এবং আধুনিক রাজনীতির বিভিন্ন সংকট, সবকিছুই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সমাজের চিন্তাভাবনার ওপর বিশাল প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যে তীব্র হয়ে উঠেছিলো, সেই প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র ছিলো একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যুগে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য তাদের চলচ্চিত্রগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, রাজ কাপুর এবং মৃণাল সেনের মতো কিংবদন্তি পরিচালকেরা ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাগুলোকে তাদের চলচ্চিত্রে নিয়ে আসেন। তাদের কাজগুলো নিছক বিনোদনমূলক ছিলো না, বরং ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ে সমাজের গভীর বৈষম্য, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা, এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা ও এ কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করাটাও উপস্থিত ছিলো।
ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর সময় এবং নতুন রাজনৈতিক চেতনা :
স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ধারা আরও জোরালো হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের চলচ্চিত্রগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ÒMother IndiaÓ (1957) নামক ভারতীয় চলচ্চিত্রে কৃষক সমাজের সংগ্রাম এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে একটি নতুন ধারা তৈরি হয়। এই চলচ্চিত্রটি শুধুমাত্র একক কোনো নারীর জীবনের চিত্রায়ন ছিলো না, বরং এটি সমগ্র দেশের দারিদ্র্য, শোষণ, এবং শ্রেণিসংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এটি একধরনের বিপ্লবী চেতনার সূচনা করে, যা পরবর্তীতে ভারতের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। পাকিস্তানের চলচ্চিত্রশিল্পেও ঔপনিবেশিক শাসন এবং নতুন রাজনৈতিক সংকটগুলো তুলে ধরতে অনেক নির্মাতা চেষ্টা করেছেন। ষাট এবং সত্তরের দশকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। ÒZarqaÓ (1969) চলচ্চিত্রটি এই অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে একজন ফিলিস্তিনি নারীর সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাস এবং প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, এর গভীরে গিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করতে হয়। রাজনৈতিক চলচ্চিত্র এই দেশে সবসময়ই ক্ষমতাসীন শাসনব্যবস্থা, জনগণের সংগ্রাম, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের নিরিখে একটি কার্যকর প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে এদেশের চলচ্চিত্রগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রাজনৈতিক ভাষার মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত হেনেছে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের প্রাথমিক আলোচনায় চলে আসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলি বাংলাদেশের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে আসে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে এক বিশাল প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসকে সংরক্ষণই করেনি, বরং তা নতুন প্রজন্মের কাছে জাতীয়তাবাদী আদর্শের পুনর্র্নিমাণ হিসেবে কাজ করেছে। কিংবদন্তি জহির রায়হান একটি বিশ্বাস ধারণ করতেন যেটি হলো ‘সিনেমা শুধু বিনোদন নয়, এটি একটি বিপ্লবী মাধ্যম যা সমাজকে পরিবর্তন করতে এবং মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে’। জহির রায়হানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে “জীবন থেকে নেওয়া” (১৯৭০) উল্লেখযোগ্য, যা সরাসরি পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি রূপক হিসেবে কাজ করেছে। এই চলচ্চিত্রে পারিবারিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থার দমনমূলক প্রকৃতিকে তুলে ধরা হয়, যা একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে শক্তিশালী করেছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হয়েছে। এই চলচ্চিত্রে তিনি অত্যন্ত কৌশলীভাবে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা সে সময়ের মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলো। এই ধরনের চলচ্চিত্র জাতির চেতনার অংশ হয়ে উঠেছিলো এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিলো।
জহির রায়হানের অন্যতম বিখ্যাত কাজ হলো “স্টপ জেনোসাইড” (১৯৭১), যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যা এবং নির্যাতনের বাস্তবতা তুলে ধরে। এই তথ্যচিত্রটি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চিত্রকে তুলে ধরে। তাঁর এই কাজ কেবল ইতিহাসের দলিল নয়, বরং জনগণের প্রতি তাঁর গভীর সংবেদনশীলতার পরিচয়ও বহন করে। তিনি জানতেন যে রাজনৈতিক সিনেমা মানুষের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে তা শুধুমাত্র একটি মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। তাই, তিনি সাধারণ মানুষের যন্ত্রণাকে ফ্রেমে ধরার জন্য তাঁর ক্যামেরাকে একধরনের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। জহির রায়হানের চলচ্চিত্রগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো সমাজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা শোষণ এবং দমন-পীড়নের চিত্র তুলে ধরা। তিনি খুবই দক্ষভাবে তাঁর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের দুর্দশা এবং তাদের বিরুদ্ধে চলমান শোষণের চিত্রায়ণ করেছেন। তাঁর “হাজার বছর ধরে” উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণে তিনি গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরেন, যেখানে শোষণ এবং বৈষম্য মানুষকে ক্রমাগতভাবে নিঃশেষ করছে। এই চলচ্চিত্রে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী, কারণ তিনি সাধারণ মানুষের যন্ত্রণাকে অত্যন্ত আবেগময় এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তুলে ধরেছেন। জহির রায়হানের কাজগুলোতে রাজনৈতিক ভাষা শুধু কাহিনীর অংশ ছিলো না, বরং এটি তাঁর চিত্রগ্রহণ, চরিত্রের সংলাপ এবং গল্পের কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কাজগুলোতে দেখা যায়, তিনি সবসময় ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলেছেন। তাঁর চলচ্চিত্রগুলোতে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে রাজনীতি, সংগ্রাম এবং শোষণের বিষয়গুলো গভীরভাবে সংযুক্ত ছিলো।
চলচ্চিত্র, বিশেষ করে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমাজকে জাগ্রত এবং প্রভাবিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আসছে। এটি কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং সমাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসাম্য, দমন-পীড়ন এবং শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনায় একটি বিপ্লবী বার্তা পৌঁছে দেয়। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ভাষার প্রয়োগ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনগণের মনোভাব এবং রাষ্ট্রের দমনমূলক ব্যবস্থাকে পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছে। আইজেনস্টাইন বলেছিলেন, ÒCinema is a weapon.Ó অর্থাৎ, চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও প্রতিবাদকে জাগ্রত করতে পারে।
ঋত্বিক ঘটকের মতে ÒCinema is a tool for awakening the sleeping minds of a nation.Ó সিনেমা একটি জাতির ঘুমন্ত মানসকে জাগ্রত করে তোলার এক শক্তিশালী হাতিয়ার।
পরিশেষে, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাষার প্রয়োগ অতীতের শোষণবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে বর্তমানের সামাজিক পরিবর্তনের চেতনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এটি সমাজকে চিন্তাশীল, সচেতন এবং প্রতিবাদী হতে সাহায্য করেছে। বিখ্যাত ইতালিয়ান পরিচালক পিয়ের পাওলো পাসোলিনি একবার বলেছিলেন, ÒCinema is not a reflection of reality; it is the reality of reflection.Ó চলচ্চিত্র শুধুমাত্র বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বরং এটি সমাজের ওপর এক গভীর প্রতিবিম্ব তৈরি করে, যা মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করতে এবং শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করে।
চার্লি চ্যাপলিনের “দ্য গ্রেট ডিক্টেটর” ফ্যাসিবাদ এবং হিটলারের নীতির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ ছিল। চ্যাপলিন বলেছিলেন, ÒThe soul of man has been given wings, and at last, he is beginning to fly.Ó মানুষের আত্মাকে পাখা দেওয়া হয়েছে, এবং অবশেষে তারা উড়তে শুরু করেছে। অর্থাৎ, তিনি বলতে চান, মানুষের আত্মা এখন মুক্তি পেতে শুরু করেছে, এবং এই মুক্তি কেবল রাজনীতির মাধ্যমেই সম্ভব।