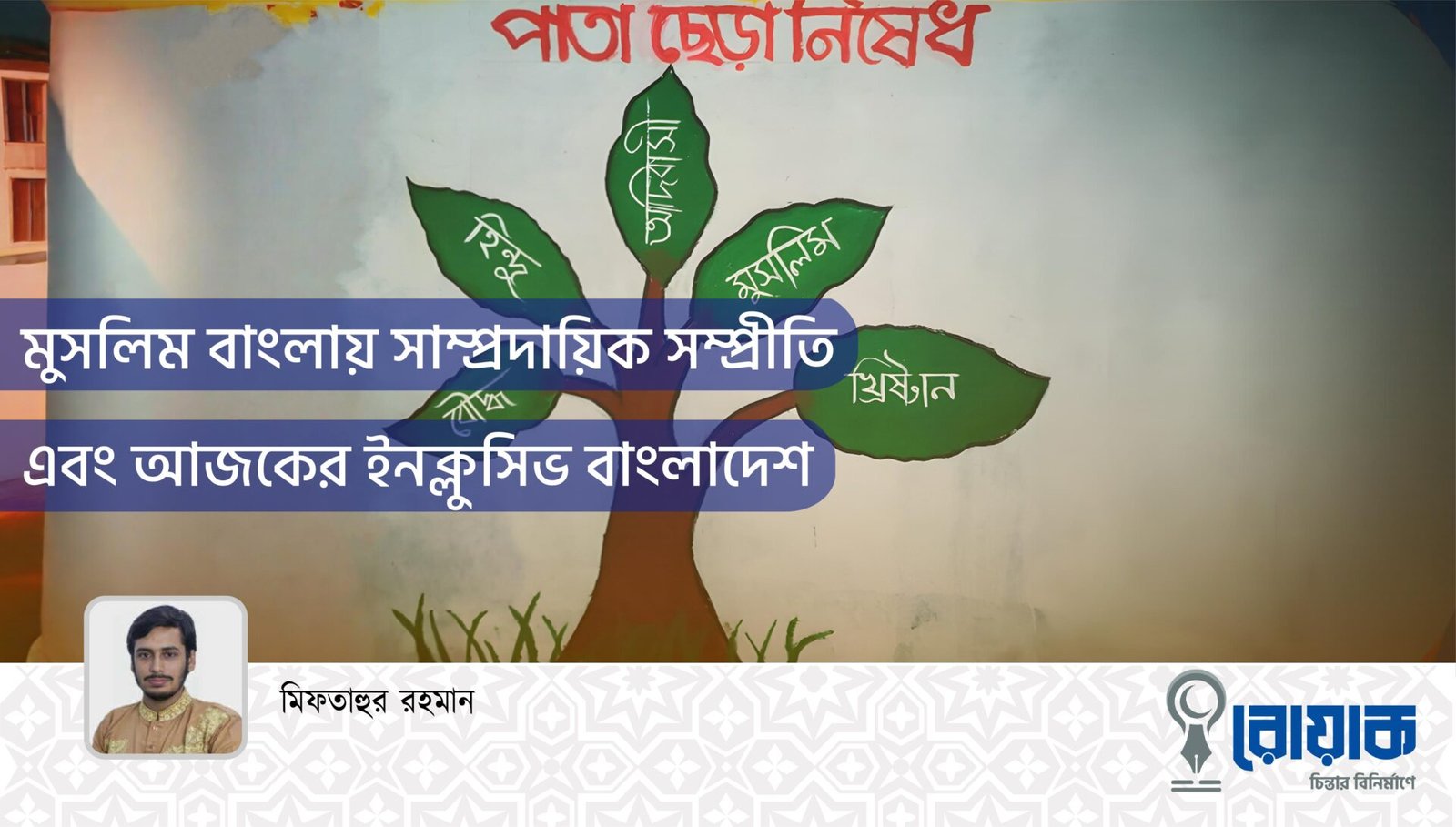এক.
গত জুলাই আন্দোলনের পর থেকেই “ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ” পরিভাষাটা বেশ অনেকবারই সামনে এসেছে। আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও যখন এদেশের জনসাধারণ এমন একটি গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত করে, এরপর আবার “স্বাধীন বাংলাদেশ ২.০” পরিভাষারও উৎপত্তি করে, তখন আসলেই উপলব্ধি হয় যে, এমন একটি গণঅভ্যুত্থান আমাদের জন্য কেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো! স্বাধীন বাংলাদেশ ২.০-এর শুরুতেই বাংলাদেশ কেমন হবে, তা নিয়ে প্রতিটি মতাদর্শ থেকেই আলোচনা আসতে থাকে। এমন সময়ই “ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ” পরিভাষাটা বারংবার শোনা যায়।
সহজ ভাষায়, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ হচ্ছে এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে না কোনো ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণিগত ভেদাভেদ। সকল ধর্মের, সকল গোত্রের এবং সকল শ্রেণিপেশার মানুষই দেশের যেকোনো নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকেও প্রত্যেককেই সমান অধিকার দেওয়া হবে। গত ৩৬ জুলাইয়ের পর যখন রাষ্ট্রীয় ও সমাজ সংস্কার নিয়ে কথা উঠেছিলো, মূলত সেসময়টাতেই এই পরিভাষাটা শোনা গিয়েছে। আর এই পরিভাষাটা এমনভাবে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছিলো, যেনো ইতোপূর্বে কখনই এদেশের কোনো ব্যক্তিরই এই বিষয়ের উপর ধারণা ছিলো না। কিন্তু, আসলেই কি তাই? ইতিহাস কী বলে এ-নিয়ে?
ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ-এর সংজ্ঞায়নের একেবারে মৌলিক বিষয় হচ্ছে, ধর্ম, বর্ণ ও মতাদর্শ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণই রাষ্ট্রের কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে পারবে এবং রাষ্ট্র থেকে কখনই কোনো ব্যক্তিকে পৃথক করে দেখা হবে না। এখন, আমরা যদি অতীত ইতিহাসের আলোকে আমাদের বর্তমানকে পর্যালোচনা করতে এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যতকে সাজিয়ে নিতে চাই, তাহলে মুসলিম বাংলার ইতিহাসকে সামনে রেখে এসব বিষয়াবলিকে পর্যালোচনা করতে হবে এবং দেখতে হবে যে, আজকের “ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ” বলতে আমাদের সামনে যে ধারণা উপস্থাপিত হচ্ছে, তা আদৌ আনকোড়া নতুন নাকি অতি পুরাতন, যা আমরা আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই আমাদের থেকে আড়াল হয়ে রয়েছে।
যেহেতু বাংলা অঞ্চলের অতীত ইতিহাসের সোনালী সময় নিয়ে কথা হবে, তাই মুসলিম বাংলার সময়কালটা অতি সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। ১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করেন। এরপর বাংলায় শুরু হয় খিলজী শাসন, চলে ১২২৭ সাল পর্যন্ত। খিলজী শাসনের পর শুরু হয় দিল্লি সালতানাত বা সুলতানী আমলের শাসন, যা চলে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। এরপরেই শুরু হয় স্বাধীন সার্বভৌম সালতানাতে বাঙ্গালা, প্রায় ২০০ বছর ধরে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলা শাসন করে স্বাধীন সুলতানরা। এরপর শুরু হয় আফগান শাসন। মাত্র কিছুদিনের আফগান শাসনের পর সম্রাট আকবর আবারো বাংলা জয় করেন। শুরু হয় সুবা বাংলার আমল। এরপর ১৭১৭ সালে নবাব মুর্শিদকুলী খানের মাধ্যমে শুরু হয় নবাবী আমল, যার শেষটা হয় ১৭৫৭ সালের পলাশীর বিপর্যয়ের মাধ্যমে। পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুসলিম সমাজের উপর নেমে পরাধীনতার খরগ।
দুই.
ইতিহাসের পাতায় খাতায়-কলমে ২০০ বছরের সালতানাতে বাঙ্গালা হলেও আলোচনার ক্ষেত্রে পুরো মুসলিম শাসনামলকেই কেন্দ্রে রাখা হবে। তাহলে শুরুটা করা যাক প্রায় সাড়ে পাঁচ শতকের মুসলিম বাংলায় ধর্মীয় সম্প্রীতি কেমন ছিলো, তা নিয়ে।
প্রাক মুসলিম ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিলো খুবই ভয়ংকর। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রকট আকার ধারণ করে। ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এ’চার শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজে নিম্ন শ্রেণির লোকদের বিশেষ করে শূদ্রদের দুরাবস্থার কোনো সীমা ছিলো না। শূদ্ররা সমাজে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো। এমন কি ধর্ম-কর্ম পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো। ঐতিহাসিক আল বেরুনী তার “কিতাবুল হিন্দ” নামক গ্রন্থে বলেন যে,
❝কোনো বৈশ্য এবং শূদ্র বেদ-গীতা পাঠ করলে, এমনকি বেদবাক্য শুনলেও শাস্তি হিসেবে তার জিহ্বা কেটে দেওয়া হতো। ভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে অন্তবিবাহ ও পানাহার নিষিদ্ধ ছিলো। এমনকি শূদ্রদের স্পর্শও অপবিত্র ছিলো। সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। জাতিচ্যুতদের ভাগ্য আরও খারাপ ছিলো। বেদ শ্রবণ করলে কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দেওয়া হতো।❞
প্রাক মুসলিম আমলে এই ছিলো সমগ্র ভারতের ধর্মীয় সহাবস্থানের নমুনা। বিপরীতে মুসলিম বাংলায় ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। মুসলিম শাসকরা উদার ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করেন। মুসলিম শাসনামলে ভারতের হিন্দুরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো। তাদেরকে দেওয়া হয় ধর্মীয় স্বাধীনতা। ফলে, এই অঞ্চলের অমুসলিমরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারতো। বখতিয়ার খিলজির সেই অভিযানের পর এই অঞ্চলের প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতির উপর ইসলামের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছেদ ও সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে।
হিন্দু ও মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে এস. এ. এ. রিজভী বলেন যে, ❝ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনে অনেক সুযোগ-সুবিধাকে উন্মোচিত করেছিলো।❞
রোমিলা থাপার মতে, ❝ব্রাহ্মণরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হলেও হিন্দু-মুসলিম মিলনের স্রোত ক্রমশ গতিশীল হয়ে ওঠে।❞
অতএব, বুঝা গেলো যে, মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিলো। আবার, সরকারি চাকরি করবার সুবাদে কিংবা মুসলমান শাসনকর্তাদের সভাসদ ও রাজকর্মচারী হিসেবে অথবা মুসলিম জনগণের প্রতিবেশী রূপে হিন্দুরা মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে। যার ফলে তারা মুসলমানদের মহৎ আদর্শ সংস্কৃতি এবং শিষ্টাচার ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়। পাশাপাশি, মুসলিম শাসক ও সুলতানদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে।
এজন্যই, সাধারণ হিন্দুদের উপর ইসলাম ধর্ম দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অথচ, সাধারণ হিন্দুদের কোনো মর্যাদাই ছিলো না। সমাজে উচ্চ ধর্মের হিন্দুর সাথে নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিলো। নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থও পাঠ করতে পারতো না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা শিক্ষা অর্জন করতো। কিন্তু বাংলার মুসলিম শাসকরা উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বাংলায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া প্রাধান্য খর্ব হয়। নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও শিক্ষা অর্জন করেন। সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন ঘটে। তারা সংস্কৃত পাশাপাশি ফার্সি ভাষাও শিক্ষা অর্জন করে উচ্চ রাজ কার্যে নিয়োজিত হয়ে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করে।
অন্যদিকে, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের পরেই ছিলো কায়স্থদের স্থান। মুসলমানদের দ্বারা তারাও প্রভাবান্বিত হয়। তারা শিল্প ও সাহিত্যে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেয়। মুসলিম শাসকরা উদারভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এসব বিখ্যাত কবিদের মধ্যে ছিলেন-মালাধর বসু (গুণরাজ খান), কবিন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, যশোরাজ খান, বিজয় গুপ্ত, কৃষ্ণ দাস কবিরাজ। মুসলিম শাসনামলে কায়স্থরা জমিদারি ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করে। মুসলিম শাসক কর্তৃক এসব কায়স্থরাই পরবর্তীতে রায়, চৌধুরী, মজুমদার, অধিকারী উপাধী লাভ করে। এটি পরবর্তীকালে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে এবং আরো পরবর্তীতে গিয়ে দেখা যায় যে, এসব পদবী মানুষের নামের সাথেও যুক্ত হয়ে যায়।
আবার, বাংলার সুলতানরা ছিলেন উদার সংস্কৃতিমনা। তারা হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং হিন্দুদের প্রতি মুসলিমদের প্রতিবেশী সুলভ মনোভাব মধ্যযুগে বাংলা হিন্দু মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আরেকটি কারণ। মূলত, এসব কারণেই যুগ যুগ ধরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রীতি্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
তিন.
এবার তাহলে দেখা যাক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় কেমন ছিলো। এটা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, যেখানে ধর্মীয় সহাবস্থান থাকে, সেখানেই অবশ্যই প্রশাসনিক সহাবস্থানও থাকবে। এর অন্যতম একটি উদাহরণ হচ্ছে মুসলমান আমলে হিন্দু শাসক ও সেনাপতি নিয়োগ।
বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মুসলমান শাসকগণ স্থানীয় হিন্দুদের শাসনকার্যে সংম্পৃক্ত করেন। শাসনকার্যে সুযোগ পেয়ে এসব হিন্দুরা যথেষ্ট যোগ্যতার ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। মুসলিম সুলতানগণ প্রতিভাবান হিন্দুদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ, রাষ্ট্রীয় উপাধী এবং সরকারি জমি দান করেন। হিন্দুরা খুবই বিশ্বস্ততার সাথে মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করে। বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন বাংলার হিন্দুরা বাংলার সুলতানের হয়ে যুদ্ধ করেছিলো। হিন্দু সেনাপতি সহদেব এ-যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। নবাবী আমলে আমরা দেখি যে, পলাশীর যুদ্ধের সময় নবাব সিরাজের সেনাপতি মীর মর্দন ও মোহনলাল দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করে।
শুধু এতোটুকুই নয়, মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই হিন্দু জমিদার শ্রেণীরও উৎপত্তি হয়। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল তার বিখ্যাত গ্রন্থ “বাঙালার সামাজিক ইতিহাসে” লিখেন যে, ইলিয়াস শাহী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই রাজশাহী জেলায় বিখ্যাত ‘সান্যাল’ এবং “ভাদুড়ী পরিবারের” উৎপত্তি হয়। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আযম শাহের রাজত্বকালে ভাতুড়িয়ার জমিদার কংস (রাজা গণেশ) যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
আবার, এর বিপরীতে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের অধীনে মুসলিম কর্মচারীও নিয়োগ হয়। মুসলিমদের শাসকদের মতো হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদাররাও তাদের শাসনকার্যে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করতেন। মীর্জা নাথানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ভুলুয়ার (নোয়াখালি) হিন্দু জমিদার অনন্তমানিক্য মীর্জা ইউসুফ নামক এক ব্যক্তিকে উজির পদে নিয়োগ দেন। এছাড়াও, চাঁদ রায় ও কেদার রায় সোলায়মান লোহানী নামে এক মুসলিমকে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দান করেন। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা এবং “কালাপাহাড়” নামে খ্যাত শ্রীহরি ছিলো দাউদ খান কররানীর অন্যতম উপদেষ্টা ও সেনাপতি।
অতএব, এটাও সত্য যে, ধর্মীয় সহাবস্থানের পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সহাবস্থান বজায় ছিলো।
চার.
এই ছিলো মুসলিম বাংলায় হিন্দু-মুসলিম প্রশাসনিক সমন্বয়। এখান থেকে আবার এটাও বলা যায় যে, যে সমাজে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সহাবস্থান থাকে, সেখানে তো বিচারব্যবস্থায় আদালত থাকবে, এটাই সত্য ও স্বাভাবিক। তবে এটা যে শুধু মুখে বললেই হবে, তা নয়। বরং অসংখ্য মুসলিম বিচারব্যবস্থার ঘটনা থেকে একটামাত্র উদাহরণ দেখা যাক।
সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম এবং ইলিয়াস শাহী বংশের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ সুলতান। সুলতান গিয়াস উদ্দিন শাহ একজন ন্যায়বিচারক শাসক ছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনে সুলতানের ন্যায়বিচারের একটি কাহিনী রয়েছে। তিনি একবার তীর ছুঁড়তে গিয়ে এক বিধবা মহিলার পুত্রকে হত্যা করে ফেলেন। বিধবা মহিলা তৎকালিন প্রধান বিচারপতি কাজী সিরাজ উদ্দিনের কাছে বিচারপ্রার্থী হলেন। প্রধান বিচারপতি নির্ভয়ে সুলতানের নামে সমন জারী করলেন। সুলতান বিচারপতির আদালতে হাজির হলে বিচারপতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন না করে তাঁর বিরুদ্ধে বিধবার আনীত অভিযোগের কথা উল্লেখ করেন এবং বিধবাকে ক্ষতিপূরণ দানে সন্তুষ্ট করতে না পারলে শরীয়ত মতে সুলতান দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সুলতান বিধবাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করেন এবং বিধবা অভিযোগের সন্তোষজনক মিমাংসার কথা বিচারপতিকে অবহিত করেন।
সুলতান তখন শাহী আসন থেকে উঠে এসে বিচারপতিকে সালাম দিয়ে বলেন, ❝আমার রাজ্যে এমন একজন ন্যায় বিচারক আছেন এজন্য দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। বিচারপতি, আপনি আইনের বিধান লঙ্ঘন করলে আমার তরবারি দিয়েই আমি আপনার মস্তক ছেদ করতাম।❞
প্রতি উত্তরে বিচারপতি বলেন, ❝আমার নির্দেশ আপনি অমান্য করলে আমিও আপনাকে বেত্রাঘাত করতাম।❞
পরবর্তীতে, সুলতান বিচারপতিকে ন্যায়বিচারের জন্য পুরষ্কৃত করেন।
পাঁচ.
এবার তাহলে ভাষা-সাহিত্যের উদাহরণও দেখা যাক। প্রশ্ন আসতে পারে যে, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে ভাষা-সাহিত্যের বিষয় কেন আসবে? ভাষা তো বহমান, কালের আবর্তে ভাষা পরিবর্তন হবে এটাই স্বাভাবিক! হ্যাঁ, কালের আবর্তে ভাষা পরিবর্তন হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, নতুন করে যদি ভাষাকে সংস্কার করা হয় বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভাষাকে বিকৃত করা হয় অথবা কোনো ভাষাকে সমূলে বিনাস করা হয়, তাহলে তখনও কি একথা প্রযোজ্য হবে? অবশ্যই না। কিন্তু, ইতিহাসে সেটাই হয়েছে।
ভাষার ধারাবাহিকতায় পাল আমলে যে বাংলা ছিলো, তা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলো সেনরা। বাংলার পরিবর্তে সেনরা সংস্কৃত-কে সামনে এনেছিলো। এমনকি, বাংলা ভাষাকেই তারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। মুসলিমরা এসে সে বাংলাভাষাকে আবারো গতিশীল করে দিয়েছিলো। শুধু বাংলাই নয়, মুসলিমরা এতোটা উদার ছিলো যে, বাংলা ও সংস্কৃত—দুই ভাষাকেই একইসাথে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। এক্ষেত্রেও, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিই হয়েছে।
কেননা, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপনে হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের অবদান ছিলো অপরিসীম। বাংলার সুলতানরা উদারভাবে হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে “রায় মুকুট” উপাধী প্রদান করেন। হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও সাহিত্যিকরা বাংলায় “রামায়ণ” ‘মহাভারত’ অনুবাদ করেন। সুলতানি আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেরও অসামান্য উন্নতি হয়। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মন্ত্রী রূপগোস্বামী ২৫টি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করে সংস্কৃত ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাশ, মালাধর, পরমেশ্বর কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দীর রচনার দ্বারা ঐ যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো। মুঘল শাসনামলেও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাংলা-সংস্কৃত ভাষার উন্নতিতে মুঘলরা যথেষ্ট অবদান রাখে। এসবই বাংলায় হিন্দু মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রমাণ করেন। অতএব, এটা সত্য যে, মুসলিম সুলতানদের জামানায় বাংলা ভাষার বিশেষ বিকাশ ঘটেছিলো। সুলতানদের সাহায্য ছাড়া বাংলা ভাষা আজকে সংস্কৃত ভাষার মতো একটি মৃত ভাষায় পরিণত হতো।
বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার প্রশংসা করতে গিয়ে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন,
❝ব্রাহ্মণগণ প্রথমদিকে বাংলা ভাষা গ্রহণ ও প্রচারের বিরোধী ছিলো। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে তারা ‘সর্বনেশে’ উপাধি প্রদান করেছিলো। যদি হিন্দু রাজাগণ স্বাধীন থাকতো, তাহলে কদাচিৎ বাংলা ভাষা তাদের দরবারে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করতো। আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিলো। মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হতেই আসুক না কেনো, এ’দেশে এসে তারা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালি হয়েছেন।❞
আর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, ❝দিল্লি সাম্রাজ্যের অধীনে শান্তি ও আর্থিক উন্নতির ফলস্বরূপই দেশীয় ভাষা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে।❞
ড. লক্ষ্মীধর বলেন, ❝আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে, দেশীয় ভাষা হিন্দিকে সর্বপ্রথম মুসলমানগণই সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। অথচ আমরা জানি যে, ব্রাহ্মণগণ ইতর ভাষা বলে এই ভাষাকে অবহেলা করেছেন।❞
মুসলিমরা যে এভাবে বাংলা ও সংস্কৃতিকে পুনরায় সামনে নিয়ে এলো, তা আবার ধ্বংস হয়ে যায় পলাশীর বিপর্যয়ের পর। ইংরেজদের “ডিভাইড এন্ড রূল” পলিসির ক্ষেত্রে এই ভাষার বিনির্মাণটাকেই কাজে লাগিয়েছে ইংরেজরা। ম্যাক্স মুলার ভারতের হিন্দুদেরকে আর্য বলে তাদের মাঝে সেনদের সেই পুরাতন মানসিকতা তুলে এনেছিলো। যার ফলে বহমান যে বাংলা ছিলো, সেটাকে সমূলে ধ্বংস করে সংস্কৃতকে জোর করে বাংলায় প্রবেশ করানো হয়েছে, যেনো মুসলিম শাসনামলের বাংলা এবং হিন্দুদের নতুন সংস্কৃত বাংলার মাঝে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়; আর শেষমেশ এ-নিয়েও যেনো হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এবং, হয়েছেও তাই-ই।
নতুন এই বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইংরেজরা নিজেরাই লিখেছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, যেসব ব্যাকরণের মাধ্যমেই নতুন বাংলার সূচনা করা হয়। কেননা, এসব ব্যাকরণে সংস্কৃতকে সামনে রেখেই বাংলার নতুন রূপ দেওয়া হয়। আর এসবকে পরিচিত করাতে কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজকে কাজে লাগিয়েছে ইংরেজরা; এবং নতুন এই বাংলাকে লেখ্য ভাষায় রূপ দিয়েছে কলকাতার সাহিত্যিকরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখাগুলো পড়লেই এসব বুঝা যায়। ঠিক এজন্যই কবি নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ এবং কবি গোলাম মোস্তফার চেয়েও এই জেন-জি প্রজন্ম রবী-শরৎ-বঙ্কিম-বিভূতিদেরকে ভালোভাবে চিনে।
এখানে এই প্রশ্নও উঠে আসে যে, ৫০০ বছর আগের মহাকবি আলাওল-এর বহমান বাংলাকে আমরা যেভাবে বুঝি না, তেমনি আমরা কেন প্রায় ২৫০ বছর আগের ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝি না? ভাষা যদি বহমান হয়, তাহলে আলাওলেরও ২৫০ বছর পরের বাংলা-তো অনেকটাই বুঝতে পারার কথা। কিন্তু, তা কেন হয় না?
মূলত, এসব কারণেই ভাষা-সাহিত্যের বিষয়টিও এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।
ছয়.
এবার সর্বশেষে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করা যাক।
মুসলিম বিজয়ের আগে ভারতবর্ষের সমাজে নারীদের অবস্থা ছিলো বড়ই করুণ। নারীদের অধিকার ছিলো খুবই সীমিত। নারীদের সাধারণত ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সমাজে পুরুষেরা বহু বিবাহ করতো। কিন্তু, নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের কোনো নিয়ম ছিলো না। বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে নারীর অপমানের বিষয়টি উঠে আসে সতীদাহ প্রথা থেকে। নারীরা সে সমাজে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সমাজে তাদের কোনো মর্যাদাই ছিলো না।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলিম বিজয়ের আগে ভারতীয় সমাজে অনেক কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো। অনেক কু-প্রথাকে সমাজে ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হতো। কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা, নরবলি এবং গঙ্গীয় শিশু কন্যা বিসর্জন ইত্যাদি কাজকে হিন্দুরা ধর্মীয় পুণ্যের কাজ বলে মনে করতো। এমনকি, ধর্মের দোহাই দিয়ে শাসকরা পর্যন্ত নারীদের রক্ষা করতে আসতো না। এছাড়াও তখন দেবদাসী প্রথাও প্রচলিত ছিলো।
বিপরীতে মুসলিম শাসনে নারীরা পূর্বের সকল ধরনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর্থিক সঙ্গতি, উচ্চশ্রেণির লোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বিবাহের ফলে সমাজে মুসলমান মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের ন্যায় অতটা অসহায় ও পুরুষের উপর নির্ভরশীলা ছিলো না।
শুরুতেই সতীদাহ প্রথা নিয়ে বলতে গেলে ইবনে বতুতার মুহম্মাদ বিন তুঘলককে নিয়ে একটা মন্তব্য তুলে ধরতে হয়, তিনি বলেন, ❝সুলতান সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ সাধনে সর্বদা ছিলেন তৎপর।❞
শুধু মুহাম্মাদ বিন তুঘলকই না, বরং সম্রাট বাবর, আকবর এবং আওরঙ্গজেবও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তকরণে ভূমিকা পালন করেন। সম্রাট আকবর একবার নিজে গিয়ে এমন হিংস্র কর্মকাণ্ডে বাধা দেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তকরণে আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করেন।
অতএব, সতীদাহ প্রথা নিয়ে মাত্র তিনশ বছর আগে নয়, বরং তারও পাঁচশ বছর পূর্বে মুসলিম শাসকরাই সর্বপ্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। সেহেতু, সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তকরণে রাজা রামমোহন রায় যেভাবে ইতিহাসে মর্যাদাবান হয়ে আছেন, সেটা আদতে মুসলিম শাসকদের অবদান ভুলিয়ে দেবার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ইংরেজদের উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড কি-না, তা গভীরভাবে যাচাই করা দরকার।
মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের ব্যাপারে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে এবং স্বীকারও করে। যাতে করে বালিকারা তাদের ধর্মের মূলনীতি, কোরআন পাঠ ও ধর্মের ক্রিয়া-কর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সেজন্যে পিতারা তাদের কন্যাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। বালিকাদেরও বালকদের মতো ‘সিমিল্লাহখানি’ অনুষ্ঠান দ্বারা অক্ষর-পরিচয় শুরু হতো এবং তারা একই মক্তবে বালকদের সঙ্গে একত্রে পড়াশোনা করতো।
গদাই মল্লিকের পুথি বা ‘মল্লিকার হাজার সওয়াল’ (মল্লিকার হাজার প্রশ্ন) নামে অভিহিত কাব্য থেকে জানা যায় যে, মল্লিকা নাম্নী মুসলমান বালিকা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, যে পুরুষ তাকে সাহিত্য-বিষয়ক বিতর্কে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই বিয়ে করবেন। বহু রাজপুত্র ও বিদ্বান ব্যক্তি তার সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন, কিন্তু সকলেই মল্লিকার নিকট পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে জনৈক সুফি পণ্ডিত আবদুল হাকিম গদা তার হাজার প্রশ্নের উত্তরদান করে তাকে বিতর্কে পরাজিত করেন। অতঃপর মল্লিকা তাঁর বিজয়ীকে বিয়ে করেন।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমান রমণীগণ যুদ্ধক্ষেত্রেও স্বামীদের সহগমন করেছেন। এই উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাসে মুসলমান রমণীদের এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কার্যক্রম মোটেই বিরল কিছু ছিলো না। বাংলার মুসলমান শাসনামলে বহু রমণী ছিলেন যারা তাদের সাহস, শক্তি ও বীরত্বের জন্যে খ্যাতি লাভ করেন।
নবাব অলীবর্দী খানের বেগম শরফুন্নেসা ছিলেন একজন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্না ও গুণান্বিতা মহিলা। তিনি তার গুণের মহিমায় সে যুগের রাজনৈতিক ও সমাজিক জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন। তিনি স্বামীর যুদ্ধাভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোরতা ভোগ করেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি তার স্বামীর একজন মূল্যবান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি সর্বদা একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী ও বন্ধুরূপে নবাবকে সাহায্য করেন। আলিবর্দী স্বয়ং বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন; তবুও স্ত্রীর উপদেশের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিলো। সঙ্কটের সময়ে শরফুন্নেসা ছিলেন স্বামীর জন্যে আশা ও উৎসাহের উৎস স্বরূপ। মারাঠারা কয়েক বছর আলিবর্দীর মহাবিপদ ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো। এমন সময় তিনি তার স্বামীর পাশে থেকে তাকে সাহস জুগিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। বাস্তবিকই নবাব আলিবর্দী খানের প্রশাসনের উপর শরফুন্নেসার গভীর প্রভাব ছিলো। গোলাম হোসেন নবাবের আত্মীয় ছিলেন; তিনি লিখেছেন, “নবাব আলিবর্দী খান তার স্ত্রীর উপদেশের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।”
নবাব আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা ও সিরাজদ্দৌলাহর মাতা আমিনা বেগম তার সুরুচি ও শিষ্টাচারের গুণে সে যুগের সমাজজীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়া মহিলা এবং অনাথ ও গরিব-দুঃখীদের আশ্রয়স্থল। এটা উল্লেখযোগ্য যে, তিনি রাজকানয়ার নাম্নী ক্রীতদাসীকে শিক্ষিতা করে তোলেন এবং পরে তাকে লুৎফুন্নেসা নাম দিয়ে স্বীয় পুত্র সিরাজের সঙ্গে বিয়ে দেন। আমিনা বেগম ও জৈনুদ্দিন ‘মুহম্মদী বেগ’ নামক এক গরিব বালককে লালন-পালন করেন এবং সে বড় হয়ে উঠলে তারা বিয়ের বন্দোবস্ত করেন শরফুন্নেসার প্রাসাদে লালিতা-পালিতা এক মেয়ের সঙ্গে। এভাবে তিনি তার ভবিষ্যৎ পুত্র হন্তা মুহম্মদী বেগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।
কোমল হৃদয়া আমিনা বেগম অন্যায়কারীর প্রতিও কোনোরূপ কঠোরতা সহ্য করতে পারতেন না। ইংরেজদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সিরাজদ্দৌলাহ্ আলিবর্দীর পীড়িত অবস্থায় প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশুনা করেন। সে সময় তিনি রাজস্বের হিসাবে বহু অনিয়ম এবং জাহাঙ্গীরনগরে ঘষেটি বেগমের দিউয়ান রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক বিপুল অর্থ আত্মসাতের তথ্য আবিষ্কার করেন। রাজা রাজবল্লভ সঠিক হিসাব না দেওয়ায় এবং তসরূপকৃত অর্থ রাজকোষে প্রত্যর্পণ না করায়, সিরাজদ্দৌলাহ্ তাকে মুর্শিদাবাদে কঠোর পাহারায় আবদ্ধ করে রাখেন। আমিনা বেগম পুত্রের নিকট তার পক্ষে মধ্যস্থতা করেন। মায়ের আদেশ রক্ষার্থে সিরাজদ্দৌলাহ্ রাজবল্লভকে মুক্ত করে দেন।
সিরাজদ্দৌলাহর সহধর্মিণী লুৎফুন্নেসা ছিলেন রমণীদের আদর্শ। কিভাবে সামান্য মর্যাদার একজন নারী স্বীয় গুণাবলীর বলে মুসলমান সমাজে খুব সম্মানিত মর্যাদায় আরোহণ করতে পারেন, তা তার জীবনে প্রতিভাত হয়েছে। সামান্য পরিচারিকার অবস্থা থেকে লুৎফুন্নেসা একজন যুবরাজের সহধর্মিণী এবং নবাবের বেগমের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়া ও উচ্চ অন্তঃকরণ সম্পন্না মহিলা।
এছাড়াও, দারাশিকোর কন্যা ও যুবরাজ মুহম্মদ আজমের স্ত্রী জাহানজেব বানু বেগম মরাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। গউস খানের বিধবা স্ত্রী একদল মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভাগলপুরে তার গৃহ রক্ষা করেন। আহমদনগরের চাঁদসুলতানার বীরত্বগাঁথা সুবিদিত। মহব্বত খাঁর বিরুদ্ধে নূরজাহানের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ইতিহাসের একটি সুপরিচিত ঘটনা। এর বাইরে মহিলারা বিবাহ অনুষ্ঠানাদি ও শোভাযাত্রায়ও যেতেন।
এ-সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, মুসলমান নারীরা গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তারা গৃহের বাইরেও যেতে পারতেন। কিন্তু তাদের পর্দা পালন করতে হতো এবং গৃহের বাইরে চলতে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করতে হতো। পর্দান্তরালে বসবাস করলেও মুসলমান রমণীরা সমাজে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। মুগল সমাজের রমণীগণ, তাদের পূর্ববর্তী ভগ্নীদের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন।
নারীদের জন্য পর্দা, বা আবরু প্রথা সমাজে আভিজাত্য ও সামাজিক শালীনতা বলে গণ্য করা হতো। সে যুগের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নারীদের মুখে ও মাথায় আবরণহীন অবস্থায় বের হওয়া অসম্মানজনক বিবেচনা করতো। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় পর্যটক বারবোসা বাঙ্গালা শহরে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে বলেন যে, উচ্চশ্রেনির লোকেরা তাদের নারীদেরকে অন্দরমহলে থাকতে বলতো। মেয়েদের উল্লেখ করে তিনি আরো লিখেছেন যে, তারা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিতা এবং স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড় এবং হিরা বসানো স্বর্ণ অলংকারে ভূষিতা। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ লেখক ভেরেলস্ট লিখেছেন, নারীদেরকে অবরোধ অবস্থায় রাখা এরূপ একটি আইন, যা’ অপরিবর্তনীয়। সমগ্র ভারতব্যাপী এই রীতি প্রচলিত ছিল এবং এটা লোকদের ধর্ম ও শিষ্টাচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলো। স্ত্রীর বে-আবরু হওয়া হিন্দু-মুসলমান উভয়ের চোখেই অমর্যাদাজনক ছিলো।
নারীদের পর্দা সম্বন্ধে ইউরোপীয় লেখকদের এসব বর্ণনা থেকে এই ধারণা হয় যে, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের রমণীরা গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলো- এই অভিমত প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। বারবোসা একদিকে মুসলমান রমণীদের অবরোধের কথা বলেছেন, আবার তিনি তাদের সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। মুসলমান মহিলারা যদি সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ থাকতেন, তাহলে কিভাবে এই সমস্ত বিদেশীরা তাদেরকে দেখতে পান এবং তাদের সৌন্দর্য ও পোশাক-আশাকের বিষয় জানতে পারেন!?
মুসলমান আমলে হিন্দুসমাজেও কিছুসংখ্যক প্রতিভাময়ী-রমণীর জন্ম হয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের নায়িকা বিদ্যার ঘটনা থেকে জানা যায় যে, উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। এরা সাহিত্য বিষয়ে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। নাটোরের জমিদার পরিবারের রানি ভবানী একজন খ্যাতনামা মহিলা ছিলেন। জমিদারি শাসনে তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা এবং জনসাধারণের হিতার্থে তার বদান্যতার জন্য তিনি সে যুগের সমাজে উচ্চ আসন লাভ করেন। জনৈকা স্ত্রী জমিদার জয়দুর্গা চৌধুরাণী রংপুরের একজন অত্যাচারী জমিদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন। অন্য একজন উল্লেখযোগ্য রমণী দেবী চৌধুরাণী ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে অধিবাসীদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।
মূলত, মুসলিম বাংলায় এভাবেই নারীগণ তাদের শিক্ষা, সাহিত্য চর্চা, পৈত্রিক সম্পত্তি ও রাজনীতির অধিকার পেয়েছিলো। অতএব, উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমান শাসনযুগে বাংলার রমণীরা হারেমে সাধারণ পর্দা প্রথার মধ্যে থেকেও এবং পুরুষদের উপর নির্ভরশীল থাকা সত্ত্বেও তারা এই প্রদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে হিসেবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলে মোটেও ভুল হবে না যে, বর্তমান সমাজ শুধু পর্দার কথা বলে এটা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, মুসলিম বাংলায় নারীরা ছিলো চার দেয়ালে আবদ্ধ, যা সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি ইতিহাস।
সাত.
সার্বিক আলোচনার পর এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার পুরো ইতিহাসে একমাত্র মুসলিম শাসনামল বা ইসলামী সভ্যতাই বাংলা অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর অনন্য উপমা পেশ করেছিলো। ধর্ম, সংস্কৃতি, নারী, শিক্ষা, রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা-সহ সমাজ নামক বিষয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি বিষয়েই ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ নিশ্চিত করেছিলো।
তবে এখানে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। সেটি হলো, ইসলামী সভ্যতা হচ্ছে সামগ্রিক, সেজন্য ইসলামী সমাজ বিনির্মাণও হয় সামগ্রিক। কখনও এভাবে দু’টি, তিনটি বা চারটি ধর্মের জন্য কাজ করে না ইসলামী সভ্যতা। বরং, সমাজের সকলকে একসাথে নিয়ে আদালত ও মারহামাতপূর্ণ একটি সমাজ গড়ে তোলা হয় ইসলামী সভ্যতায়। অতএব, বাংলা অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে মুসলিম বাংলায় শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বলে আলাদা কোনোকিছু ছিলো না। কেননা, এখানে হিন্দুদের পাশাপাশি বৌদ্ধদেরও বড় একটা অংশ বসবাস করতো। এমনকি, এই বৌদ্ধ জনসাধারণই মুসলিমদেরকে ভারত অভিযানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো।
আবার, হিন্দু-মুসলিম সামাজিক সহাবস্থান বজায় রাখা বা রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি সেক্টরে হিন্দু-মুসলিম একত্রে কাজ করাটাই শুধু সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের উদাহরণ নয়, বরং মুসলিম সমাজের মাঝেও যদি অভ্যন্তরীণ কোন্দল লেগে থাকে, সে সমাজকেও সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দে পরিপূর্ণ একটা সমাজ বলা যায় না। অতএব, এখানে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান বলে আদতে কিছুই নেই। যা আছে তা হলো, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষকে নিয়ে আদালত, আখলাক ও মারহামাতপূর্ণ একটি সমাজ বিনির্মাণ করা; যা ইসলামী সভ্যতা সুদীর্ঘকালব্যাপী সমগ্র বাংলা অঞ্চলে প্রমাণ করে দেখিয়ে এসেছে।
তাহলে উপরের আলোচনা থেকে এটাই বুঝা গেলো যে, “ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ” পরিভাষাটা হয়তো নতুন করে আমাদের সামনে এসেছে, কিন্তু, এমন পরিভাষাটা মুসলিম বাংলায় পরিভাষা হিসেবে না থাকলেও এমন ধারণাটা ঠিকই বিদ্যমান ছিলো এবং তা থেকে ভালোভাবেই সকল জনগণ উপকৃত হতে পারতো।
মূলত, ইতিহাস থেকে তখনই উপকৃত হওয়া সম্ভব, যখন সে ইতিহাসটি সঠিক ধারার হয়ে থাকে, যে ইতিহাস নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখে এবং সে জাতির আত্মপরিচয়কে সামনে এনে জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করতে পারে।
অতএব, আমাদের বাংলাদেশ ২.০-এ তখনই ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে, যখন অতীত ইতিহাস থেকে এই ধারার সবটুকু জেনে নিয়ে পূর্বের ভুলগুলোকে পর্যালোচনা করবো এবং বর্তমানকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবো। তবেই তাহলে আমরা সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দে পরিপূর্ণ একটি বাংলাদেশ পাবো এবং পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীন ভারতের যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিলো, আর কোথাও থেকে হোক বা না হোক, যে বাংলার ভূমি থেকেই স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিলো, সেই বাংলার উর্বর জমিন থেকেই আবারো স্বাধীন ভারতের সূর্যোদয় হবে, ইনশাআল্লাহ।
হাওলা:
০১. বাংলার ইতিহাস – আবদুল করিম
০২. বাংলার ইতিহাস – মাহবুবুর রহমান
০৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস – আব্বাস আলী খান
০৪. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস – ড. এম. এ. রহিম
০৫. বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস – মাহবুবুর রহমান
০৬. বাংলা অঞ্চলে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস; মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা – হাসান আল ফিরদাউস (ত্রৈমাসিক মিহওয়ার, চতুর্থ সংখ্যা)
০৭ জ্ঞান ও সভ্যতার পুনর্জাগরণে মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ভাষা ‘বাংলা’ – হাসান আল ফিরদাউস (ত্রৈমাসিক মিহওয়ার, পঞ্চম সংখ্যা)
০৮. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতা: সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের অনন্য উপমা – মিফতাহুল জান্নাত (ষাণ্মাসিক শিউলিমালা, চতুর্থ সংখ্যা)
০৯. ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস – ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক
১০. আলিম ইসলামের ইতিহাস – আলিম শ্রেণি – লেকচার পাবলিকেশন্স
১১. মুসলিম শাসনে ন্যায়বিচার – তোফাজ্জল বিন আমীন