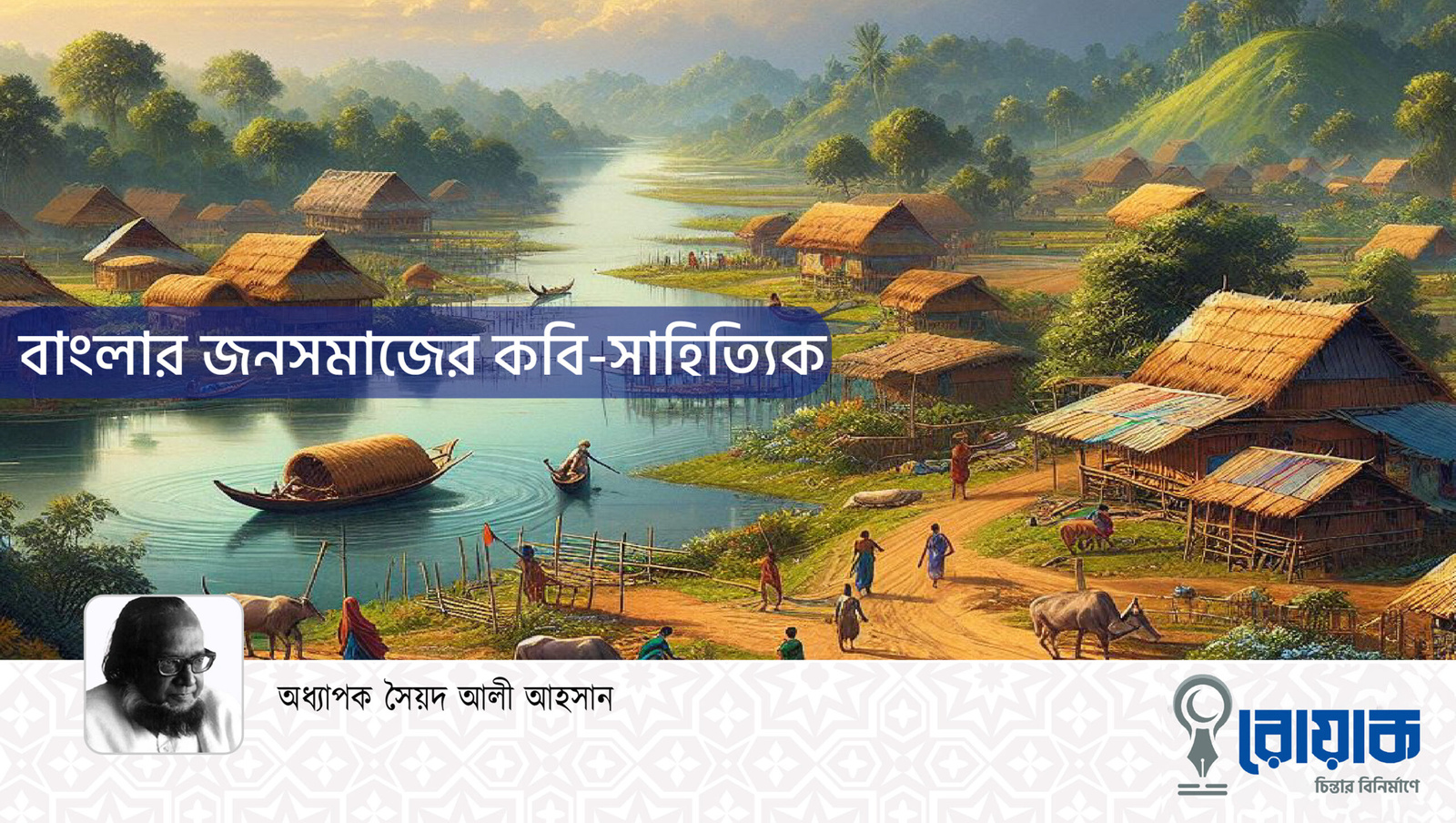ব্রিটিশদের অনুসৃত ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতির ফলে এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়, সেটার অন্যতম প্রয়োগক্ষেত্র দেখা যেত সাহিত্যে। বিশেষ করে, খ্যাতিমান হিন্দু লেখকদের সাহিত্যকর্মে সেটার সর্বাধিক বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। প্রথম প্রথম বাঙালী মুসলমান খ্যাতিমান হিন্দু লেখকদের কাছে বাংলার বৃহৎ জনসমষ্টির অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাবী করেছিলেন, তাঁরা চেয়েছিলেন যেন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র মুসলমানদের জীবন কথা নিয়ে উপন্যাস বা গল্প লেখেন। যেখানে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান এবং এ দেশের মানুষের প্রধান জীবিকা যে কৃষি এ কর্মকাণ্ডের অধিকাংশ লোকগুলোও মুসলমান, সুতরাং এসব মানুষের কথা সাহিত্যে কেন থাকবে না এ-প্রশ্ন মুসলমানদের ছিল। এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন একটি কবিতায়। যেখানে তিনি বলেছিলেন, “তোমার এবং আমার মধ্যে কাঁটার বেড়া ঘন হয়ে ওঠেছে এবং তা হয়েছে সহসা রাতারাতি। এ বেড়াকে স্বদেশের অশ্রুজলে আরো কি দুর্ভেদ্য করে তুলবো? এই যে সর্বনাশটি ঘটেছে তাকে আমরা ধর্মের নামে মহার্ঘ করে তুলেছি এবং আঙিনা ভাগ করে তার দু’দিকে আমরা বসবাস করতে চাচ্ছি শয়তানকে পূজা করে।” শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন ‘অবাঞ্ছিত ব্যবধান’ নামে একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিলো অধুনায় বিলুপ্ত হওয়া ‘বুলবুল’ পত্রিকায়। শরৎচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, “এটা অত্যন্ত বেদনার যে আমরা হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে সামাজিক এবং ধর্মীয়বোধের দিক থেকে চিনি না। মানুষ হিসাবে কখনও কখনও চিনবার চেষ্টা করলেও সমাজের এবং ধর্মের বিবিধ ব্যবধান মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর কাছে আমরা নত স্বীকার করি। এ দুর্ভাগ্য আমাদের সকলের। এ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সৌন্দর্য্যে, আনন্দে, সৌভাগ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদনা ও দুঃসহতায়/দুর্ভরতায় একে অন্যের অংশীদার হওয়া। সেটা হচ্ছেনা কেননা আমরা একে অন্যকে জানতে চাচ্ছি না।” এ দুজন মহৎ ব্যক্তির কাছে ব্যবধানের স্বীকারোক্তি আমরা পেয়েছি এবং তৎকালীন ক্ষোভ এবং অবিশ্বাসের একটা ইঙ্গিতও তাদের উক্তিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর ‘কালান্তর’ নামক গ্রন্থে হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় সামাজিক এবং রাষ্ট্রগত ইচ্ছার মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান এবং দ্বিমুখী তৎপরতা রয়েছে সেসব কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলন যখন হলো তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি ভিন্নতর সাহিত্য নির্মাণের আকাঙ্খার কথা মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকরা ব্যক্ত করেছিলেন। সত্যিই যখন দেশ বিভক্ত হলো ১৯৪৭ সালে তখন কলকাতা ছেড়ে আমরা যারা চলে এলাম যেমন জসীম উদ্দিন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন এবং সৈয়দ আলী আহসান। তাঁরা চেষ্টা করলেন নতুন স্বাধীনতার পটভূমিতে স্বচ্ছন্দে নতুন উপকরণ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করার। এটা সম্ভব হলো কি হলো না সেটা পরের কথা কিন্তু দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে একটি ভিন্নতর ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য নির্মাণের লৌকিক কর্মকান্ড শুরু হলো। ‘বাংলাদেশের কবিতা’র আলোচনা এখান থেকেই শুরু করতে হবে।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর-ই যে ভাবধারাকে কাব্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সচল এবং প্রবল দেখতে পেলাম তা হচ্ছে– ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসকে স্মরণ করে সৃষ্ট একটি আনন্দময় রোমান্টিক ভাবধারা। এ ভাবধারার প্রধান কবিরূপে যিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন, তিনি ফররুখ আহমদ। এ ছাড়া কবিতাকে শিল্প হিসেবে পরীক্ষা করে অনেকে কাব্য চর্চায় অগ্রসর হয়েছেন। আবার কেউ কেউ পল্লী জীবনের আবহ শব্দে উচ্চকিত করতে চেয়েছেন। অনেকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসকে কবিতার উপজীব্য করেছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশের কবিতা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে। চিন্তা, জ্ঞান, ইতিহাস এবং ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই তা প্রসারিত হয়েছে।
ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪):
ধর্মীয় বিশ্বাসকে কবিতার আবেগে রূপান্তরিত করে একটি সার্থক কাব্যকলা নির্মাণ ফররুখ আহমদের একটি অনন্য-সাধারণ বিশিষ্টতা। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিতে মৌল ধর্মতত্ত্ব, সূফীবাদের ত্যাগ ও বিনয় এবং একইসাথে ইসলামের ইতিহাসের গতিশীলতার প্রতি সমর্থন ছিলো। তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান একটি কাব্য-শরীর নির্মাণ করেছিলেন যেখানে তিনি একক নায়ক ছিলেন। বাংলা কবিতার প্রবৃত্তির মধ্যে নতুন একটি মাত্রা তিনি সংযোজন করেছিলেন। ধর্ম-বিশ্বাস ফররুখের কাছে কোনো উপাদান অথবা কোনো উপকরণ ছিলো না, বরং সেটা ছিলো তাঁর অকৃত্রিম উপলব্ধি। যার ফলে তিনি তাঁর কাব্যভাষায় একটি নতুন স্বাদ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিরিশের দশকের কবিকুল যারা বাংলা কাব্যে নতুন বাণীভঙ্গি প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের প্রতাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ফররুখ আহমদ নতুন একটি কণ্ঠস্বর আমাদের শুনালেন। ফররুখ আহমদের সঙ্গে সঙ্গে যে কজন তরুণ মুসলমান কাব্যশিল্পী বাংলা কবিতার প্রাঙ্গণে নতুন পদক্ষেপ রেখেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস এবং সৈয়দ আলী আহসান। পরিচয়ের বৃত্তে যূথবদ্ধ হয়েও এঁরা প্রত্যেকেই কাব্যকর্মে স্বতন্ত্র ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে বাংলা কবিতায় নতুন বিশ্বাস এবং অভিপ্রায়কে প্রকাশমান করেছিলেন। ফররুখ আহমদ বিশেষ করে বাংলা কবিতার জন্য একটি নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন। সে ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদ নাবিককে পাই এবং একইসাথে হাতেম ও নৌফেলকে পাই। একদিকে আরব্য উপন্যাস এবং পুঁথির জগৎ থেকে ঐতিহ্য তিনি আহরণ করেছেন; আবার অন্যদিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের কর্মকাণ্ড থেকে জীবনের উপলব্ধির সন্ধান করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সাতসাগরের মাঝি’ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এ কাব্যগ্রন্থে সিন্দাবাদ নাবিক প্রেরণা-পুরুষ। এখানে আমরা সত্যের সন্ধানে দুর্গম পথে সমুদ্র যাত্রার উৎসাহকে রূপ পেতে দেখি। এই কাব্যগ্রন্থে কবির উদ্দেশ্য জড়তামুক্ত একটা নতুন জীবনকে আবিষ্কার করা। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে নতুনভাবে আবিষ্কারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রাসূলে খোদা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলকে উপলক্ষ্য করে এ কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ‘সিরাজুম মুনীরা’ ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। ‘সিরাজুম মুনীরায়’ ‘সাত সাগরের মাঝির’ ধ্বনিগত অনুবর্তন প্রকাশ পেয়েছে। ‘নৌফেল ও হাতেম’; একটি নাট্য কাব্য। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। ‘মুহূর্তের কবিতা’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এ কাব্যগ্রন্থটি সনেট রচনায় কবির দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। অতুলনীয় প্রসাদ গুণ, ভাব সংযম এবং ছন্দের নিটোল বাঁধুনিতে এ কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলি অসাধারণ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনী কাব্য ‘হাতেম তায়ী’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। এটি একটি দোভাষী পুঁথির পূনর্নিমাণ। অজস্র সম্পদ এবং সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কারণবশত সওদাগরজাদী হুসনাবানু প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সাতটি সওয়াল করবেন। যে ব্যক্তি এই সাতটি সওয়ালের জবাব এনে দিতে পারবে তাঁকেই তিনি বিবাহ করবেন। খরজমের শাহাজাদা মুনীর শামী একজন চিত্রশিল্পীর কাছে হুসনাবানুর তসবির দেখে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু পহেলা সওয়ালের জবাব দিতে না পেরে তিনি তখন সংসার ছেড়ে অরণ্যে প্রস্থান করেন। মহাপ্রাণ হাতেম তা’য়ীর সঙ্গে সেখানেই মুনীর শামীর পরিচয় ঘটে। মুনীর শামীর দূরবস্থা দেখে হাতেম তায়ী হুসনাবানুর সওয়ালের জবাব এনে দেন এবং অবশেষে মুনীর শামীর সঙ্গে হুসনাবানুর পরিণয়ের ব্যবস্থা করেন। কাহিনীটির মধ্যে রহস্য, রোমান্টিকতা এবং বিচিত্র ঘটনাবর্ত আছে। ফররুখ আহমদ অপূর্ব কুশলতায় এ কাহিনীটি পুনর্নির্মাণ করেছেন, দীর্ঘ পরিসরের এই কাহিনীকাব্যে ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের একটি সরল প্রবাহ পাঠককে মুগ্ধ করে। ‘হে বন্য স্বপ্নেরা’ ফররুখ আহমদের কবি জীবনের প্রথম দিকের ৪৯ টি কবিতার সংকলন। এই গ্রন্থটি ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।
ফররুখ আহমদ জীবিতকালেই এ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন কিন্তু প্রকাশ করে যেতে পারেননি। ১৯৩৬ সালের দিকে যে সমস্ত কবিতা ফররুখ আহমদ লিখেছিলেন সেগুলোর অনেকগুলো এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলো নিঃসর্গ বিষয়ক, প্রেম বিষয়ক এবং বাস্তব জীবনভিত্তিক। তিনি যে প্রকৃতিকে শান্তির মধ্যে এবং দুর্যোগের মধ্যে দেখেছেন সে প্রকৃতির চিত্র তিনি অনেকগুলো কবিতায় এঁকেছেন। এসব বর্ণনার মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু উচ্ছ্বাসটি অনেকটা সংযত। প্রেমের কবিতাগুলো আবেগবহুল। তবে সে আবেগের মধ্যে কবির সংঘাতক্লিষ্ট জীবনের ইঙ্গিত আছে। বাস্তব ভিত্তিক কবিতাগুলো বাস্তবের রূঢ়তা, সংঘাত এবং সংশয়কে ফুটিয়ে তুলেছে। এগুলোর মধ্যে ‘কাঁচড়া পাড়ায় রাত্রি’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরেকটি কবিতা আছে ‘প্রেসম্যান’, এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর ‘কাফেলা’ নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের কবিতাগুলো ১৯৪৩-৪৪ সালে রচিত হয়েছিল। ফররুখের ‘সিরাজুম মুনিরা’ কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে ‘কাফেলা’ কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর মিল আছে। সুতরাং ‘সিরাজুম মুনিরা’ কে আমরা যে মানসিকতায় বিচার করব ‘কাফেলা’কেও সে মানসিকতায় বিচার করতে হবে। ফররুখের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থের নাম ‘পাখির বাসা’ (১৯৬৫), এবং ‘হরফের ছড়া’ (১৯৭০)। তাঁর এ দুটি গ্রন্থ শিশু কিশোরদের জন্য লেখা। ‘ছড়ার আসর’ বলে তার অন্য একটি কাব্যেও শিশু কিশোরদের জন্য লেখা। ‘ছড়ার আসর’ বলে তার অন্য একটি শিশু পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত কিছু পান্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে, যেমন, ‘হে বন্য স্বপ্নেরা’, ‘ফররখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা’।
আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৩):
আহসান হাবীবের জন্ম, শৈশবকাল এবং স্কুল জীবন কাটে বরিশালে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৩৮ এর দিকে কলকাতায়। সেখানে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসের কাজ করেছেন, সর্বশেষ কর্মব্যবস্থা ছিল ‘অল ইন্ডিয়া’ রেডিওতে। সৈয়দ আলী আহসান এবং তিনি একই সঙ্গে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে কাজ করতেন। সে সময় থেকেই আহসান হাবীব কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। যৌবনের মোহমুগ্ধতা, প্রেম, অভয় এবং সান্ত্বনা তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তখন বিকাশ লাভ করেছে। তাঁর ‘রাত্রিশেষ’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এটাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। শব্দ ও ছন্দের মোহময় গাঁথুনিতে এ গ্রন্থের কবিতাগুলো স্বাক্ষরিত। তখন থেকেই কবিতায় তিনি স্নিগ্ধতা এবং অলস অপরাহ্নের বিশ্রামের আনন্দ এনেছেন। তিনি সামাজিক কর্তব্যের কথাও কবিতায় বলেছেন এবং ধন-সম্পদ বন্টনের অসাম্যের কথাও কবিতায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যগুলো কোনো প্রকার যন্ত্রণা নিয়ে কাব্যে সমর্পিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বিষয় নির্বাচনে তিনি আধুনিক হলেও শব্দ ব্যবহারে এবং ছন্দের নির্ভাবনাময় প্রয়াসে তিনি রোমান্টিক। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম ‘ছায়া হরিণ’ (১৯৬২), ‘সারা দুপুর’ (১৯৬৪), ‘আশায় বসতি’ (১৯৭৪), ‘মেঘ বলে চৈত্রে যাবো’ (১৯৭৬), ‘দুই হাতে দুই আদিম পাথর’ (১৯৭১)। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাত্রিশেষে’ যে অন্তরালবর্তিতা, সংকোচ এবং বিনয় আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর সকল কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই একই বিনয় ও সংকোচ প্রবাহিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে মরমী কবি খলিল জিবরানের রহস্য মধুরতা আহসান হাবীবের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। যার ফলে তিনি আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন অনেক বেশী এবং নিজের জন্য নির্জনতা নির্মাণ করেছেন। ‘অরণ্য নীলিমা’ (১৯৬২) নামে তাঁর একটি উপন্যাস আছে। এটি একটি প্রণয় উপাখ্যান। এ গ্রন্থের ভাষা রোমান্টিক; অনেকটা কবিতার মতো। শিশু সাহিত্যেও আহসান হাবীবের বিশেষ অবদান আছে। শিশুদের লেখা তাঁর বইগুলোর নাম, ‘জ্যোৎস্না রাতের স্বপ্ন’, ‘রাণীখালের সাঁকো’, ‘ছুটির দিন দুপুরে’ এবং ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’।
সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫):
নানাবিধ কারণে সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। তিনিই একমাত্র কবি যিনি পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে কবিতায় ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর দুটি কবিতা এ কারণে খুব বিখ্যাত হয়ে আছে, একটির নাম ‘বাংলা ছাড়ো’, আরেকটির নাম ‘আমাদের সংগ্রাম চলবেই’। একটি আশ্চর্য তীব্র গতিবেগে তিনি তার ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যা তৎকালীন সময়ে তরুণদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। সিকান্দারের আরেকটি বিশেষ পরিচয় তিনি ‘সমকাল’ নামক একটি সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি আমাদের লেখকদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর কিছুর জন্য না হলেও শুধু ‘সমকাল’ প্রকাশের জন্য তিনি পরিচিত হয়ে থাকবেন।
সিকান্দর আবু জাফরের কবিতায় ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের উজ্জ্বল সাবলীলতা আছে। তিনি তাঁর বক্তব্যকে অনায়াস-নির্ভাবনায় প্রকাশ করেছেন। সঙ্গীত রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এক সময় ঢাকায় নাট্য আন্দোলনের একজন অগ্রণী কর্মী ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম- ‘প্রসন্ন প্রহর’ (১৯৬৫); ‘তিমিরান্তিক’ (১৯৬৫); ‘বৈরী বৃষ্টিতে’ (১৯৬৫); ‘বৃশ্চিক লগ্ন’ (১৯৭১);
কবিতা- ‘১৩৭২’ (১৯৬৮); ‘১৩৭৪’ (১৯৭১); ‘বাংলা ছাড়ো’ (১৯৭১) । দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতায় অবস্থান কালে সিকান্দার আবু জাফর কথাশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। সে সময়কার দু’টি উপন্যাসের নাম ‘পূরবী’ (১৯৪০); এবং ‘নতুন সকাল’ (১৯৪৩), সে সময়কার একটি গল্পগ্রন্থ আছে ‘মাটি আর অশ্রু’ নামে। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪১ সালে। তিনি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের বাংল অনুবাদ করেছিলেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।
আবুল হোসেন (জন্ম ১৯২১):
আবুল হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘নব বসন্ত’ ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। মুসলমান কবিদের মধ্যে আধুনিকতার সূত্রপাত যখন অর্থাৎ ১৯৩৯-এর দিকে তখন আবুল হোসেন কাব্য-বোধের ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। আধুনিক ইংরেজী কবিতার একটি বিশিষ্টতা অর্থাৎ সংলাপের ব্যবধানগত সহজতা আবুল হোসেন তাঁর সার্থক পরীক্ষা করেছিলেন। সম্প্রতি আবুল হোসেন আরও দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ‘বিরস সংলাপ’ এবং ‘হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস’ (১৯৮২)। সর্বশেষ গ্রন্থটিতে কবি তাঁর বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাংসারিক এবং একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বেদনার স্মারক হিসেবে উপস্থিত করেছেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ ‘দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে’ (১৯৮৭)। আবুল হোসেনের জন্ম খুলনার সৈয়দ মহল্লায়।
তালিম হোসেন (জন্ম ১৯১৮):
পাকিস্তান-পূর্ব যুগ থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির মুহূর্ত পর্যন্ত তালিম হোসেন ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহ নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। যেগুলো তৎকালীন মুসলমান পরিচালিত কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। এ সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে তালিম হোসেনের নিজস্ব কোন প্রকার সত্ত্বা প্রকাশ পায়নি। সে সময় কাব্যজগতে ফররুখ আহমদের একটি বলিষ্ঠ আবির্ভাব ঘটেছে। ফররুখ আহমদ ইসলামী ভাবাবহ নিয়ে কবিতা লিখলেও তাঁর কবিতায় শব্দ ব্যবহারের
একটি নৈপুণ্য ছিল এবং উপমা ব্যবহারের একটি নিজস্বতা ছিল। এর পাশাপাশি তালিম হোসেনের কবিতা অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হয়েছিলো। তাঁর ‘দিশারী’ কাব্যগ্রন্থ; যেটি ১৯৫৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, কবির প্রাক-পাকিস্তান যুগের কবিতাগুলোর সংকলন গ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থের সবক’টি ফররুখের ধাঁচে রচিত। তার ‘শাহীন’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এ কাবগ্রন্থের মধ্যেও ফররুখের প্রভাব অনুভব করা যায়। তালিম হোসেনের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ ‘নূহের জাহাজ’। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। এ কাব্যগ্রন্থেই আমরা প্রথম কবি তালিম হোসেনকে তার নিজস্ব অভিনিবেশে আবিষ্কার করি। এখানকার কবিতাগুলোতে কবির নিজস্ব কন্ঠস্বর শোনা যায়। কবির বিশ্বাসের মূল প্রবৃত্তি ‘নূহের জাহাজ’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এ কাব্যের প্রথম কবিতাটি বাংলাদেশের বন্যা এবং দৈব দুর্বিপাক নিয়ে। কবি বলছেন, সবকিছু অতলে গেছে কিন্তু এদেশের মানুষ ধ্বংসের রাশ টেনে চেষ্টা করে চলেছে, প্রলয়ের সিন্ধুর ওপারে ভিড়াতে জীবন্ত জয়ী নূহের জাহাজ।
সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯২):
চল্লিশের দশকে যে কয়জন কবি বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নতুন বক্তব্য এবং রসবোধ আনবার চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে সানাউল হক অন্যতম। তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং সৈয়দ আলী আহসানের কলেজ জীবনের সহপাঠী ছিলেন। কলেজ জীবন থেকেই তাঁর লেখা কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। প্রশাসনিক কর্মের দায়িত্বে থেকে তিনি তাঁর কাব্য সাধনায় কোনরূপ অলসতা প্রদর্শন করেননি। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি এবং মানবমনের কামনা ওতপ্রোতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কবিতায় তাঁর ব্যক্তিত্বকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। দেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা তাকে কখনো আনন্দিত, কখনো নিরানন্দ এবং কখনো ব্যঙ্গমুখর করেছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম – ‘নদী ও মানুষের কবিতা’ (১৯৫৬); ‘সূর্য অন্যতর’ (১৯৬৩); ‘সম্ভবা অনন্যা’ (১৯৬২); ‘বিচূর্ণ আরশীতে’ (১৯৬৮); ‘একটি ইচ্ছায় সহস্রপালে’ (১৯৭৩); ‘কাল সমকাল’ (১৯৭৫); ‘পঙ্ঘিনী শঙিনী’ (১৯৭৬); ‘প্রবাস যখন’ (১৯৮১); ‘বিরাশির কবিতা’ (১৯৮৩); ‘উত্তীর্ণ পঞ্চাশে’ (১৯৮৪)। তাঁর ‘বন্দর থেকে বন্দরে’ নামক অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ কাহিনী এক সময় খুবই খ্যাতি পেয়েছিলো।
সৈয়দ আলী আশরাফ (জন্ম ১৯২৪):
ইসলামী ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত ব্যক্তি হিসেবে সৈয়দ আলী আশরাফ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আদর্শ বিষয়ে তাঁর অনেক ইংরেজি গ্রন্থ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ‘বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য’ এবং ‘নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়’ নামক দুটি গবেষণা ধর্মীয় গ্রন্থ আছে। তাঁর কাব্য গ্রন্থ তিনটি। প্রথম গ্রন্থটির নাম ‘চৈত্র যখন’ দ্বিতীয়টির নাম ‘বিসংগতি’ এবং তৃতীয় গ্রন্থটির নাম ‘হিজরত’। প্রথম গ্রন্থে আলী আশরাফ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং এর অনুরূপ ‘মনোলোগ’ নির্মাণ করেন। এ কাব্য গ্রন্থে ইংরেজী কবিতার কলা কৌশলকে বাংলা কাব্যে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ‘হিজরত’ নামক কাব্যগ্রন্থ মক্কা এবং মদীনা তাঁর অবস্থানের অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। এ কাব্য গ্রন্থে আল্লাহ ও রাসুলের পথে সমগ্র সত্ত্বা বিলিয়ে দেবার একটি আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।
আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৫):
বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সংবাদপত্রের প্রশাসনের ক্ষেত্রে আবদুল গণি হাজারী বহুদিন পরিচিত থাকবেন। দীর্ঘকাল তিনি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর কবিতায় নগরজীবনের নানা অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। বলবার ভঙ্গীতে, সোচ্চার ব্যঙ্গ ও ভাষার সাংবাদিক সুলভ সারল্য সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় যে সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায় তা পাঠককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ তিনটি- ‘সামান্য ধন’ (১৯৫৯); ‘সূর্যের সিঁড়ি’ (১৯৬৫) এবং ‘জাগ্রত প্রদীপে’ (১৯৭০)। তাঁর কিছু অনুবাদ গ্রন্থও আছে। ‘কালো প্যাচার ডায়েরী’ (১৯৭৬) নামে তার একটি রম্য রচনা আছে। ‘কতিপয় আমলার স্ত্রী’ নামে একটি কবিতার জন্য তিনি ম্যানিলার পি.ই.এন ক্লাবের পুরস্কার পেয়েছিলেন।
আশরাফ সিদ্দিকী (জন্ম-১৯২৭):
লোক সাহিত্যের গবেষক হিসাবে আশরাফ সিদ্দিকী খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘বাংলাদেশের ফোকলোরের’ উপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি পেয়েছেন। ‘লোক সাহিত্য’ নামক একটি গবেষণা গ্রন্থ তিনি ১৯৬৪ সালে প্রকাশ করেন। লোক সাহিত্যের উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে এটি দীর্ঘদিন পরিচিত থাকবে। কবিতার ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত ‘তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা’ নামক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে তিনি প্রবেশ করেন। এরপর আরো অনেক কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন। যেমন- ‘সাতভাই চম্পা’ (১৯৫৫); ‘বিষকন্যা’ (১৯৫৫); ‘উত্তর আকাশের তারা’ (১৯৫৮); ‘তিরিশ বসন্তের ফুল’, ১ম ও ২য় খন্ড (১৯৭৫); ‘কুচবরণ কন্যা’ (১৯৭৭) ইত্যাদি। শিশুদের নিয়েও লেখা তাঁর অনেক গ্রন্থ আছে।
আবদুর রশিদ খান (জন্ম ১৯২৭):
সনেটের আঙ্গিকে ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালাটি নবরূপ দানের প্রচেষ্টার জন্য আবদুর রশিদ খানের ‘মহুয়া’ উল্লেখযোগ্য। আবদুর রশীদ খানের অন্য দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম- ‘নক্ষত্র মানুষ মন’ ও ‘বন্দী মুহূর্ত’।
আবদুস সাত্তার (জন্ম-১৯২৭):
লোক সাহিত্য এবং লোকজীবন নিয়ে নানাবিধ গবেষণা করে আবদুস সাত্তার খ্যাতি অর্জন করেছেন। লোকজীবনের উপর বিশেষ করে আদিবাসীদের জীবনের উপর তাঁর ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনেকগুলো গ্রন্থ আছে। এ সমস্ত গ্রন্থ তাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে।
আদিবাসী বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণা কর্ম হিসাবে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত ‘অরণ্য জনপদে’ গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কবি হিসাবে আবদুস সাত্তার সামাজিক, ধর্মীয় এবং গৃহগত পরিবেশের পটভূমিতে সহজ এবং হৃদয়গ্রাহী কবিতা লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘বৃষ্টি মুখর’ গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি হিসাবে আবদুস সাত্তার সামাজিক, ধর্মীয় এবং গৃহগত পরিবেশের পটভূমিতে সহজ এবং হৃদয়গ্রাহী কবিতা লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম- ‘বৃষ্টি মুখর’ (১৯৫৯); ‘অন্তরঙ্গ ধ্বনি’ (১৯৭০); ‘নামের মৌমাছি’ (১৯৭৩); ‘আমার ঘর নিজের বাড়ী’ (১৯৭৬); ‘আমার বনবাস’ (১৯৮২); ‘বিম্বিত স্বরূপ’ (১৯৮৫); ‘আমার বাবা মার কাসিদা’ (১৯৮৫); ‘আব্দুস সাত্তার ও অন্যান্য কবিতা’ (১৯৯০)।
শামসুর রাহমান (জন্ম ১৯২৯):
শামসুর রাহমান বিশেষভাবে নাগরিক কবি। ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’(১৩৬৬) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিরিশের কবিদের বিশেষত জীবননান্দ দাশের প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘রৌদ্র করোটিতে’ (১৯৬৩) কবির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। তাঁর কোনও কোনও কবিতার আবহ বাংলা কাব্যে নতুন। নগর জীবনের হতাশা ও অবয়বহীনতা তার কাব্যে শব্দে সমর্পিত। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম ‘বিধ্বস্ত নীলিমা’ (১৯৬৭); ‘নিরালেকে দিব্যরথ’ (১৯৭৫); ‘নিজবাসভূমি’; ‘বন্দী শিবির থেকে’ (১৯৭৩); ‘দুঃসময়ের মুখোমুখি’; ‘আমি অনাহারী’; ‘এক ধরনের অহঙ্কার’; ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে’; ‘মাতাল ঋত্বিক’ (১৯৮২); ‘উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’ (১৯৮২); ‘শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ইত্যাদি। তাঁর অনুবাদ কবিতাগ্রন্থ- রবার্ট ফ্রষ্টের কবিতা, খাজা ফরিদের কবিতা।
শামসুর রাহমানের শব্দ-ব্যবহার মধুর ও কোমল। তাঁর সকল কবিতার মধ্যে একই প্রকৃতির রূপাভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। শামসুর রাহমান তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই একটি নিরুপদ্রব নির্জনতা সন্ধান করেছেন।
হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩):
হাসান হাফিজুর রহমানের বিশিষ্ট কৃতিত্ব হলো- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সম্পাদনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের পক্ষ থেকে যে সমস্ত দলিল সংগৃহীত হয়েছিল সে সমস্ত বিপুল আয়তন দলিল সমূহ থেকে নির্বাচিত দলিলগুলো নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে এগুলো প্রকাশিত হয়, এক্ষেত্রে হাসান হাফিজুর রহমানের দান অনন্যসাধারণ।
বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যকলার ক্ষেত্রে হাসান হাফিজুর রহমান একটি প্রধান ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আধুনিক কবি এবং কবিতা বিষয়ে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে, যে গ্রন্থে তিনি আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করেছেন। আজীবন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁর কবিতায় সাংবাদিকতা সুলভ কোন প্রকাশভঙ্গি নেই। অত্যন্ত বলিষ্ঠ তার উচ্চারণ এবং নিজের বক্তব্যকে উদাত্ত কন্ঠে প্রকাশ করার ক্ষমতাও তিনি রাখতেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম-‘বিমুখ প্রান্তর’ (১৯৬৩); ‘আর্ত শব্দাবলী’ (১৯৬৮); ‘অন্তিম স্বরের মত’ (১৯৬৮); ‘যখন উদ্যত সঙ্গীন’ (১৯৭২); ‘বজ্রেচেরা আঁধার আমার’ (১৯৭৬); ‘শোকার্ত তরবারী’ (১৯৮২); ‘আমার ভেতরে বাঘ’ (১৯৮৩) এবং ‘ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী’ (১৯৮৩)।
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (জন্ম-১৯৩৪):
ছড়ার আঙ্গিকে কবিতা রচনা করে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করেন। এসব কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর একপ্রকার সফল নিরীক্ষা ছিল। ‘সাতনারীর হার’ (১৯৬৫) বইটি দিয়ে বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রবেশ। এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্যে অন্নদাশংকর রায়ের ছড়ার আমেজ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম ‘কখনো রঙ, কখনো সুর’ (১৯৭০); ‘কলমের চোখ’ (১৯৭৫); ‘আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি’ (১৯৮১); ‘সহিষ্ণু প্রতীক্ষা’ (১৯৮২); ‘বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা’ (১৯৮৩); ‘প্রেমের কবিতা’ (১৯৮২); ‘আমার সময়’ (১৯৮৭)।
সৈয়দ শামসুল হক (জন্ম ১৯৩৫):
বর্তমানে সৈয়দ শামসুল হক কথা সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সমধিক পরিচিত। কবিতা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন, বিশেষ করে গ্রামীণ শব্দ ও বাকভঙ্গি নিয়ে। গ্রামীণ ক্রিয়াপদও তিনি ব্যবহার করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে- ‘একদা এক রাজ্যে’ (১৯৬১); ‘বিশাল বিরতিহীন উৎসব’ (১৯৬৯); ‘বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা’ (১৯৭০); ‘প্রতিধ্বনিগণ’ (১৯৭৩); ‘অপর পুরুষ’ (১৯৭৮); ‘পরানের গহীন ভিতর’ (১৯৮০); ‘নিজস্ব বিষয়’ (১৮৮২); ‘রজ্জুপথে চলেছি’ (১৯৮৮); ‘বেজাল শহরের জন্য কোরান’ (১৯৮৯); ‘এক আশ্চর্য সঙ্গমের স্মৃতি’ (১৯৮৯); ‘অগ্নি ও জলের কবিতা’ (১৯৮৯); ‘কাননে কাননে তোমারি সন্ধানে’ (১৯৯০); ‘আমি জন্মগ্রহণ করিনি’ (১৯৯০); ‘তোরাপের ভাই’ (১৯৯০)। তাঁর কয়েকটি মঞ্চ সফল কাব্য নাট্য আছে। যেমন, ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ (১৯৭৬); ‘গণনায়ক’ (১৯৭৬); ‘নুরুলদীনের সারাজীবন’ (১৯৮২); ‘এখানে এখন’ (১৯৮৮)।
জাহানারা আরজু (জন্ম ১৯৩২):
দীর্ঘকাল কবিতা লিখে আসছেন এবং বর্তমানে তাঁর কবিতা একটি নিজস্ব ভঙ্গি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি, গৃহ-সংসার, সমাজিক, পারিবারিক সত্তা এবং বাংলা ভাষা ও শব্দের জগত এগুলোই হচ্ছে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। তাঁর মোট কবিতা গ্রন্থ সতেরটি। গ্রন্থগুলোর নাম- ‘নীল স্বপ্ন’ (১৯৬২); ‘রৌদ্র ঝরা গান’ (১৯৬৪); ‘শোণিতাক্ত আখর’ (১৯৭১); ‘আমার শব্দে আজন্ম আমি’ (১৯৮৩); ‘ক্রন্দসী আত্মজা’ (১৯৮৪); ‘বিমুক্ত পঙতি মালা’ (১৯৮৮); ‘তৃষ্ণার্ত পানির চুম্বন’ (১৯৯০); ‘সবুজ সবুজ অবুঝ মন’ (১৯৮০); ‘বাদল মেঘে মাদল বাজে’ (১৯৮৭); ‘ছড়ার নুপুর’ (১৯৮৮)। তিনি অনেকগুলো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে- একুশের রাষ্ট্রীয় পদক এবং কমর মুশতরী স্মৃতি পুরষ্কার। নারী জীবনের নির্যাতন এবং দুর্ঘটনা নিয়ে তিনি ‘শবমেহের তোমার জন্য’ নামে একটি কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতা অবলম্বনে ১৮৮৯ সালে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মিত হলে ব্যাপক নারী আন্দোলনে রূপ পায়।
আলাউদ্দিন আল আজাদ (জন্ম ১৯৩২):
আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলাভাষার অধ্যাপক হিসাবে সুপরিচিত। তিনি লন্ডন থেকে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের উপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি পেয়েছেন।
যদিও উপন্যাস এবং গল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি অধিক কিন্তু কবিতার রচনার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশিষ্টতা আছে যা অস্বীকার করা যায়। মুক্তগতি এবং দীর্ঘচরণ সম্বলিত কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর কবিতা গ্রন্থগুলোর নাম- ‘মানচিত্র’ (১৯৬১); ‘ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ’ (১৯৬২); ‘সূর্য জ্বালার সোপান’ (১৯৬৪); ‘লেলিহান পান্ডুলিপি’ (১৯৭৫); ‘নিখোঁজ সনেট গুচ্ছ’ (১৯৮৩); ‘আমি যখন আসব’ (১৯৮৪); ‘সাজঘর’ (১৯৯০); ‘ঝড় বৃষ্টি ও শস্যের কবিতা’ (১৯৯১); ‘আমার রুবাইয়াৎ’ (১৯৯১); ‘হরিৎ সনেটগুচ্ছ’ (১৯৯১); ‘গাঙচিল’ (১৯৯১); ‘সোনামতী বর্ণমালা’ (১৯৯১)। সমাজ সচেতন কবি হিসাবে আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর পাঠকদের কাছে সমর্থন পেয়েছেন।
মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ (জন্ম ১৯৩৬):
মোহাম্মদ মাফুজউল্লাহর প্রথম কাব্য ‘জুলেখার মন’ – গ্রন্থে পুঁথিসাহিত্যের উপমা ও বাক্যরীতির প্রয়োগ প্রচেষ্টা আছে। অন্যদিকে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অন্ধকারে একা’ সাংবাদিক-সুলভ বিচিত্র সমকালীন বিষয়নিষ্ঠ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ‘রক্তিম হৃদয়’ (১৯৭০) ও ‘আপন ভুবন’ (১৯৭৫)। ‘মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কাব্যসম্ভার’ প্রকাশিত হয়েছে।
ফজল শাহাবুদ্দীন (জন্ম ১৯৩৬):
দেহজ কামনা-বাসনার অনাবৃত প্রকাশ ও জীবনের নৈরাশ্য ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতার বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম- ‘তৃষ্ণার অগ্নিতে একা’ (১৯৫৫); ‘আকাঙিক্ষত অসুন্দর’ (১৯৭২); ‘আততায়ী সূর্যাস্ত’ এবং ‘অন্তরীক্ষে অরণ্য’। ফজল শাহাবুদ্দীন তাঁর যৌবনকালের শরীরী অস্তিত্বকে এখনও সুনিপুণভাবে ধরে রেখেছেন। শব্দ ব্যবহারের চাতুর্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করে আবেগের গতিপথে তিনি তাঁর কবিতার শব্দ এবং ছন্দকে নির্মাণ করেছেন। তার ‘নির্বাচিত কবিতা’ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।
আল মাহমুদ (জন্ম ১৯৩৬):
গ্রাম বাংলার সঙ্গে রয়েছে আল মাহমুদের নিবিড় আত্মীয়তা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘লোক লোকান্তর’- এ তার পরিচয় আছে। পরিশীলিত কাব্যগ্রন্থে আঞ্চলিক শব্দের সুচারু ব্যবহারের এ নিরীক্ষায় তিনি নিমগ্ন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য ‘কালের কলস’ এ (১৯৬৭) তার সাক্ষ্য বর্তমান। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম- ‘সোনালী কাবিন’ (১৯৭৩); ‘মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো’ বা ‘আল মাহমুদের কবিতা’; ‘প্রহরান্তের পাশ ফেরা’; ‘আরব্য রজনীর রাজহাঁস’।
আল মাহমুদ পল্লী-প্রকৃতি থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনের কর্ম ও উৎসব থেকে তাঁর কবিতার জন্য শব্দ সংগ্রহ করেছেন। এ শব্দগুলো তাদের সহজ সৌন্দর্য নিয়ে আল মাহমুদের কবিতায় নতুন বৈভবে আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন বিয়ের আসরে আসীন সুসজ্জিতা কন্যার চিত্তের উদ্বেলতাকে কবি ‘গাঙের ঢেউয়ের’ সঙ্গে তুলনা করেছেন।
আল মাহমুদ কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তার গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চারটি। এগুলো সবই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ এর মধ্যে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে ‘পানকৌড়ির রক্ত’। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। এ যাবত প্রকাশিত তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘পানকৌড়ির রক্তকেই’ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ জীবন, পরিবেশ এবং গ্রামীণ বিশ্লেষণ তাঁর গল্পগুলোর প্রতিটি শব্দে এবং বাক্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি জন্মবধি যে গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন তাকে কবিতায় যেভাবে রূপ দিয়েছেন গল্পেও সেভাবে রূপ দিয়েছেন।
আল মাহমুদ অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে উপন্যাস রচনাক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ কোনো অঙ্গীকার নেই। উপন্যাসের সংখ্যাও তাঁর কম নয়। প্রায় ৯ টির মত। কিন্তু উপন্যাসের সাহায্যে তিনি কথা সাহিত্যের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলেও তাঁকে সকলেই কবি হিসেবে গ্রহণ করবে। আল মাহমুদের কাব্য রচনার সময়কাল ৩০ থেকে ৩৫ বছর। এ সময়ের মধ্যে তিনি মোট ১১টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ‘লোক-লোকান্তর’ (বাংলা ১৩৭০ সাল); ‘কালের কলস’ (১৩৭৩ সালে); ‘সোনালী কাবিন’ (১৯৭৩); ‘মায়াবী পর্দা দুলে উঠো’ (১৯৭৬); ‘অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না’ (১৯৮০); ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ (১৯৮৫); ‘আরব্য রজনীর রাজহাঁস’ (১৯৮৭); ‘প্রহরান্তের পাশ ফেরা’ (১৯৮৮); ‘এক চক্ষু হরিণ’ (১৯৮৯); এবং ‘মিথ্যাবাদী রাখাল’ (১৯৯৩)। আল মাহমুদের কবিতা সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, “আল মাহমুদের কবিতার মধ্যে আছে গ্রামীণ জীবন ধারার নিরুপদ্রব সততার অহংকার এবং প্রাকৃত শব্দ সম্ভারের অসাধারণ অর্থময়তা। যে বিপুল প্রতীতীতে এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, আমাদের কাব্যক্ষেত্রের জন্য তা নতুন এবং একনিষ্ঠ সংযোজন। কবিতার শব্দ ব্যবহারের নিপুণতাই নয়, কিন্তু স্বতঃবেদ্য স্বাভাবিকতা এবং বিশ্বাসের অনুকূলতা নির্মাণে আল মাহমুদ নিঃসংশয়ে আধুনিক বাংলাভাষার একজন অগ্রগ্রামী কবি। বাংলাভাষার কাব্যকর্মে তাঁর প্রতিষ্ঠার একটি স্বতঃসিদ্ধতা এসেছে।”
মোহাম্মদ মনিররুজ্জামান (জন্ম ১৯৩৯):
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- ‘দুর্লভ দিন’ (১৯৬১), বুদ্ধির দীপ্তি ও আবেগের প্রাবল্যের দ্বারা চিহ্নিত। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ– ‘শঙ্কিত আলোকে’ (১৯৬৮)-এ সমাজ সচেতনতা ও তির্যক ব্যঙ্গ উপস্থিত। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ- ‘বিপন্ন বিষাদ’ (১৯৬৮)-এ আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা, সংক্ষোভ, হতাশা ও সম্ভাবনার বিচূর্ণ সমাহার। তাঁর কবিতায় একাডেমিক এবং বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা মেধা শাসিত ও মননসিদ্ধ। কিন্তু তাঁর কবিতায় আবেগ যে নেই একথা সত্য নয়। তাঁর অনেক কবিতায় গীতিময়তা লক্ষ্য করি। সমসাময়িক কালের হতাশা, ক্ষোভ, সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও প্রেরণা তাঁর কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। তিনি জীবনবাদী এবং বর্তমান সময়কে সর্বক্ষণ স্পর্শ করতে চান। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম- ‘প্রতনু প্রত্যাশা’ (১৯৭৩); ‘ভালবাসার হাতে’ (১৯৭৬); ‘ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার’ (১৯৮৪); ‘তৃতীয় তরঙ্গে’ (১৯৮৪); ‘কোলাহলের পর’ (১৯৯০); ‘ধীর প্রবাহে’ (১৯৯২); ‘অশান্ত অশোক’ (১৯৭৬); ‘সঙ্গী বিহঙ্গী’ (১৯৮৪)।
রফিক আজাদ (১৯৪৩):
বর্তমান সময়ে রফিক আজাদের কবিতা শব্দ ব্যবহারের একটি নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। কবির কাছে বর্তমান সময়টি একটি দুর্ভাগ্যের সময় এবং হতাশার সময়। এ দুর্ভাগ্য এবং হতাশা যেমন এদেশের সমাজ জীবনে, রাজনীতিতে এবং কর্মের প্রবঞ্চনায়, তেমনি এ কবিতাগুলো কবির ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য ও বেদনারও। শুধুমাত্র নৈরাশ্য ও বেদনা কখনোই ভালো কবিতা নির্মাণ করতে পারে না কিন্তু রফিক আজাদের কবিতার মধ্যে একটি সাহসী প্রতিবাদ আছে। তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা একটি নতুন প্রতিবাদের সুর দেখতে পাই। প্রতিবাদ অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং সামাজিক। কিন্তু তাহলেও তাঁর কবিতা কোনো বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তিনি নিজস্ব সত্তায় তাঁর সময়কালের বক্তব্যকে নিপুণ স্পষ্টতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। তিনি বর্তমান কালের ধ্বংস ও শান্তির পারস্পরিক অবলম্বনগত স্থিতিকে কবিতায় প্রতিপাদ্য করেছেন। রফিক আজাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থের নাম- ‘অসম্ভবের পায়ে’ (১৯৭৩); ‘সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে’ (১৯৭৪); ‘চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া’ (১৯৭৭); ‘সশস্ত্র সুন্দর’ (১৯৮২); ‘এক জীবনে’ (১৯৮৩); ‘হাতুড়ীর নীচে জীবন’ (১৯৮৪) এবং ‘পরিকীর্ণ পাঠশালা আমার স্বদেশ’ (১৯৮৫)। যদিও রফিক আজাদ ঢাকা শহরেই বসবাস করেন কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের মুগ্ধতা এবং সততার স্বাক্ষর আছে। নগর অতিক্রম করে তিনি বারবার গ্রামের বৃক্ষলতা পরিকীর্ণ জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেলবার চেষ্টা করেছেন।
আবদুল মান্নান সৈয়দ (জন্ম ১৯৪৩):
‘জন্মান্ধ কবিতা গুচ্ছ’ নামক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের আবির্ভাব। তখন সকলেই কেমন যেন আহতবোধ করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন অনেকেই, কবি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কঠিন ও কোমল শব্দের সমন্বয় করে কোন অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন? যখন গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কবি বয়সে তরুণ এবং জীবনের অভিজ্ঞতার পথে প্রথমেই পা বাড়িয়েছেন। তাই সকলে এ কবিতাগুলোকে যৌবনের বিক্ষুব্ধ চিত্রের প্রতিবাদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মান্নান সৈয়দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে ‘জ্যোস্না রৌদ্রের চিকিৎসায়’ আমরা নতুন ধরনের কিছু চিত্র রচনা পাচ্ছি। এসময়কার কবিতায় অনেক উপমা এবং শব্দ স্থাপনার প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দ দাশকে উপস্থিত দেখতে পাই। একজন কবির পক্ষে যথার্থ শব্দের সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন। এই অনুসন্ধান কর্মে আবদুল মান্নান সৈয়দ দীর্ঘকাল হলো ব্রতী রয়েছেন। তার ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে; ‘জোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা’ ১৯৬৯ সালে; ‘ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে; ‘পরাবাস্তব কবিতা’ ১৯৮২ সালে এবং ‘কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড’ ১৯৮২ সালে।
নির্মলেন্দু গুণ (জন্ম-১৯৪৬):
বাংলাদেশে বর্তমান সময়ের কবিদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণ রাজনৈতিক সংগ্রামের কবিতা লিখে থাকেন বলে সবাই বলে। তিনি মনুষ্য সমাজের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের যে কথা মার্কসবাদীরা দীর্ঘকাল ধরে বলে চলেছেন সেই শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী। এই শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি তাঁর কবি জীবনের নিত্যদিনের সংগ্রাম বলে মনে করেন। দুর্বলের প্রতি যে অত্যাচারের কথা তিনি বলেন সে অত্যাচার হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থে একটি দলের অকুশল। তিনি সে অকুশলের বিরোধিতা করতে চান এবং যে দলটি রাজনৈতিকভাবে নির্যাতিতদের পক্ষ নিচ্ছে বলে তিনি মনে করেন সেই দলটির সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতা। তাঁর রাজনৈতিক কবিতাগুলো ‘ইস্কা’ নামক কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। একসময় নির্মলেন্দু গুণ প্রেমের কবিতা লিখতেন। তাঁর ‘ও বন্ধু আমার’ গ্রন্থে তিনি প্রেমের একটি অমরাবতী নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
আবুল হাসান (১৯৪৭-৭৫):
আবুল হাসানের কবিতায় উত্তেজনা নেই, প্রবল প্রতিবাদ নেই কিন্তু অসহায় মানুষের শংকিত পদক্ষেপের যাত্রা আছে। একটি কবিতায় তিনি বলছেন, তাঁর সকল ‘অবোধ বোধ’ একপ্রকার অলসতার মতো। তাঁর কবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত অসুস্থতার অনুভূতি বারবার এসেছে। তিনি তাঁর অসুখকে বলেছেন, ‘অমৃতের এক গুচ্ছ অন্ধকার’। আবুল হাসানের ‘রাজা যায় রাজা আসে’ কাব্যগ্রন্থে তাঁর স্বদেশ প্রেমের গুঞ্জরণ আছে, কিছুটা রাজনৈতিক চিন্তাও আছে। কিন্তু সকল কিছু অতিক্রম করে এমন একটি গৃহে প্রত্যাবর্তনের তার বাসনা আছে যেখানে প্রাচুর্য নেই কিন্তু দারিদ্রের অমোঘ নিয়তি আছে। আবুল হাসান বর্ণনার স্বচ্ছতায়, ঋদ্ধতায় ও সুস্পষ্টতায় এবং একটি কল্লোলিত আন্তরিকতায় আমাদের মনকে সহজেই জয় করে নেন। আবুল হাসানের কাব্যগ্রন্থের নাম ‘রাজা যায় রাজা আসে’ (১৯৭৩); ‘যে তুমি হরণ করো’ (১৯৭৪) এবং ‘পৃথক পালংক’ (১৯৭৬)।
শহীদ কাদরী (জন্ম-১৯৪২):
বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে যথার্থ নাগরিক সত্তার কবি একমাত্র শহীদ কাদরী। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই প্রথম কবি যিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে স্বকীয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উত্তরাধিকারে’–এর বিস্তৃত পরিচয় আছে। একটি নগর বিত্তবান মানুষের যেমন, তেমনি তা পথচারী অসতর্ক পথিকেরও। শহীদ কাদরীর কবিতা একজন নিসঙ্গ পথিকের একাকী অবস্থার স্মারকলিপি। যেহেতু তিনি একটি নগরে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে চলেছেন সুতরাং কোন সঙ্গীর তাঁর প্রয়োজন নেই। শহীদ কাদরী তাঁর একাকীত্বকে তাঁর বিশ্বাস ও আনন্দের উপকরণ করেছেন। তিনি যা দেখছেন তা যেন একাকী দেখছেন এবং সে দেখার সহমর্মী কাউকে সঙ্গে রাখছেন না। বৃষ্টিতে হোক, দিবালোকে হোক অথবা ইন্দ্রজাল বিস্তৃত তারকাখচিত রাত্রিতে হোক সবক্ষেত্রে সময়কালের উপভোগটা কবির একার। ‘উত্তরাধিকার’ কাব্যগ্রন্থের দ্বারা-ই শহীদ কাদরীর যথার্থ কবি স্বীকৃতি। এই গ্রন্থটি ছাড়া তাঁর আরো দু’টি কাব্যগ্রন্থ আছে। কিন্তু সেগুলোতে তিনি বড় বেশী সাম্প্রতিকতায় জড়িয়ে পড়েছেন। ‘উত্তরাধিকার’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে; ‘তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তম’ ১৯৭৪ সালে এবং ‘কোথাও কোন ক্রন্দন নেই’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে।
আজীজুল হক (জন্ম ১৯৩০):
আজীজুল হক দীর্ঘকাল ধরে কবিতা লিখছেন। কিন্তু রচনার বৈশিষ্ট্যের কারণে যেভাবে তাকে সকলের দৃষ্টির সামনে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল সেভাবে আমরা তাকে দেখতে পাইনি। তার প্রধান কারণ তিনি রাজধানীর বাইরে থাকেন এবং সাধারণতঃ রাজধানীতে আসেন না এবং এখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টাও করেন না। অথচ তাঁর মধ্যে একটি অনুভূতিপ্রবণ মন আছে। মূলত লোকজ উপাদান গ্রহণ করে তিনি কবিতা লিখে থাকেন। এবং তাঁর কবিতার মধ্যে একধরনের শান্ত ও নির্জন অনুভূতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম ‘ঝিনুক মূহূর্ত সূর্যকে’; ‘বিনষ্টের চিৎকার’; ‘ঘুম ও সোনালী ঈগল’।
আবু বকর সিদ্দিক (জন্ম ১৯৩৬):
আবু বকর সিদ্দিক কবিতা ই প্রথমে লিখতেন। বর্তমানে কথা সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সকলের দৃষ্টিতে পৌঁছেছেন। তাঁর কথা সাহিত্যের মধ্যে মানবতার একটি আদিমরূপকে তিনি প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টায় তিনি সফলকামভাবে নাগরিক নিরীক্ষার বাইরে দৃষ্টি ফেলেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে লোকজ স্মৃতি এবং বিশ্বাসকে তিনি কবিতার উপাদান করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কযেকটি কাব্যগ্রন্থের নাম- ‘ধবল দুধের স্বরগ্রাম’; ‘বিন্দ্রিকালের ভেলা’; ‘হে লোক সভ্যতা’; ‘মানুষ তোমার বিক্ষত দিন’; ‘হেমন্তের সোনালতা’; ‘নিজস্ব এই মাতৃভাষায়’।
ওমর আলী (জন্ম-১৯৩৯):
দীর্ঘকাল ধরে ওমর আলী কবিতা লিখে চলেছেন এবং তিনি কবিতার উপকরণ পেয়েছেন বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির পুরুষ এবং রমণীদের কাছ থেকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি একসময় খুব সুনাম অর্জন করেছিল। গ্রন্থটির নাম ‘এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি’। এ কাব্যগ্রন্থটিতে বাংলাদেশের গ্রাম্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও শ্যামল রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। দীর্ঘকালের অভিনিবেশে ওমর আলী বাংলাদেশের কাব্য ভবনে একটি নিজস্ব মন্ডলী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের নাম- ‘অরণ্যে একটি লোক’; ‘ডাকছে সংসার’; ‘যে তুমি আড়ালে’; ‘শুধু তোমাকে ভাল লাগে’; ‘ছবি’; ‘পুরনা বেগম’। এছাড়াও তাঁর আরো অনেক ক’টি কবিতার বই আছে। তাঁর কবিতার মধ্যে জীবন এবং স্বপ্নের সংমিশ্রণ আছে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর একটি আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়।
ফরহাদ মাজহার (জন্ম-১৯৪৭):
ফরহাদ মাজহার রজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করেন, সমাজের বঞ্চনা এবং অবিবেচনা নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রখেন। এগুলো তাঁকে বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি পরিচয়ের বৃত্তে এনেছে। কিন্তু কবি হিসাবে ফরহাদ মাজহার যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লোকজ উপাদান এবং নাগরিক প্রত্যয়কে তাঁর কবিতায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অনেকগুলো প্রকাশিত কাব্য রয়েছে। এগুলোর নাম- ‘আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে’; ‘এবাদতনামা’; দরদী বকুল’; ‘অসময়ের নোটবই’; ‘বৃক্ষ’; ‘অকম্মা’; ‘রপ্তানীমুখী নারী মেশিন’; ‘খোকন ও তার প্রতিপুরুষ’। তাঁর বইয়ের নামগুলো দেখলে বোঝা যায় যে, এগুলোর মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ ও শ্লেষ আছে।
মুহম্মদ নূরুল হুদা (জন্ম ১৯৪৯)
মুহাম্মদ নূরুল হুদা দীর্ঘকাল ধরে কবিতা লিখছেন এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ টির মতো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রাগৈতিহাসিক উপাদান কবিতায় ব্যবহার করবার চেষ্টা করেন। তাঁর কবিতার নামগুলো দেখলেই এটা বোঝা যায়, যেমন- ‘আমরা তামাটে জাতি’; ‘শোভাযাত্রা’; ‘দ্রাবিড়ার প্রতি’; ‘জাতি সত্তার প্রতীক’।
আবিদ আজাদ:
বাংলাদেশের এ সময়কার কবিদের মধ্যে আবিদ আজাদ বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছেন। তাঁর কবিতা সুসজ্জিত বাগানে পরিভ্রমণ নয়। বরঞ্চ এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়ে পদচারণ। যে অবস্থায় হোক তিনি কবিতার পদচারণকে সুস্পষ্ট করতে চান, সুদৃঢ় করতে চান।
কবি আবিদ আজাদ বর্তমানকালের অবক্ষয়কে এবং দুর্যোগকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন। এখানেই তাঁর কবিতার সার্থকতা। তিনি রাজনৈতিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেননি অথবা সংস্কারক হিসেবে অতিব্যস্ত হননি। তিনি নিশ্চিন্তে একজন কবি হিসেবে তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটকে উন্মোচন করেছেন। আবিদ আজাদের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- ‘ঘাসের ঘটনা’ (১৯৭৬); ‘আমার মন কেমন করে’ (১৯৮০); ‘বনতরদের মর্ম’ (১৯৮২); ‘শীতের রচনাবলী’ (১৯৮৩); ‘আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি’ (১৯৮৭); ‘ছন্দের বাড়ি ও অন্যান্য কবিতা’ (১৯৮৭); ‘তোমাদের উঠোনে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে?’ (১৯৮৮); ‘আমার কবিতা’ (১৯৮০); ‘খুচরো কবিতা’ (১৯৯০)।
খোন্দকার আশরাফ হোসেন (জন্ম-১৯৫০):
খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় শব্দ ব্যবহারের একটি নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়। এ নিপুণতাটি তৈরী হয়েছে মোটামুটি একাডেমিক ভাব প্রকল্প থেকে। এটা বাংলা কবিতার জন্য একটি নতুন অনুশাসন। তবুও একথা বলতেই হয় যে, ৫০-এর দশকে যাদের জন্ম সেসব কবিদের মধ্যে খন্দকার আশরাফ হোসেন নিজস্ব একটি কাব্য ভুবন নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কবিতাগ্রন্থগুলোর নাম- ‘তিন রমণীর কাসিদা’; ‘পার্থ তোমার তীব্র তীর’; ‘জীবনের সমান চুমুক’ এবং ‘সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর’।
বর্তমান সময়ে যারা ক্রমান্বয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নিজেদের বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়- বিমল গুহ, বেলাল চৌধুরী, জাহিদুল হক, খালেদা এদিব চৌধুরী, শিহাব সরকার, সুহিতা সুলতানা, রবিউল হুসাইন, রেজাউদ্দিন স্টালিন, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল প্রমুখ। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি বিশেষ মানসিকতার লক্ষ্য করা যায় তা হলো বর্তমানের বিপর্যস্ত সময়ের কারণে এক প্রকার দুঃখবোধ।