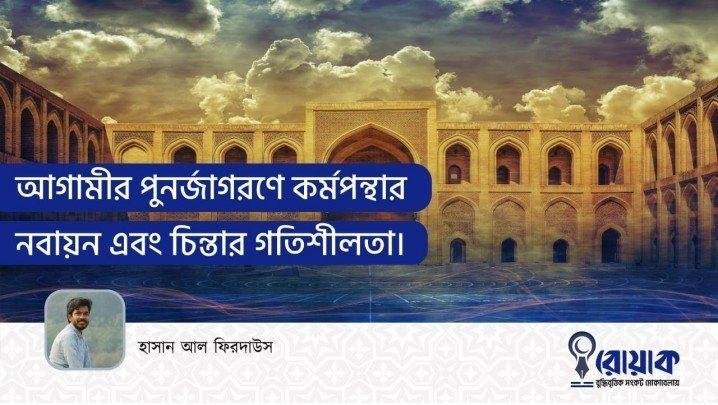ইবনে খালদুন মনে করেন ইসলামী সভ্যতার পতন মূলত অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে হয়নি। তার মতে চিন্তার ধারাকে বিকশিত বা অগ্রসর করতে না পারা তথা ইজতিহাদী জ্ঞানের মৃত্যুবরণই সভ্যতার পতন ডেকে আনে।
বর্তমানে মুসলিমরা কঠিন সংকট ও পতনাবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করছে। এক্ষেত্রেও ইবনে খালদুনের উপরোক্ত কথা আমাদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং এটিই আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। কেননা আমরা সবাই জানি সকল ইসলামী দল এবং ইসলাম পন্থীরা একটি বিষয়ে একমত। আর সেই বিষয়টি হলো-‘সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে, আর এজন্য আমাদের কোরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে’।
কিন্তু কীভাবে ফিরে যাব? কীভাবে যুগের আলোকে নিজেদের তুলে ধরব? কীভাবে ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করব? কীভাবে নিজেদের শক্তিশালী উম্মাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব?
এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিভিন্ন মত পার্থক্যের সৃষ্টি হচ্ছে অথবা মূলে ফিরতে গিয়ে উল্টো সবচেয়ে বেশি পেছনে পড়ে থাকতে হচ্ছে।
যে বিষয়গুলো ব্যতীত মুসলমানদের কর্মপন্থা নির্ণয় করা অনেকটাই অসম্ভব, সেগুলো হলো–
• স্থায়ী উসূল বা মূলনীতির সঠিক মূল্যায়ন।
• ইসলামী চিন্তার ধারাবাহিতা ও পর্যায়কাল।
• ইসলামী চিন্তা ও দর্শনের ব্যাপকতা এবং সামগ্রিকতা।
• ইসলামী সভ্যতার নানা প্রেক্ষাপটসমূহ।
• ইসলামী সভ্যতার পতনকালীন সময়ের সকল বিষয়ের পর্যালোচনা ও পতনের প্রধান কারণগুলো নির্ণয়।
• বর্তমান যুগকে ভালোভাবে বোঝা এবং এই যুগের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার যোগ্যতা অর্জন।
আর এ বিষয়গুলো ছাড়া যেসব ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব, তা হলো–
• মৌলিক কাজ নির্ধারণ।
• অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ, উদ্যোগগুলো নির্ণয়।
• সময় উপযোগী ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের রূপরেখাস্বরূপ কাজ ও কর্মসূচি নির্ণয়।
এছাড়াও গতানুগতিকভাবে অথবা কোনো পূর্ববর্তী মডেলকে সামনে রেখে আগাতে থাকলে পথ চলা যাবে, কিন্তু ফলাফল যে আসবে না এ ব্যাপারেও আমরা সবাই নিশ্চিত।
এখন কথা হলো ইবনে খালদুন কোন প্রেক্ষিতে উক্তিটি করেছিলেন? এটি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি তা কীভাবে বুঝবো?
ইতিহাস দেখলেই আমরা তার উত্তর পেয়ে যাবো। যেমন, উসমানী এবং মোঘল সালতানাতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতনের আগেই জ্ঞান মৃত্যুবরণ করে, তারপর আস্তে আস্তে সামগ্রিক পতন হয়। অর্থাৎ ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে, তাকলিদের কারণে স্থবিরতার সূচনা হয়, এক পর্যায়ে গতিশীল চিন্তা ও জ্ঞানের মৃত্যু ঘটে!
আমরা জানি, ইবনে খালদুনের বিখ্যাত ‘মুকাদ্দিমা’ গ্রন্থটি মূলত তার নিজের জীবনের প্রশ্নের উত্তর। তৎকালীন সময়ে মোঙ্গলদের আক্রমণ ও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ মুসলমানদেরকে চরম হতাশায় নিমজ্জিত করে। “কিয়ামত চলে এসেছে”, “ইমাম মাহদীর আগমনের সময় হয়েছে”– এ রকম হাজারো কথা খোদ আলেমরাই বলতে শুরু করেন। বাকিদের অনেকেই পূর্ববর্তী গতানুগতিক কিছু কাজকেই সফলতা ও জান্নাত প্রাপ্তির উপায় মনে করে মানসিক তৃপ্তি পেতে থাকে, আবার কেউ কেউ নিজেদের উন্নত করার বদলে কোনো নির্দিষ্ট আলেম বা খানকার অন্ধ অনুকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শুরু করে। সে সময়ে এসব কথিত বয়ান ও চিন্তাকে খন্ডিয়ে নতুন এক আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিলেন একমাত্র মুজতাহিদ আলেমগণ। সে সময়েই ইতিহাস-দর্শনকে নতুনভাবে দাঁড় করান ইবনে খালদুন এবং তিনি চিন্তা ও জ্ঞানের বিশাল এক সমুদ্রকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি নিজের প্রশ্ন আর উত্তরগুলোকে নিয়ে জ্ঞানের নতুন একটি শাখা দাঁড় করিয়ে এক অসাধারনত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন যা আজও আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।
মোঙ্গল আক্রমণ পরবর্তীতে যে পতন হয়েছিলো, তার চেয়েও ভয়াবহ ও বড় পতন গত দেড়শো বছরে হয়েছে। সুতরাং, আমাদের মনেও কি সর্বদা একই প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছে না? সেই হতাশা, হীনমন্যতা আর অযোগ্যতায় কি আমরা নিমজ্জিত হইনি? কিন্তু আমরা কি ইবনে খালদুনদের মতো পর্যালোচনা করতে পারছি? পারলে আমরাও হয়তো উত্তর পেয়ে যেতাম।
আর ইমাম গাজ্জালী তো ইবনে খালদুনের বহু আগেই মোঙ্গলদের দখল পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের অবস্থা বলে গেছেন। অর্থাৎ, জ্ঞানের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই সভ্যতার পতন শুরু হয়। আবার ইতিহাস এটিও সাক্ষ্য দেয়, সভ্যতার মূল উত্থানও শুরু হয় চিন্তা ও জ্ঞানের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়েই। কেননা এরপরেই উনাদের হাত ধরে জ্ঞানের এক বিশাল আন্দোলন শুরু হয়, যা উসমানী খেলাফতকে ৬০০ বছর টিকিয়ে রাখে। এজন্য বড় বড় শিক্ষকগণ উক্ত আলেমদের বিষয়ে পড়ানোর সময় সে সময়ের ইতিহাস, সামাজিক অবস্থা, আলেমদের জীবনের সবকিছুকে সামনে নিয়ে আসেন। অতঃপর আলেমদের চিন্তাদর্শনকে পর্যালোচনা করেন ও শিক্ষা গ্রহণ করেন।
কারণ–
• এ পদ্ধতির মাধ্যমে স্থায়ী মূলনীতি নিরূপণ করা যায়। ইসলামী চিন্তার ধারাবাহিকতা ও পর্যায়কালকে উপলব্ধি করা যায়। ইসলামী সভ্যতার নানা প্রেক্ষাপটের আলোকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।
• আলেমগণ যুগ‐জিজ্ঞাসার জবাব কীভাবে দিয়েছেন তা বোঝা যায় এবং এটিই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হলো প্রত্যেক বড় প্রজ্ঞাবান মুজতাহিদ আলেম তার যুগের আলোকে সমস্যা নিরূপণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য মূলনীতি দিয়েছেন। যেমন– ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম গাজ্জালী একই ধারার চিন্তাবিদ, কিন্তু তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ “আর রিসালা” ও “আল মুসতাসফা” পড়লেই বোঝা যায় কত বেশি ভিন্নতা রয়েছে। কারণ কী? কারণ তাদের সময়ের পার্থক্য কয়েকশো বছর। অর্থাৎ উভয়েই তাদের যুগের আলোকে নিজেদের চিন্তাদর্শন, মূলনীতি ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা দিয়েছেন।
এভাবে বড় বড় শিক্ষকদের এসব পর্যালোচনাকে সামনে রাখলে দেখবো ইবনে খালদুনের উপরোক্ত কথা বর্তমান সময়ের জন্যও সামগ্রিকভাবেই প্রযোজ্য। বর্তমানে উপমহাদেশীয় অঞ্চলে পতন পরবর্তী সবচেয়ে বড় সংকটও এটিই!
এক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষণীয়–
• শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ও আল্লামা শিবলী নোমানীর পর আলেমদের মধ্য থেকে গত ১০০ বছরে (২য় বিশ্বযুদ্ধ, ইয়াল্টা কনফারেন্স পরবর্তী দুনিয়ায়) তাদের মতো কোনো আলেম কি উঠে এসেছে?
• আল্লামা ইকবালের ইজতিহাদী চিন্তা ও রাজনৈতিক দর্শনের পর তার চেয়েও বড় ব্যক্তিত্ব উঠে আসা, তার চিন্তাকে বিকশিত করা তো বহু দূরের কথা, আল্লামা ইকবালকেই কি আমরা বুঝতে পেরেছি? তাকে ধারণ করতে পেরেছি? ইসলামী চিন্তাদর্শন, কালাম, মেথডোলজি দিয়ে আল্লামা ইকবালকে পরিমাপ করতে পেরেছি?
• মাওলানা মওদূদীর পর তার রেখে যাওয়া ধারা কি তার চিন্তাকে আরও উন্নত করতে পেরেছে? তার রেখে যাওয়া মিরাসকে আরো উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছানোর মতো কোন ব্যক্তিত্ব কি গড়ে উঠেছে? নাকি কোনো রকম অনুকরণ ও জয়ধ্বনির স্লোগানেই তা সীমাবদ্ধ?
একটু ভেবে দেখুন তো।যেখানে এমন আলেমদেরই আমরা বিকশিত করতে পারিনি, বুঝতে পারিনি, সেখানে ইবনে খালদুনের মতো কেউ কীভাবে উঠে আসবে? কীভাবে এ যুগের ‘রিসালা’, ‘মুকাদ্দিমা’ রচিত হবে? আর এমন মুজতাহিদ আলেম ব্যতীত মুক্তির রূপরেখাই-বা কে দিবে? অথচ অবস্থা এমন যে, মুক্তির রূপরেখা নয় বরং মুক্তির স্বপ্নও দেখতে পারবো না আমরা!
আমরা আমাদের নিজেদের যুগকেই-বা কতটুকু বুঝতে পেরেছি?
হিকমতের শক্তি, আত্নবিশ্বাসের শক্তিই-বা কতটুকু আছে আমাদের?
সবশেষে একটি দ্বিমতের জায়গা থাকে, সেটি হলো চিন্তার বিকাশই একমাত্র কারণ নয়, একইসাথে নেতৃত্বের সংকট বা অযোগ্য নেতৃত্বও সভ্যতার পতনের অন্যতম একটি কারণ। কিন্তু হিকমতের শক্তি ও আত্মবিশ্বাসী ইশতেহার ব্যতীত কি নেতৃত্ব হয়? আর যারা সেই হাকীকত অন্বেষী নয় তারা যখন নেতা হয়, তখন কি তারা আদৌও বুঝতে পারে কোনটি ইজতিহাদী চিন্তা আর কোনটি অন্ধত্ব?
এ কারণে যুগে যুগে অবদান রাখা দূরদর্শী নেতাগণও একেকজন মুজতাহিদ আলেম ছিলেন। অন্যথায়, সভ্যতার বিজয়ে তাদের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত আসা অসম্ভব ছিলো। একইভাবে এসবে ঘাটতি থাকায় নেতাদের কারণেই বিশাল সভ্যতার পতনও হয়েছে!
এজন্য মূলকথা হলো সবকিছুর উর্ধ্বে গিয়ে সভ্যতার পুনর্জাগরণ ঘটাতে হলে সংকটসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা পর্যালোচনার আলোকে সঠিক কর্মপন্থা খুঁজে বের করতে হবে। কারণ, খেলাফতের পতন মূলত এসব ক্ষেত্রে ঘাটতির কারণেই শুরু হয়েছিলো। একইভাবে প্রত্যেক যুগের সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে চিন্তা ও জ্ঞানের পুনর্জাগরণ তথা চিন্তা বিকশিত করে সে আলোকে গড়ে ওঠা আন্দোলন সমূহ-ই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে, সভ্যতাকে স্থায়ী ভিত্তি ও ধারাবাহিকতা দিয়েছে; যেভাবে মোঙ্গল পরবর্তী জ্ঞানের আন্দোলন উসমানী খেলাফতকে ৬০০ বছর স্থায়ীত্ব দিয়েছিলো।
তাই পতন পরবর্তী বর্তমান দুনিয়ায় আমাদের এই মুহুর্তে সবচেয়ে বড় কাজ হলো চিন্তার ধারাকে বিকশিত বা অগ্রসর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং ইজতিহাদী জ্ঞানের উদ্ভাবন করা। অন্যথায়, দূরদর্শী নেতৃত্ব উঠে আসা, মুক্তির ইশতেহার প্রদান, পাশ্চাত্যের বিপরীতে ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও সভ্যতার পুনর্জাগরণ স্বপ্নই থেকে যাবে!